সাহিত্যে নোবেল ঘোষণার ঘটনায় বিগত কয়েক বছর ধরে নোবেল কমিটি ভালোই চমক দিচ্ছেন। বিশ্বজুড়ে পঠিত ও পরিচিত লেখকদের পরিবর্তে তুলনামূলক অপঠিত বা সম্পূর্ণ অজানা লেখককে বেছে নিচ্ছেন তাঁরা। আলী আহমদ সাঈদ ইসবার ওরফে অ্যাডোনিস, হারুকি মুরাকামি, মার্গারেট অ্যাটউড, সালমান রুশদির মতো সুপরিচিত লেখকরা পেতে পারেন বলে অনেকে ধারণা করেন প্রতি বছর। বাস্তবে ঘটে উলটো। এ-বছর যেমন অ্যাডোনিস ও অমিতাভ ঘোষ ছিলেন আলোচনায়। সকলের অনুমানে জল ঢেলে নোবেল কমিটি এমন এক লেখককে সামনে এনেছেন, ব্যতিক্রম বাদ দিলে তাঁর নাম ও সাকিন সকলের অজানা ছিল এতদিন! তিনি যদিও নোবেলের আগে বুকার পেয়ে বসে আছেন। সংগতকারণে, সাহিত্যমহল বেশ উৎসাহ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন।

অনলাইনের এই জামানায় তথ্য সুলভ হওয়ার কারণে অজানাও বেশিখন অজানা থাকে না। উৎসাহীরা বেশ দ্রুত হাড়ির খবর বের করে আনেন। অনেকে একে তাচ্ছিল্য ও পরিহাসের চোখে দেখছেন যদিও! রসিকতা আর নেতিবাচক মন্তব্য ছাড়ছেন দেদার। তাতে কার কী ফায়দা হচ্ছে, সে মোর জানা নেই! একজন লেখকের নাম না শোনা অথবা শোনার পর তাঁকে জানতে আগ্রহী হওয়ার মধ্যে তো দোষের কিছু নজরে আসছে না।
জগৎজুড়ে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলার বিচিত্র বিষয় নিয়ে কাজের পরিধি এখন যে-কোনো সময়ের চেয়ে ব্যাপক। মানুষের হাতে বেঁচে থাকা সময় ও যাপন-জটিলতাকে যদি হিসাবে ধরি, তাহলে কারো পক্ষে সকল খুঁটিনাটিতে চোখ রাখা সম্ভব নয়। নোবেল বা বুকার-এর মতো গ্ল্যামারে ঠাসা স্বীকৃতির সুবাদে যদি অশ্রুত-অজানা কবি-লেখককে জানতে পারা যায়, তাতে ক্ষতির কারণ দেখি না! উন্নাসিকরা বরং সস্তা রসিকতা বাদ দিয়ে জানতে পারার চেষ্টায় গমন করলে অন্যদের উপকার হয়। তাদের মাধ্যমে অচেনা-আজানা লেখককে জানাবোঝার নতুন পরিসর যে-মিলবে না, এমন তো নয়!
অ্যানিওয়ে, লাসলো ক্রাসনাহোরকাইকে নিয়ে উৎসাহ দুদিন বাদে আপনা থেকে মিইয়ে যাবে। ইস্যু-ঠাসা মানবগ্রহে সাহিত্যমহলে চরে খাওয়া লোকজন অন্য কিছু নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বেন। আপাতত, এই-যে তাঁকে জানাবোঝার চেষ্টা চলছে, সেটি উপভোগ করাটাই শ্রেয়। বিধ্বস্ত বাংলাদেশে মনমেজাজ এমনিতেও কেরাসিন সবার! নোবেলের মেডেল পাওয়া একজন লেখককে আবিষ্কারের চেষ্টা সেখানে রিলিফের খোরাক দিতেও পারে খানিক। দুখানা বিষয় কেবল চোখে বিসদৃশ ঠেকেছে। যথাসম্ভব সংক্ষেপে তা বলার চেষ্টা করব এখানে।
প্রথমত, লাসলো ক্রাসনাহোরকাইয়ের গল্প,আখ্যান ও সাক্ষাৎকার ইত্যাদি নিয়ে কবিলেখকরা ঘাঁটছেন বোঝা যায়। উৎসাহের ঠেলায় ছোট ও মাঝারি আকৃতির গল্প আর সাক্ষাৎকার অনুবাদ করছেন অনেকে। মন্দ নয় এ-প্রয়াস;—কিন্তু সেখানে (ব্যতিক্রম থাকতে পারেন) তাঁর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রচনা স্যাটানট্যাঙ্গোর আলাপ বড়ো আকারে কেউ তুলেছেন, এমনটি চোখে পড়েনি এখনো! নোবেলজয়ী লেখকের সঙ্গে আমাদের আদি পরিচয়ের শিকড় যদি খুঁজতেই হয়,—স্যাটানট্যাঙ্গো আসবেই;—এবং তা বেলা তার/বেলা টারের (Béla Tarr) কারণে আসতে বাধ্য।
হাঙ্গেরির এই অবসরে যাওয়া চলচ্চিত্র নির্মাতার হাত দিয়ে স্যাটানট্যাঙ্গোর মতো ধ্রুপদি গদ্য-মহাকাব্য সিনেমার ভাষায় রূপান্তর নিয়েছিল গত শতাব্দীর নয়ের দশকের মাঝামাঝি সময়ে। বাংলাদেশে ভিন্নধারার চলচ্চিত্রের খোঁজখবর যাঁরা রাখেন, তাঁদের কাছে তিনি ভিনগ্রহের জীব নন। ইনফ্যাক্ট, তাঁকে নিয়ে রুদ্র আরিফসহ আরো অনেকে লিখেছেন, এবং সেখানে স্যাটানট্যাঙ্গো বাদ পড়েনি বলে আমরা নিশ্চিত থাকতে পারি। স্বেচ্ছা-অবসরে যাওয়া বেলা টারের পরিমিত মেয়াদি ফিল্ম ক্যারিয়ারে স্যাটানট্যাঙ্গো হচ্ছে এমন এক মাইলফলক,—একে স্কিপ করে তাঁর ব্যাপারে আলোচনা ফাঁদার প্রশ্নই আসে না।
প্রায় সাড়ে সাত ঘণ্টার এপিক আর্টপিসটি আমার মতো প্রান্তে পড়ে থাকা মানুষ যদি বেশ কয়েকবার দেখে থাকে ইতোমধ্যে, রাজধানীর সাহিত্যমহলে থাকা লোকজন দেখেননি,—এ-কথা বিশ্বাস করা কঠিন। তাঁরাও হয়তো সেখানে এর আদি স্রষ্টা লাসলো ক্রাসনাহোরকাইকে তখন নোটিশ করেননি। চিত্রনাট্যকার লাসলোর নাম পর্দায় কখন কোন ফাঁক গলে চলে যাচ্ছে, সেটি খেয়াল থাকেনি;—বেলা টারে ছিল মনোযোগ।
এখন তো জানা,—সমাজতন্ত্রের পতন ও পরিণাম তুলে ধরা ভিজুয়্যাল মাস্টারপিসের কাহিনিসূত্র বা এর রচয়িতা হলেন দুইহাজার পঁচিশ সনের নোবেলজয়ী লেখক। কেবল তাই নয়, খেয়াল করলে দেখতে পাচ্ছি,—বেলা টারের সঙ্গে লাসলো ক্রাসনাহোরকাইয়ের জুড়ি ম্যালা দিনের! স্যাটানট্যাঙ্গো ছাড়াও দ্য তুরিন হর্স ও ড্যামনেশন-র চিত্রনাট্য তাঁরা দুজনে মিলে লিখেছেন! মানে দাঁড়াচ্ছে, বেলা টারের ছবির পোয়েটিক ভিশন ও ফিলোসফির ভিত মজবুত করতে লাসলো বড়ো ভূমিকা নিভিয়েছেন। যেটি, তাঁর চলচ্চিত্র নিয়ে আলোচনায় নোটিশ করা হয়নি। আহাম্মকিই বটে!
এখন, আস্তে-আস্তে জানা যাচ্ছে সবটা;—যেখানে আবার ওই স্যাটানট্যাঙ্গোকে ফিরেফিরে আলাপ থেকে বাদ পড়তে দেখে খটকা জাগছে মনে! আমাদের উৎসাহী কবিলেখকরা কি তাহলে সাড়ে সাত ঘণ্টার এপিক জার্নির ব্যাপারে অবগত ছিলেন না? নাকি, ছবির দৈর্ঘ্য দেখে দেখার ইচ্ছে মরে গিয়েছিল তাঁদের? স্যাটানট্যাঙ্গোকে যদিও পর্ব ধরে বা পজ দিয়ে-দিয়ে সহজেই দেখে ফেলা যায়। ফিলিপিনো চলচ্চিত্রকার লাভ ডিয়াজের এরকম একখানা ছবি আছে;—প্রায় সাড়ে দশ ঘণ্টা দৈর্ঘ্য তার! এমনকি বাংলাদেশের একজন চলচ্চিত্রকার আশরাফ শিশির আমরা একটা সিনেমা বানাবো নামে সম্ভবত সাড়ে একুশ ঘণ্টার একখানা ছবি তৈরি করেছিলেন। ছবিটি দেখার কোনো সুযোগ হয়নি; সুতরাং আশরাফ শিশিরের নির্মিতি নিয়ে বলা সম্ভব নয়, তবে ট্রেলার ইত্যাদি চোখে পড়েছিল তখন। সে যাইহোক, অনলাইনের যুগে ভেঙে-ভেঙে এরকম ছবি দেখা এমন কোনো মুশকিল নয় এখন।
হিসাব কাজেই মিলছে না বিলকুল! লাসলো নিয়ে সাহিত্যমহলের উৎসাহী হওয়ার ইতিবাচকতা ভালো ঘটনা, কিন্তু সেখানে তাঁর স্বকীয়তাকে আমরা কীভাবে জানার চেষ্টা করছি, তার কিছু মাথায় ঢোকেনি! তাঁকে নিয়ে সাহিত্যমহলের উৎসাহ কি তাহলে হুজুগ অথবা নিজেকে আপডেট প্রমাণের চেষ্টা? এরকম ভাবতে চাই না একদম। তবে, একজন লেখকের স্বকীয়তাকে বোঝার চেষ্টা আমাদের কবিলেখকরা করছেন, এবং সেটি স্যাটানট্যাঙ্গোকে বাদ দিয়ে,—হিসাব বাহে মিলছে না! লাসলোর ব্যাপারে প্রাথমিক ধারণা হয়ে যাওয়ার পর যে-কেউ বুঝে যাবেন,—বেলা টার তাঁর ক্যামেরায় যেুটুকু ধরেছেন, সেখানে এই লেখকের সাহিত্যিক ব্যঞ্জনা ভিন্ন মোড় নিলেও,—তাঁকে চিনিয়েও যায়। আমাদের সাহিত্যমহলে তাঁর ব্যাপারে উৎসাহ ইতিবাচক মনে হলেও, তাঁকে বুঝে ওঠার জায়গা থেকে এই উৎসাহকে বিট অ্যারাউন্ড দ্য বুশের মতো লাগছে দেখে!
দ্বিতীয়ত, গেল ক’দিনের যৎসামসান্য খবরাখবরে বোঝা গেল, লাসলো ক্রাসনাহোরকাই দুটি জায়গায় ব্যতিক্রম। একটি হচ্ছে তাঁর ভাষা-ব্যবহার, যেখানে জেমস জয়েসের মতো তিনিও যতিচিহ্ন একপ্রকার বিলোপ ঘটিয়ে লেখেন। যার মধ্য দিয়ে তৈরি করেন গীতলতা, যেটির ওপর ভর দিয়ে তাঁর কাহিনির মূল অংশ দাঁড়িয়ে থাকে। ইউরোপের জন্য নতুন নয় এই লিখনশৈলী, তথাপি নোবেলে কিমতি রেখেছে বরাবর।
গতকাল রাতে লাসলোর স্বকণ্ঠে পঠিত একখানা গল্প শুনছিলাম। একটি লোকের কাহিনি বলছেন গল্পে;— দুটি বড়ো স্যুটকেস হাতে লোকটি তার বাড়িতে প্রবেশ করতে যাচ্ছে। প্রবেশক্ষণকে নিয়ে টানা লয় তৈরি করছেন লাসলো। যার ভিতর দিয়ে বাড়িটির সঙ্গে তাঁর সম্পর্কিত হওয়ার অন্ধিসন্ধি উঠে আসে। যেখানে, নির্বাসিত হওয়া ও প্রত্যাবর্তনের ওই চিরাচরিত বেদনার দার্শনিক উন্মোচন ঘটাচ্ছেন লাসলো। বোঝা গেল,—তিনি একজন উত্তম বাচিকশিল্পী! গল্পটি পাঠের সময় তাঁর কণ্ঠস্বরের মধ্যে থাকে গাঢ় অন্তর্মগ্নতা, এবং তা সম্মোহক।
গল্পটি শোনার তাৎক্ষণিক রেশ কাটতে-না-কাটতে কমলকুমার মজুমদার স্মৃতিতে হানা দিয়ে গেলেন। ভাষার কারিকুরি আর নিরীক্ষা ও দর্শনমগ্নতা,—যেটি এখন লাসলো ক্রাসনাহোরকাইয়ে আমরা পাচ্ছি, অভিভূত হচ্ছি,—কমলকুমার মজুমদারেও তা মিলবে বিলক্ষণ। অন্তর্জলী যাত্রা, সুহাসিনীর পমেটম, গোলাপ সুন্দরী অথবা তাঁর গল্পগুলোয় গুঞ্জরিত গদ্যময় কাব্যিক বিস্তার, ধ্বনিব্যঞ্জনা, সংগীতময় গাঢ়তা, সর্বোপরি দার্শনিকতাকে যদি ইয়াদ করি এখন,—সেগুলো কোনোভাবেই লাসলোর চেয়ে হীনবল নয়! কমলকুমার ফরাসিসহ একাধিক ভাষা জানতেন; শিল্পকলার অন্ধিসন্ধির ওপর দখল ছিল তাঁর;—ভাষাকে দুমড়ে-মুচড়ে নতুন ভাষা তৈরির পথও গড়ে নিয়েছিলেন। সেই কমলকুমারকে কারো মনে পড়ছে না দেখে অবাক লাগছে বৈকি!

হতে পারে, লাসলো নিয়ে উৎসাহীরা সেরকম কিছু টের পাচ্ছেন না! বিদেশি এক লেখককে আবিষ্কারের উত্তেজনা সব ছাপিয়ে যাচ্ছে সেখানে। কিন্তু, লেখকের আবার দেশ-বিদেশ কী! লাসলো স্বয়ং তাঁর বয়ানের মধ্যে উন্মূল ও শিকড়তাড়িত হয়েও শিকড় থেকে বিতাড়িত বিশ্বে নিজেকে উন্মোচন করছেন ফিরেফিরে। যেটিকে নৈরাশ্যের দুঃসহ নরক বলে আমাদের এখানে চিনছেন উৎসাহীজন। যেটি, ইউরোপের সাহিত্যে একপ্রকার অকাট্য সিগনেচার বলে বিদিত অনেকদিন ধরে।
লাসলোর বলার ভঙ্গি, ভাষার প্রয়োগ ও নিগূঢ় মনোজগতে প্রবাহিত ভাবনারীতি… কেন জানি কমলকুমারকে তথাপি ইয়াদ বিলিয়ে যাচ্ছে বেশ! মনে-মনে ভাবছি,—তাঁকে ভাষান্তর ও ঠিকঠাক নোবেল কমিটি বরাবর পৌঁছানো গেলে কী ঘটত তখন! নোবেল কমিটি কি ধরতে পারতেন প্রাচ্যবাসী লেখকের কাব্যঘন বয়ানের অন্তরালে সংগোপন আ্যধাত্মিক খেদ? ধরতে পারতেন অন্তর্জলী যাত্রার প্রারম্ভিক বিবরণের মাহাত্ম্য? যেখানে, কমলকুমার শুরুই করছেন সম্মোহক :
আলো ক্রমে আসিতেছে। এ নভোমণ্ডল মুক্তাফলের ছায়াবৎ হিম নীলাভ। আর অল্পকাল গত হইলে রক্তিমতা প্রভাব বিস্তার করিবে, পুনৰ্ব্বার আমরা, প্রাকৃতজনেরা, পুষ্পের উষ্ণতা চিহ্নিত হইব। ক্রমে আলো আসিতেছে।
এই-যে লাসলোকে জানতে যেয়ে কমলকুমারকে আরো নিবিড় মনে পড়া, তাঁকে জেনে ওঠা ও জানার তাগিদ,—এগুলো হচ্ছে দামি। বাকিদের কাছে হয়তো নয়! জানি না, তারা কী জানছেন লাসলোর থেকে!
. . .
সংযুক্তি
(কবি কুমার চক্রবর্তীর বক্তব্য পাঠের জের ধরে এই সংযুক্তি)

লাসলো ক্রাসনাহোরকাইকে নিয়ে আমাদের এখানে যেসব কথাবার্তা চোখে পড়েছে, তার মধ্যে কবি কুমার চক্রবর্তীর বক্তব্য তুলনামূলক যুক্তিগ্রাহ্য লেগেছে পাঠ করে। তাঁর বক্তব্যে ভাবনার রসদ আছে। সারসংক্ষেপ যদি করি তাহলে দুটি রসদ পাচ্ছি সেখানে :
প্রথম রসদ, ইউরোপের সাহিত্য সামগ্রিকভাবে জয়েস-কামু-কাফকা সৃষ্ট ভাষাপৃথিবীতে এখনো বন্দি ও এর পুনরাবৃত্তিতে অন্তহীনভাবে রিক্ত ও নিঃস্ব। ক্রমশ অনুবাদ-অযোগ্য এক ভাষাবৃত্তে নিজেকে পরিকল্পিতভাবে বন্দি করছে ইউরোপ। দ্বিতীয় রসদ, ইউরোপ এটি করছে ভাষারাজনীতিতে নিজের আধিপত্য ধরে রাখতে।
তাঁর দাবি মিথ্যে নয়; তবে সরলীকরণ আছে সেখানে। যেমন, কুমার লিখেছেন : ‘আমাদের কাছে শব্দ হলো শব্দব্রহ্ম যার মধ্যে চৈতন্য থাকে।’ যেটি, তাঁর মতে ইউরোপীয় সাহিত্যে জেমস জয়েসের সময় থেকে তামাদি হতে শুরু করে। জয়েসদের নতুননত্ব ও অনন্যতা ব্যাখ্যা করে কুমার বলতে চেয়েছেন,—ভাষা ‘গুরুত্বপূর্ণ’, কিন্তু তা যদি ভাবনার স্পেসকে গিলে ফেলে, তাহলে নতুন সাহিত্য সৃষ্টি অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।
ইউরোপে জয়েস-কামু-কাফকাদের পরে সেই অর্থে নতুন সাহিত্য যে-কারণে সৃষ্টি হয়নি বলে তিনি মত রেখেছেন। তাঁর মতে যেটি হয়েছে বা এখনো হচ্ছে, তা হলো এঁনাদের সৃষ্ট ভাষাজগতের চর্বিতচর্বন। যেখানে, ভাষার সৌন্দর্য আছে, কিন্তু নতুনত্ব নেই;—না আছে ‘ভাবনা’র গভীর উন্মোচন।
‘ভাবনা’ বলতে কুমার চক্রবর্তী ঠিক কী বুঝিয়েছেন, তা অবশ্য পরিষ্কার হলো না খুব একটা! শব্দে বিরাজিত চৈতন্যকে এখানে আমরা মোটের ওপর বস্তুতীত, ইন্দ্রয়াতীত অথচ ইন্দ্রীয় দ্বারা অনুভবযোগ্য বলে ধরে নেই;—যেটি আবার ইউরোপে চর্চিত কনশাসনেস নামক প্রপঞ্চের সঙ্গে খাপে খাপ মিশ খায় না! আমরা তাই ভাবি,—ভাষায় চৈতন্যের প্রকাশ ঘটে রহসময়তায়। এ-কারণে শব্দ কেবল শব্দ নয়, তা ব্রহ্মস্বরূপ ও মানুষের অন্তরলোককে উন্মোচনের মতো শক্তিশালী। সবই বোঝা গেল, কিন্তু এখানে কুমার কথিত ‘ভাবনা’কে তো খুঁজে পাচ্ছি না!
ভাবনা বা থটস, যাই বলি, এটি আসছে কোথা থেকে? ভাবনার রসদ তৈরিতে কনসাশনেস ভূমিকা রাখে বলে ওখানে তারা মত দিয়ে থাকেন। আমরা চৈতন্যকে ভাবনার অতীত প্রবাহন বলে বুঝি। আমরা, এই-যে ভাষায় প্রকাশ করছি সবকিছু,—সেটি অতীন্দ্রিয়, মরমি, আধ্যাত্মিক; আর তারা একে নামিয়ে আনছেন মন-মধ্যে বা চেতনায় প্রবাহিত তরঙ্গ রূপে। তারা মনের ভিতরে চলতে থাকা অনুভূতির তরঙ্গকে ভাষায় ব্যক্ত করেন, যার মধ্যে কাহিনির শাসন মেনে তৈরি পরম্পরা ও শৃঙ্খলা জরুরি থাকে না। বড়ো হয়ে দাঁড়ায়,—মনে যা-চলছে, তাকে ভাষায় অবমুক্ত করা। যে-কারণে কাফকার গ্রেগর সামসা অবলীলায় নিজেকে পোকায় রূপান্তর নিতে দেখে।

এর মধ্যে আবার যে-জগতে সে বসবাস করছে, তার প্রভাব কাফকার বয়ানে উঠে আসে। মূলত, জাগতিক বাস্তবতা তার মনে যে-ভীতি ও এলিয়েনেশন তৈরি করে দিচ্ছে, সেটি চেতনায় গিয়ে পতঙ্গে রূপান্তরিত হওয়ার মতো অ্যাবসার্ড ঘটনাকে বাস্তব করে তুলছে। এর ফলে, কাফকাদের জগতে শব্দ আমাদের এখানকার মতো শব্দব্রহ্ম নয়, তা ওই মাইন্ড স্টেট বা মানসিক অবস্থার বহিঃপ্রকাশ সেখানে। জেমস জয়েসের রচনা এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কুমার চক্রবর্তী নিজের লেখায় এদিকটি নিয়ে সুন্দর বলেছেনও।
প্রশ্ন হলো,—এভাবে প্রকাশ যদি ঘটেই থাকে, তাতে অসুবিধে কোথায়? বোধগম্য হলো না কিছু! ইউরোপের সাহিত্য তো এখানে সামগ্রিকভাবে যে-যাপনের মধ্যে তারা পড়ে গেছেন,—তার প্রতিফলন। যেখানে, আমাদের মতো করে শব্দব্রহ্ম নামক চৈতন্যপ্রকাশক অনুভবকে জ্ঞাপন করার অবস্থায় তারা নেই। যেমন নেই , লাতিন ও আফ্রিকান বাস্তবতায়। আমাদের পয়েন্ট অব ভিউ থেকে আমরা নিজেকে যতখানি লাতিন ও আফ্রিকান বাস্তবতার নিকট ভাবছি, ইউরোপের পক্ষে তা ভাবা অবান্তর। যেহেতু, সময়টানে ইউরোপের জীবনধারা যে-মাত্রায় উনপীত হয়েছে ও সামনে হতে চলেছে, সেখানে বিমানবিক বা ডিস্টোপিয়ান ফিল বরং আগে মনজুড়ে গেড়ে বসে।
প্রসঙ্গত, বেলা টারের ছবি দ্য তুরিন হর্স মনে পড়ছে। তিনি ও লাসলো ক্রাসনাহোরকাই মিলে এর চিত্রনাট্য লিখেছিলেন। ছবিটি প্রথম দেখি সাত-আট বছর আগে। দেখার পর বেলা টার কী বলতে পারেন তার আন্দাজ পেতে চেষ্টা করছিলাম। রাশপ্রিন্ট-এ পরে লিখেছিও কয়েকছত্র। মনে হয়েছিল বেলা টার সামনাসামনি বসে বলছেন :
দেখো জীবন এরকম-ই। ভীষণ একঘেয়ে। রুটি-রুজির তালে সকলে একছন্দে ঘুরছি। পরিবেশ বৈরী। হাওয়া প্রতিকূল। স্রষ্টা নিখোঁজ। এসবের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পেটের দায় মেটাচ্ছে জগতের লক্ষ-কোটি কোচোয়ান। নিটশের অনেক কিছু বলার ছিল এবং তিনি সেটা বলেছেন, তবে কিছু পালটাতে পারেননি, তাই হয়তো পাগল হয়ে গেলেন!
আমার ছবির ওই কোচোয়ানের সত্যি কিছু বলার আছে বলো? একটা কথাই কেবল বলতে পারে সে,—‘আমাকে খাটতে হবে কিয়ামত তক। ঘোড়ার গাড়ি চালিয়ে পেট ভরাতে হবে। এমন জায়গায় থাকি, যেখানে আবহাওয়া বৈরী। এর মধ্যেই ঘোড়া নিয়ে বেরোনোর কাজ প্রতিদিন করতে হচ্ছে। যদিও পারি না বের হতে সবদিন। অন্যত্র যাবো, তার উপায় নেই। পালানোর রাস্তা বন্ধ ভায়া। খাটনিই এখানে কিয়ামত। ’
বেলা টার বলি আর লাসলো ক্রাসনাহোরকাই… তাঁরা বুঝে গেছেন, ধ্বংসেই সভ্যতার পরিত্রাণ। কারণ, এক্সিট রোড নেই। মানুষ নিজ হাতে তা ধ্বংস করে দিয়েছে। ধ্বংস বা প্রলয় বা কিয়ামত থেকে কেবল জন্ম নিতে পারে নতুন বাস্তবতা! চরম নৈরাশ্যবাদ, তাতে সন্দেহ নেই; কিন্তু ওরা যেভাবে নৈরাশ্যবাদের অতল ছুঁয়ে দেখছেন অবিরত,—আমরা কি পারছি সাহস করে তার মুখোমুখি দাঁড়াতে?
এর পালটা ওই-যে শব্দই ব্রহ্ম বলে মরমিকরণ করছি হামেশা, শান্ত ও ইতিবাচক প্রতিরোধের কথাটথা আওরাচ্ছি হামেশা, রক্তমাংসে জীবনকে উষ্ণ ও ক্লেদাক্ত ভাবছি বা লড়াই করছি দাঁত চেপে… এখন, এসব প্রতিরোধকে কি ভাবনাযোগ্য করার মতো গভীরতা খুঁজে নিচ্ছে আমাদের ভাষা? আমাদের এহেন মরমিকরণের মধ্যে কি মরণবিকার ও একঘেয়ে ক্লান্তির ভার নেই? নৈরাশ্য কি গায়েব সেখানে? প্রশ্নগুলো মনে জাগছে বটে!
স্পিরিচুয়াল অ্যাবসেন্স ইউরোপে বড়ো সমস্যা। যেটি নিয়ে চর্চা হয়েছে অনেক। যেখানে, এর পেছনে সক্রিয় রাজনৈতিক বাস্তবতাকে ইউরোপের সাহিত্য প্রতিফলিত করেনি, এটি কি বলা যাবে? ক্রাসনাহোরকাইয়ের স্যাটানট্যাঙ্গো বা তাঁর গল্প ইত্যাদি যেগুলো আমরা একটু-একটু করে জানছি, সেখানে তো ওই রাজনীতির পরিণাম প্রত্যক্ষ। যেখানে, রুশ বাস্তবতাবাদী ন্যারেটিভে একে প্রকাশের স্তর ইউরোপ অনেক আগে পেরিয়ে এসেছে। যান্ত্রিক যাপনের ধকল সেখানে সত্তার যাপন ও শূন্যতার বোধি মিলে একধরনের অর্থহীনতাকে অতিকায় করেছে, এবং তা অনিবার্য ও যৌক্তিক ছিল;— এবং সেখানে জয়েসরা একটি ট্রাডিশনের মতো তাঁদের ওপর চেপে বসেছেন। তাদের জায়গা থেকে ভাষা-আঙ্গিকটা সুতরাং ভাবনা হয়ে দাঁড়িয়েছে।
ডিস্টোপিয়ান সমাজের দিকে গমনের ক্ষণে ভাবনা অপসৃত হয় বা ভাবনার পরিসর মরে যাওয়াটাই বড়ো ভাবনার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। জেমস জয়েসরা অতটা যেতে পারেননি তখন। যে-কারণে ভাষার কাব্যিক সৌন্দর্যের মধ্য দিয়ে একধরনের অবোধ্য স্বপ্নময়তাকে তাঁরা ধারণ করেছিলেন। কুমার চক্রবর্তী যেটিকে প্রেইজ করছেন তাঁর বক্তব্যে, কিন্তু লাসলো ক্রাসনাহোরকাই বা সারামাগোকে তিনি মেনে নিতে পারছেন না। ভাবনাশূন্য হয়ে পড়ার ভাবনাকে যে এঁনারা রূপ দিচ্ছেন, সেটি মনে হচ্ছে তাঁর বিবেচনায় গুরুত্ব রাখে না।
আজকে লেসলো ক্রাসনাহোরকাইদের সঙ্কট জয়েসদের চেয়েও ব্যাপক। তাঁদের জন্য সভ্যতা কোনো কেন্দ্র অবশিষ্ট রাখেনি;—এমনকি আধ্যাত্মিকতাও। ভাবনার মরণকে যে-কারণে তাঁরা ভাষায় ধরছেন অবিরত। যার ফলে আমাদের সঙ্গে তাদের তুলনা অবান্তর ও অপ্রাসঙ্গিক এক্ষেত্রে।

আমাদের এখানে এসব বিমানবিক বোধি ও চাপ অতটা ব্যাপক নয় এখনো অথবা আমরা এখনো একধরনের আধ্যাত্মিক মরমি অনুভব দিয়ে একে প্রতিহত করে যাই। এদিকটা কুমার মনে হলো ভেবে দেখেননি। ইউরোপের সাহিত্য ‘ভাবনা’কে গিলে নিচ্ছে ভাষার জয়েসীয় সৌন্দর্যের পুনরাবৃত্তির মধ্য দিয়ে;—এই ধরনের রায়ে সরলীকরণ তাই চোখে লাগছে। লাসলো ক্রাসনাহোরকাই হয়তো ভাষিক আঙ্গিকের প্রশ্নে জয়েসদের পুনরাবৃত্তি করছেন, এবং সে-কারণে তাঁকে ক্লিশে ও অনুবাদ-অযোগ্য বলা যেতেই পারে, কিন্তু তাঁর রচনায় জীবনের সংক্ষুব্ধ দিকগুলো নেই… এরকম ভাবাটা উদ্ভট শোনাচ্ছে কানে। তাঁরা যে-বিমানবিক বোধিকে ক্রমাগত অনুশীলন করছেন, তার মধ্যে ভাবনাবীজ ও দার্শনিক মীমাংসা খোঁজার তাড়না… সবটাই রয়েছে। আমাদের সঙ্গে তা মিলছে না;—তফাত এটুকুই।
দ্বিতীয় যেটি, ইউরোপ ভাষারাজনীতিতে নিজের অধিপত্য ধরে রাখতে এরকম ভাষা তৈরি করছে বলে কুমার দাবি করেছেন,—এর যৌক্তিকতা কিছু বোঝা গেল না! তাহলে, লাতিন ও আফ্রিকান সাহিত্য নোবেল পেত না। আমরা এটি বলতে পারি,—আফ্রিকান বা লাতিন বাস্তবতাকে ইউরোপ তার বাস্তবতায় প্রবেশ ও ব্যবহাযোগ্য ভাবে না। আমরা যেমন ইউরোপকে সকলক্ষেত্রে একসেস দেওয়ার কথা চিন্তাও করতে পারি না। সেটি করতে গেলে অনুকরণসর্বস্ব বাকোয়াজি জন্ম নেবে।
কুমার চক্রবর্তী প্রশ্ন তুলেছেন। ভাববার মতো প্রশ্ন, তবে এর মধ্যে উঁকি দিচ্ছে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের পুরোনো বিরোধ;—যেখানে এরা আজো একজন আরেকজনকে বোঝা ও বিনিময়ের জায়গায় সবল দাঁড়িয়ে নেই। পাশ্চাত্য এখনো মোটাদাগে প্রাচ্যকে রোমান্টিসাইজ করে। নয়তো প্রাচ্যের ভাষা ও বয়নরীতির আগামাথা কিছু তারা ধরতে ও বুঝতে পারে না। ট্রাশ ভেবে বাতিলও করে হামেশা! প্রাচ্য আবার অনেকসময় অন্ধের মতো পাশ্চাত্য ন্যারেটিভকে নিজের ভাষায় ধার করতে যেয়ে অনুকরণে নিঃস্ব হয়। এটি সমস্যা। এবং এখানে এসে আমরা দেখি, দুই গোলার্ধ কমবেশি পুরাতনের পুনরাবৃত্তিতে অনেকটা নিঃস্ব।
সুতরাং, প্রাচ্যের দরকার আছে ক্রাসনাহোরকাইদের ভাষাসৃষ্ট বয়ানের কার্যকারণ অনুভব করা ও এর থেকে উপযোগী অংশ শুষে নেওয়ার। ইউরোপের দরকার আছে,—প্রাচ্যের একজন কমলকুমার মজুমদারের মতো লেখকের ভাষারীতিতে তৈরি হতে থাকে আধ্যাত্মিক সংবেদ ও স্থানিকতার রস উপলব্ধি করা। এখানে জাজমেন্টাল না হওয়াটাই মনে হচ্ছে অধিক ফলদায়ক।
. . .
. . .



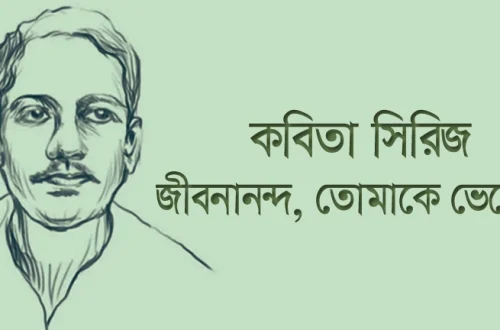


One comment on “বিট অ্যারাউন্ড দ্য বুশ!”