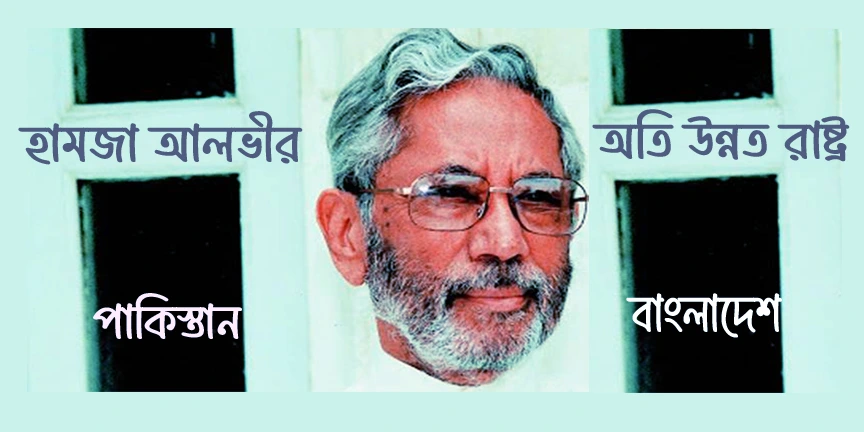দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের নিয়তি-মানচিত্র কেন বারবার ঘনঘটার সম্মুখীন হয় সেটি নিয়ে ব্যাখ্যা ও বাদানুবাদের অভাব নেই। হামজা আলভীর ব্যাখ্যাকে তার মধ্যে ব্যতিক্রম গণ্য করা যেতে পারে। পাকিস্তানের এই প্রখ্যাত মার্কসবাদী তাত্ত্বিককে ঘিরে বাংলাদেশের বিদ্বানমহল একসময় বেশ আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। ভারত ও পাকিস্তানে তিনি যদিও গোড়া থেকে সুপরিচিত। গুরুত্ব সহকারে পঠিত হয়ে আসছেন এখনো। বাংলাদেশে তাঁকে ঘিরে আগ্রহ তৈরি হয় আট-নয় দশকের গোড়ায়। স্মরণশক্তি যদি প্রতারণা না করে তাহলে রাষ্ট্রক্ষমতায় পাকিস্তানের সামরিক বাহিনির ভূমিকা ও পরিণাম বিষয়ে তাঁর একখানা বই উক্ত দশকসীমায় প্রকাশিত হয়। জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ অথবা ইউপিএল থেকে সম্ভবত বইটি বেরিয়েছিল। অনুবাদকের নাম এখন আর মনে পড়ছে না।
পাকিস্তান কেন এবং কীভাবে সামরিকচক্রে পড়ে ক্রমাগত পর্যদুস্ত হলো, তার ভিন্নধর্মী ব্যাখ্যা ছিল বইটির সম্পদ। তবে উপনিবেশ পরবর্তী পাকিস্তানে রাষ্ট্রকাঠামোর গতিবিধি ব্যাখ্যায় নৈপুণ্য হামজা আলভীর সুখ্যাতির বড়ো কারণ ধরা যেতে পারে। পাকিস্তান ও বাংলাদেশের উত্তর ঔপনিবেশিক সমাজের গঠন ও পরিণাম (The State in Post-Colonial Societies Pakistan and Bangladesh) আলোচনায় অতি উন্নত রাষ্ট্রের (Overdeveloped State) তত্ত্ব নিয়ে তিনি হাজির হলেন তিনি। দক্ষিণ এশিয়ার ভৌগলিক পরিসীমায় চিহ্নিত রাষ্ট্রপুঞ্জের মধ্যে বিশেষভাবে পাকিস্তান ও বাংলাদেশকে কী কারণে অতি উন্নত রাষ্ট্র ভাবছেন, অর্থাৎ এর নেপথ্যে যেসব যুক্তি তিনি তুলে ধরেন,—সেগুলো সংগতকারণে আলোচনার জন্ম দিয়েছিল।
পোড়খাওয়া মার্কসবাদী হামজা আলভীর পর্যবেক্ষণ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ কতিপয় প্রবণতা ঘুরেফিরে অকাট্য হতে দেখা যায়। ইংরেজ শাসনের খোয়ারি কেটে যাওয়ার পর কেমন চলছে পাকিস্তান? ভারত ও বাংলাদেশের অবস্থা সেখানে কেমন? সামাজিক বিন্যাস কি অতীতছকে ঘুরছে এখনো? নতুন পুনর্বিন্যাস কি দেখছি সেখানে? কৃষিপ্রধান সমাজকাঠামোয় কৃষির বৈপ্লবিক রূপান্তর কি আদৌ ঘটেছে? কৃষকসমাজ কি আরো বেশি প্রান্তিক ও শোষণের নতুন মাত্রায় গমন করছে অবিরত? এসব জিজ্ঞাসাকে হামজা আলভী তাঁর পর্যবেক্ষণে অবিচ্ছেদ্য করে নিয়েছিলেন। পাকিস্তান ও বাংলাদেশের উত্তর ঔপনিবেশিক সমাজ নামক বইয়ে যার গাঠনিক বিবরণ তিনি পেশ করেছেন।
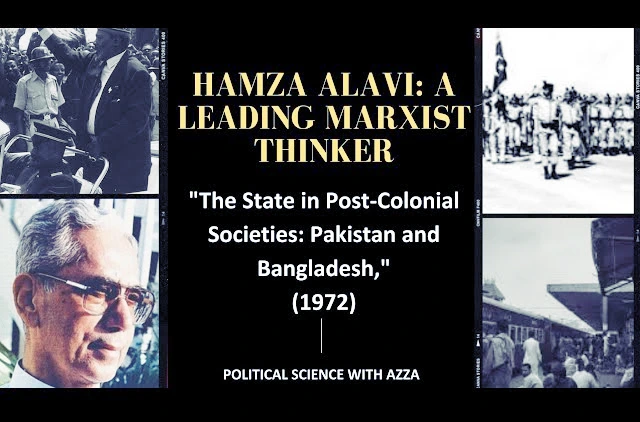
আলভীর বইটিকে বিদ্বানমহল অভিনব ও ব্যতিক্রম বলে রায় দিয়েছিলেন তাৎক্ষণিক। বইটি পরে বাংলায় ভাষান্তরিত হয়। এনামুল হাবিব সম্ভবত তর্জমা করেছিলেন। ইংরেজি সংস্করণ পাঠ করলেও বাংলা ভাষান্তর পাঠের সুযোগ হয়নি। সে যাইহোক, পোড়খাওয়া মার্কসবাদী হিসেবে পরিচিত পেলেও আলোচিত বইয়ে সংকটের কারণ ব্যাখ্যায় হামজা আলভী বিপরীত পথে হেঁটেছেন। পাকিস্তান ও বাংলাদেশের রাষ্ট্রকাঠামো বা তার বিবর্তনকে অতি উন্নত রাষ্ট্র (Overdeveloped State) নামক ধারণার আলোয় সংজ্ঞায়িত করার মাধ্যমে তিনি দেখালেন,—দক্ষিণ এশিয়ার উত্তর-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রসমূহ পশ্চিমা ধাঁচের পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোর মতো স্বাভাবিক পথে গড়ে ওঠেনি।
ঔপনিবেশিক আমলে গড়ে ওঠা আমলাতান্ত্রিক ও সামরিক কাঠামো শক্তিশালী হয়ে ওঠার ফলশ্রুতিতে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অসরকারি পুঁজিপতিরা প্রভাব বিস্তারে ব্যর্থ হয়। হামজা আলভীর এই ডিমার্কেশন ছিল গুরুত্বপূর্ণ। আমরা কমবেশি জানি, পশ্চিমা দেশগুলোয় পুঁজিবাদের বিকাশপর্বে বুর্জোয়া শ্রেণি যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করেছিল। রাষ্ট্র গঠনের ক্ষেত্রে বিকাশমান বুর্জোয়া শ্রেণির ইচ্ছা ও স্বার্থ সেখানে প্রতিফলিত হয়েছিল। মার্কস যে-কারণে বুর্জোয়া শ্রেণির পরিণতি বিকাশের মধ্যে পুঁজিবাদের মরণঘণ্টা নিহিত বলে রায় ঠুকতে দেরি করেননি।
পাকিস্তান (এবং এশিয়া ও আফ্রিকার) রাষ্ট্র আমলাতান্ত্রিক কাঠামোছকে বিকাশ লাভ করায় অর্থনীতিসহ রাষ্ট্র পরিচালনায় বুর্জোয়া শ্রেণি আজো চালকের আসনে বসতে পারেনি। রাষ্ট্র পরিচালনার শক্তি বা ম্যান্ডেটের কোনোটাই তাদের কপালে জোটে না। আলভী দেখাচ্ছেন,—পাকিস্তানের রাষ্ট্রব্যবস্থা ইংরেজদের রেখে যাওয়া ঔপনিবেশিক শাসনের উত্তরাধিকার আজোবধি বহন করছে। তারা যে-প্রশাসনিক কাঠামো রেখে গেল সেটি পরবর্তীতে পাকিস্তানে রাষ্ট্র ক্ষমতা পরিচালনার নিয়ামক হয়ে দাঁড়ায়। দেশটি মূলত সামরিক-আমলাতান্ত্রিক জোটের (Military-Bureaucratic Oligarchy) দ্বারা শাসিত হয়েছে। বছরের-পর-বছর ধরে এরকম শাসন জারি থাকার ফলে গণতান্ত্রিক কাঠামো জখম হওয়া ছাড়া দ্বিতীয় কোনো ফলাফল আসেনি।
হামজা আলভী তাঁর বইয়ে ব্যাখ্যা সহকারেই বলছেন,—ভিন্নপথে গমনের সম্ভাবনা থাকলেও একটি স্বাধীন ভূখণ্ড হিসেবে বাংলাদেশ যাত্রালগ্নেই হোঁচট খায়। পাকিস্তানের অনুরূপ কাঠামো উত্তরাধিকারসূত্রে সে বইছে সেখানে। সম্ভাবনা বলতে হামজা এখানে সদ্য স্বাধীনতাকে বোঝাচ্ছিলেন। তাঁর বইটি বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পরের বছর বের হয়। কথা মিথ্যে নয়,—জনমুখী গণতান্ত্রিক চেতনার একটি ধারা মুক্তিযুদ্ধ ও নব্বইয়ে সামরিক শাসনের পতন ঘটানোর মধ্য দিয়ে এখানে তৈরি হয়েছিল।
বাংলাদেশের নতিজা পাকিস্তানের সঙ্গে অভিন্ন হওয়ার বড়ো কারণ,—আমলাতন্ত্র ও সামরিক বাহিনীর সক্রিয়তা সমাজের ভেতরে প্রোথিত থাকায় উভয়ের সংস্কার ঘটাতে রাজনৈতিক দলগুলো ব্যর্থ হয়। আলভী এখন বেঁচে থাকলে, ধারণা করি বাংলাদেশকে খোদ পাকিস্তানে বিকশিত মিলিটারি, ব্যুরোক্রেসি ও মোল্লাদের সমাবেশে গঠিত অলিগার্কের কার্বন কপি বলে রায় ঠুকতেন। এরকম কাঠামোয় গণতন্ত্র অকার্যকর হতে বাধ্য। আর বামপন্থার পক্ষে শ্রেণিসচেতন রাজনীতির বাতানুকূলে গমন দুরূহ। বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে বাম রাজনীতির ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে যেটি ফিরে-ফিরে সত্য প্রমাণিত হয়েছে।
বাংলাদেশে বামরা আবারো ইসলামকে নিজের রাজনৈতিক কৌশল ও বয়ানে গুরুত্ব দিতে গিয়ে উগ্র মৌলবাদের কাছে মানসম্মান খুইয়েছেন। কারণ বড়ো কিছু নয়,—তাদের লড়াই করার কৌশল ভুলে ভরা থেকেছে তখনো, এবং এখনো তাতে হেরফের ঘটেনি একরতি। সামরিক ও বেসামরিকতন্ত্রের কাছে জিম্মি রাষ্ট্রব্যবস্থার সমালোচনা যে-কারণে বামরা কার্যকর উপায়ে করতে পারে না। উগ্রবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের রাজনৈতিক ভাষা তৈরির পরিবর্তে সেকুলার ও ননসেকুলার স্টেটের দ্বন্দ্বে তারা গমন করেছেন, যার পরিণাম চোখের সামনে সকলে দেখছে এখন।
হামজা আলভী মার্কসবাদী হলেও তাঁর বিশ্লেষণ ঐতিহ্যবাহক মার্কসবাদী শ্রেণিসংগ্রাম নিয়ে রকমারি যত তত্ত্ব, তার থেকে পৃথক মোড় নিয়েছে। মূল মার্কসবাদী ধারণায় বলা হচ্ছে, রাষ্ট্র সাধারণত অর্থনৈতিক শক্তির প্রতিফলন, যেখানে এক শ্রেণি অন্য শ্রেণির ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করবে। আলভী দেখিয়েছেন,—পাকিস্তানের জলবায়ুতে রাষ্ট্র স্বতন্ত্র শক্তিকেন্দ্রে পরিণত হিতে সময় নেয়নি। স্বাভাবিক পুঁজিবাদী সমাজের ন্যায় কেবল বুর্জোয়া শ্রেণির স্বার্থ রক্ষায় তাকে আমরা খাটতে দেখি না। সামরিক ও আমলাতান্ত্রিক অভিজাত শ্রেণির লোকজন এখানে মূল চালিকাশক্তি বা নিয়ন্ত্রক হিসেবে প্রাধান্য বিস্তার করেছেন। তাদের ভূমিকা ও সক্রিয়তাকে নিষ্ক্রিয় করার মতো পরিস্থিতি আজো তৈরি হয়নি।
সমাজ ও অর্থনীতির চালক হিসেবে বণিকনির্ভর সুগঠিত বুর্জোয়া শ্রেণি পাকিস্তান ও বাংলাদেশে গড়ে না উঠায় এখানকারর শ্রেণিশোষণের ছক বা এর বিরুদ্ধে লড়াই সর্বদা ঘোলাটেই থেকে গেছে। হাসিনা আমলে ব্যবসায়ীদের দাপট আমরা দেখেছি, তবে খেয়াল করা প্রয়োজন,—ব্যবসায়ী শ্রেণিটি সেখানে মার্কসকথিত পুঁজবাদী শক্তিতে নিজেকে রূপান্তরিত করতে সক্ষম ছিল না। সামরিক ও বেসামরিক আমলাতন্ত্রকে নেপথ্য চালিকাশক্তি মেনে নিয়ে তারা কেবল লুম্পেনে পরিণত করেছে নিজেকে। আর গেল তিরিশ বছরের ছকে এই অলিগার্কিকে পূর্ণতা দিতে মোল্লারা যুক্ত হয়েছেন। আলভীর অতি উন্নত রাষ্ট্রের পরিহাসকে যেটি বাংলাদেশে সত্য প্রমাণ করছে।
হামজা আলভীর ব্যাখ্যা মার্কসবাদী রাষ্ট্রতত্ত্বের দুটি প্রধান ধারা ধ্রুপদি মার্কসবাদ ও গ্রামশির হেজিমনি তত্ত্বের মাঝামাঝি অবস্থান করছে ধরা যায়। তিনি দেখাচ্ছেন,—রাষ্ট্র সবসময় নিছক শ্রেণির হাতের পুতুল নয়, বরং তার নিজস্ব গাঠনিক শক্তি বড়ো ভূমিকা পালন করে। ব্যাখ্যার সারার্থ আমাদের দেখায় :
দক্ষিণ এশিয়ার উত্তর-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলো পুঁজিবাদী সমাজ বিকাশের অপরিহার্য ধাপ অনুসারে গড়ে ওঠেনি। ঔপনিবেশিক শাসনের জের ধরে তাদের রাষ্ট্রকাঠামো অতি উন্নত হয়ে গেছে।
পাকিস্তানে সামরিক-আমলাতান্ত্রিক জোট রাষ্ট্রশক্তির মূল ধারক হয়ে ওঠায় গণতান্ত্রিক শক্তিগুলো আজো সবল হতে পারছে না।
বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও আমলাতান্ত্রিক প্রভাব কাজ করেছে, যদিও এখানে গণতান্ত্রিক চেতনা বিকাশের সুযোগ ছিল, কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলোর হঠকারিতায় তা বিনষ্ট হয়েছে।
হামজার বিশ্লেষণকে কাজেই বর্তমান বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের রাজনৈতিক-সামাজিক প্রেক্ষাপট বোঝার পক্ষে জরুরি মানা যেতে পারে। আফসোস, আমাদের বামপন্থী শক্তি একজন দীক্ষিত মার্কসবাদীর ভিন্নমাত্রিক চিন্তন থেকে কোনো শিক্ষা নিতে পারেনি। উল্টো বিভ্রান্তির কুম্ভিপাকে ঘুরপাক খেয়ে বিকল্প রাজনৈতিক ভাষা হয়ে ওঠার শেষ সম্ভাবনায় পেরেক ঠুকেই চলেছেন।
. . .
. . .