. . .
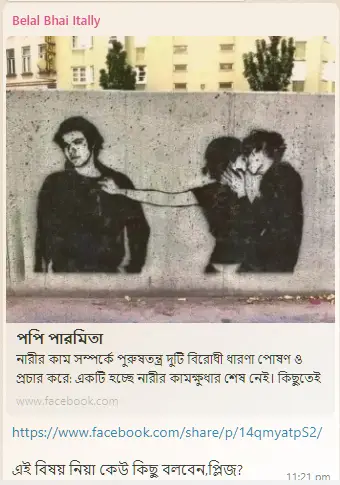
ভালো টপিক। হুমায়ুন আজাদের নারী থেকে কোট করেছেন পপি পারমিতা। আপনার ধারণা আগে জানতে আগ্রহী বেলাল ভাই। এই বিষয়ে প্রত্যেকের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও অভিজ্ঞতা রয়েছে। আপনার, আমার… সকলের। যেখানে আমার ধারণা, সুনির্দিষ্ট প্যারামিটার সেট করা কঠিন। কাজেই আপনার ভাবনাটা জানতে চাই। ওইটা ধরে নাহয় আমরা সামনে আগাব।
. . .
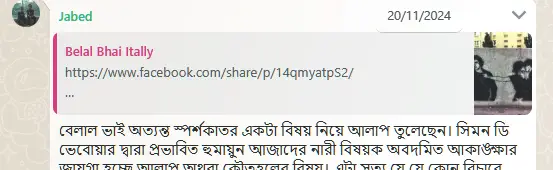
বেলাল ভাই স্পর্শকাতর আলাপ তুলেছেন। সিমন দ্য বেভোয়ার প্রভাবিত হুমায়ুন আজাদের নারী কেন্দ্রিক অবদমিত আকাঙ্ক্ষার বিষয়টি আলাপ ও কৌতূহল জাগিয়ে তোলে। হুমায়ুন আজাদ বাংলা ভাষায় নারী বিষয়ক চিন্তায় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাক্তি। তাঁর দ্বিতীয় লিঙ্গ ও নারীতে সবিস্তারে বিষয়গুলি উঠে এসেছিল।
এখন একটি মাত্র কোটেশন থেকে মন্তব্য হুমায়ুন আজাদ ও নারী… কারো প্রতি সুবিবেচনাপ্রসূত হবে না। সামগ্রিক পাঠের দরকার রয়েছে। পুরুষতন্ত্রকে মাথা থেকে আগে সরাতে হবে আমাদের। ধর্মীয় ও সামাজিক যেসব মূল্যবোধ, যার ভিত্তি আবার পুরুষতন্ত্র, তাকেও খারিজ করা লাগবে। এমন এক জায়গা থেকে পাঠে যাওয়া দরকার, যেখানে ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষার দিক থেকে নারী পুরুষে কোনো ভেদ নেই। ধর্মীয় ও সামাজিক বিধিনিষেধ ঘেরা এই-যে পুরুষতান্ত্রিক গণ্ডিতে বসে প্রশ্ন তোলা উভয় পক্ষের জন্যই বিব্রতকর মনে করি।
. . .
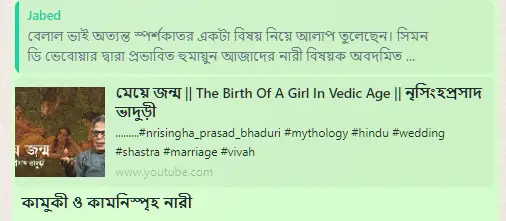
বেলাল ভাইয়ের তোলা টপিকটা আসলেও ইন্টারেস্টিং জাভেদ। জানি না উনি বা অন্যরা এই ব্যাপারটি কীভাবে দেখেন। বেলাল ভাইকে বলছি উনার মত জানাইতে। বাবুল ভাইসহ যারা আছেন, আমার ধারণা, সকলের এই ব্যাপারে নিজস্ব মত থাকবে। মিল এবং বেমিল থাকবে সেখানে। এখন বেলাল ভাই হয়তো উনার মতো করে বলবেন পরে। আপাতভাবে আপনার বক্তব্যপাঠে একটি জিজ্ঞাসা মাথায় ঘুরতেছে। সেটি হইল, নারী কামশীতল বা কামনিস্পৃহ… এই ধারণা সমাজে আছে। আবার নারীর কামক্ষুধা প্রবল… এটিও আছে। এখন উভয় ভাবনার জড় কোনখানে গাঁথা?
ইউরোপ-আমেরিকার দেশগুলায় কনসেপ্টটা মনে হয় না এরকম আছে এখন, কিন্তু ওরিয়েন্টাল বলয়, বিশেষ করে ভারতবর্ষ বা মুসলমান শাসিত আরব দেশগুলায় এইটা ব্যাপকভাবে এখনো সক্রিয়। এর পেছনে কোন কোন উপাদানকে আমরা মুখ্য ধরব? ধর্ম? সামাজিক রীতিনিয়ম? সংস্কৃতি? রাষ্ট্রীয় বিধান ও শিক্ষার ধরন? ঐতিহ্য? ঠিক কোনটা? নাকি টাবু বা সংস্কারটা এখানে প্রবল ভূমিকা রাখতেছে?
বেলাল ভাইয়ের সুবাদে হুমায়ুন আজাদ আবার প্রাসঙ্গিক হইতেছেন। উনার নারী বা সিমন দ্য বেভোয়ারের দ্য সেকেন্ড সেক্স -এর বাংলা ভাষান্তর স্মৃতিতে ফেরত আসতেছে পুনরায়। ওসব নিয়ে আলোচনা হইতে পারে। তবে আরেকটা জিনিস মনে হইল, বাৎসায়নের কামসূত্র তো এমন এক সময়ে রচিত, যখন নারী ও পুরুষের মেলামেশা এবং যৌনমিলনে সামাজিক টাবু প্রবল ছিল না, এখন যেমন আছে।

তো সেখানে রতিসুখের বিচিত্র তরিকা বাতলানোর পথে বাৎসায়ন কিন্তু নারী প্রজাতির দৈহিক গঠনের উপ্রে ফোকাস করতেছেন। ওই পদ্মিনী, চিত্রিণী, শঙ্খিনী, হস্তী… অনেকটা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের মতো বর্ণবিভাজনের তরিকায় কামক্ষুধায় কোন প্রজাতির নারী কেমন তার সবিস্তার উনি লিপিবদ্ধও করছেন।
অজন্তা এবং ইলোরার গুহাচিত্র বা ভাস্কর্যেও আমরা বিচিত্র রতিআসনের পরিচয় পাইতেছি। তার মানে প্রাচীন ভারতবর্ষে নারী এবং পুরুষের কামক্ষুধার বিষয়টি অনেকটাই ওপেন স্পেস ছিল। মহাভারত বা রামায়ণে গেলে সেইটা পাবো। পুরাণের কথা বাদই দিতেছি। সেখানে দেবতাদের কেচ্ছার তো অন্ত নাই। সবটাই রগরগে। দেবতার মানবায়ন-এ নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী এসব নিয়া বিস্তর আলোকপাত করছেন একসময়। অন্যরাও করছেন। তো এই জায়গা থেকে কেবল পুরুষতন্ত্রের কারণে কি কামক্ষুধার্ত নতুবা কামনিস্পৃহ নারীর ধারণা গড়ে উঠতেছে? নাকি অন্য কারণ আছে সেখানে?
. . .
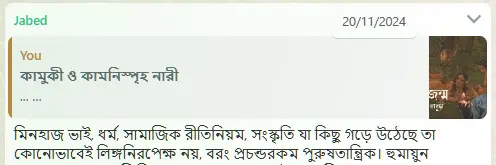
মিনহাজ ভাই, ধর্ম, সামাজিক রীতিনিয়ম ও সংস্কৃতিসহ যা-কিছু গড়ে উঠেছে সেগুলো কোনোভাবেই লিঙ্গনিরপেক্ষ নয়, বরং প্রচণ্ড পুরুষতান্ত্রিক। হুমায়ুন আজাদের যে-কথাটি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে সেই বাক্যটি খেয়াল করার মতো, যেখানে উনি বলছেন,- একাধিক পুরুষের সাথে কামসংসর্গে তার আপত্তি নেই, তবে পুরুষতন্ত্রের ভয়ে অধিকাংশ নারীই তা স্বীকার করে না।
পুরুষতন্ত্র এমন এক বাধা, আকাঙ্ক্ষা যদি জন্ম নিয়েও থাকে, নারী সেটি প্রকাশ করে না। ফ্রয়েডের ভাষায় অবদমন তৈরি করে নিজে। এখন নারীতান্ত্রিক সমাজেও পুরুষের একই অবস্থা হইত। ফলে এক্ষেত্রে সুবিবেচনার জায়গা বলতে সকল আরোপিত ভাবনা থেকে সরে এসে বিষয়টির দিকে তাকানো। প্রাচীন ভারতে মহাভারত রামায়ণ-এর কালপর্বে কিছুটা ওপেন স্পেস থাকা সত্ত্বেও পুরুষতন্ত্র প্রবল ছিল। কামসূত্রও তো পুরুষেরই হাতে সৃষ্ট। ওরিয়েন্টাল বলয়ও উক্ত প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি।
. . .
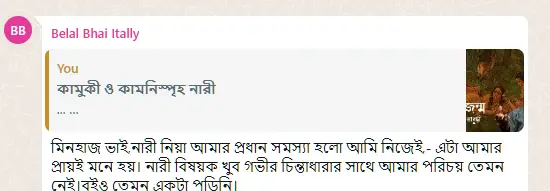
মিনহাজ ভাই, নারী নিয়া আমার প্রধান সমস্যা আমি নিজেই,- এটা আমার প্রায়ই মনে হয়। নারী বিষয়ক খুব গভীর চিন্তাধারার সাথে আমার পরিচয় তেমন নেই। বইও তেমন একটা পড়িনি। আজাদের বইটি হাতে আসে প্রকাশ হওয়ার সাথে সাথে, কিন্তু বইটি পড়ে তখন খুব বেশি উপলব্ধি করার মতো বয়স বা মানসিকতা – কোনোটাই ছিলো না। এমনিতে কওমি মাদ্রাসায় পড়ার কারণে হাতেগোনা নিকটাত্মীয় নারী ছাড়া কারো সংস্পর্শে আসিনি বললেই চলে, তবে অফুরন্ত কৌতূহল ছিল। ফ্রয়েড ও অন্যান্যদের পাঠ করার পর তার কারণও জানতে পারি।
শৈশবের ঘর পেরিয় যখন যৌবনে এলাম – এসে দেখি আমরা পুরুষরা নারীকে নিয়া একটা মহা বেরাছেরা অবস্থায় আছি এবং অতীতেও ছিলাম। তখন কিছু বামপন্থী বন্ধুরাই দেখতাম, নারীকে নিয়ে একটু মুক্তপরিসরে আলোচনা করতে আগ্রহী, আর সামান্য কজন সাংস্কৃতিক কর্মী। তারাও-যে নারী নিয়ে খুব স্বচ্ছ ধারণা রাখতেন তা আগেও মনে হয়নি, এখনো না। নারী বিষয়ে অনেককে প্রশ্ন করে মনের মতো উত্তর না পাওয়ার বেদনা আমার অনেক পুরোনো।
বিশ্বরাজনীতির মতো বিশ্ব নারীবাদ নিয়েও কোথাও যেন একটা ঘাপলা রয়ে যাচ্ছে বলে প্রায়ই মনে হয়। ইউভাল নোয়া হারারি সাপিয়েন্সসহ আরো যেসব লেখক মানবসমাজের কথা বলতে গিয়ে নারীর উথান-পতনের গল্প ও রপরেখা আমাদের সামনে তোলে ধরেন,- তাতে অনেক কিছু জানা যায় সত্য, কিন্তু তারপরেও ভিতরে কী একটা খচ্খচানি চলতে থাকে।
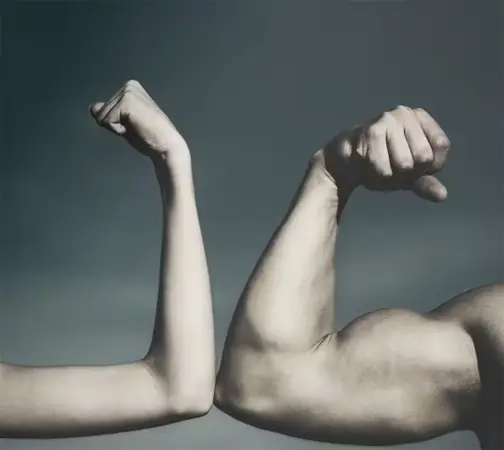
প্রশ্ন হল, আমরা চাঁদে চলে গেলাম সেই কবে, আর আমার পাশের নারী এখনো আমার কাছে অনেকটাই রহস্যাবৃত, কখনো উদভ্রান্ত আবার কোথাও-কোথাও সবকিছু থাকার পরেও উদবাস্তু থেকে যাচ্ছে কেন? হ্যাঁ, ইউরোপে নারীরা অনেকটা স্বাধীন। অর্থ-বিত্ত-শিক্ষায়, সৃজন ও মতপ্রকাশে তারা স্বাধীন। তারপর কী? এতকিছুর পরেও একজন ইউরোপীয় পুরুষ নারীকে কোন দৃষ্টিতে দেখে? মানবিক দৃষ্টিতে দেখে কি? যদি দেখে, তবে তাদের সংখ্যা কত পার্সেন্ট হবে?
আর, নারীকে যদি তারা পণ্য মনে করে, তাহলে কেন করে? সঠিক শিক্ষার অভাবে করে কি? এক্ষেত্রে সঠিক শিক্ষা জিনিসটা কী? কী কারণে আজো একজন মার্কিন নারী প্রেসিডেন্ট আমরা পেলাম না? সবকিছুর মতো এখানেও যৌক্তিক ইতিহাস আছে জানি। তারপরও আরো একবার নারীর সামগ্রিক দিক নিয়ে কেউ আলোচনা করলে আমার উপকার হয়।
. . .




