শর্ট ইন্ট্রো : সময়ের মেধাবী ভাবুক বুুয়িং-চুল হান পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় মানবসত্তার অবচয়কে মরণদশায় একীভূত করে দেখেছেন। দেখার কার্যকারণ তাঁকে নিয়ে থার্ড লেন হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের নেটালাপ-এ অবদায়ক মোস্তাফিজুর রহমান জাভেদের প্রাঞ্জল ও ধারাবাহিক আলাপে চোখ রাখলে পাচ্ছি বৈকি। পুঁজিবাদ ও মৃত্যুবাসনাকে একসুতোয় গেঁথে রচিত নিবন্ধ Capitalism and the Death Drive-এ দগ্ধসমাজে বিয়ং-চুল হান বর্তমান মানবসমাজ কীভাবে ন্যাক্রোফিলিয়ায় (Necrophilia) আক্রান্ত তা দেখানোর চেষ্টা করেছেন। ন্যাক্রোফিলিয়া বলতে এতদিন মৃতদেহের প্রতি কারো যৌনআসক্তি বা বিকারকে আমরা বুঝে এসেছি। হান এটিকে পুঁজিবাদ সৃষ্ট মরণফাঁদ হিসেবেও দেখছেন;—যার পাল্লায় পড়ে মানব-সমাজ জম্বিতে পরিণত হয়েছে বললে খুব একটা অত্যুক্তি হবে না।
এ-যুগের মানুষ নামমাত্র বেঁচে থাকে। নামমাত্র বেঁচে থাকা পঙ্গপালের সঙ্গে মৃতের ফারাক করা কাজেই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে ক্রমশ। পুঁজিবাদের পাতা একের-পর-এক মরণফাঁদে পা দিয়ে বসায় মানবজাতিকে কবর থেকে উঠে আসা মৃতদের সঙ্গে তুলনা করা যুক্তিসংগত বলেই মানছেন বিয়ং-চুল হান। মোস্তাফিজুর রহমান জাভেদ তাঁকে নিয়ে থার্ড লেন হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে এ-পর্যন্ত যেটুকু আলোচনা করেছেন, এখন সে-আলাপের পাঠউত্তর প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে ন্যাক্রোপলিটিক্স (Necropolitics) ও ন্যাক্রোক্যাপিটালিজমের (Necrocapitalism) কথা তুলেছিলাম। উক্ত প্রসঙ্গে আরো কিছু কথা যোগ করা আশা করি অবান্তর হবে না। কথা আর না বাড়িয়ে তাহলে শুরু করি বরং…
. . .

প্রযুক্তি-সামন্তবাদের মতো ন্যাক্রোপলিটিক্স ও ন্যাক্রোক্যাপিটালিজমকে তাত্ত্বিক নিদান রূপে আমাদের সামনে হাজির করা হয়েছে। স্লাভয় জিজেক ও ইয়ানিস ভারোফাকিস যে-সমাজের নিদান তাঁদের লেখা বইপত্র ও তর্কালাপে তুলে ধরছেন অহরহ, সেখানে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রিত কাঠামোয় নজরবন্দি করার সম্ভাবনা অদূর ভবিষ্যতে কীভাবে আরো ব্যাপক হবে তার ছবিখানা পাচ্ছি। বিমানবিক সমাজে উত্তরণের প্রাথমিক ধাপ হিসেবে এর সঙ্গে মানুষকে হয়তো অভ্যস্ত করে তোলা হবে। পুঁজিবাদ কাজেই থাকছে না সেখানে। তার খোলনলচে পালটে দিতে এমন এক ব্যবস্থা গড়ে উঠবে, যাকে জেরেমি বেন্থাম ও মিশেল ফুকোর প্যানোপটিকনের (Panopticon) নিকটবর্তী কিছু ঠাউরে নেবে মানুষ!
একটি বৃত্তাকার কয়েদখানা, যেখানে কয়েদি নিজেও জানে না কে বা কারা তার ওপর নজর রাখছে, এবং রাখলে কীভাবে রাখছে সেটি। ভারোফাকিস ও জিজেক যে-কারণে হামেশা বহুজাতিক বিধাতার হাতে নিয়ন্ত্রিত প্রযুক্তিকে উন্মুক্ত করার বয়ান ঝাড়েন। এর জন্য যে-রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার প্রয়োজন পড়ছে তার রূপররেখা বিষয়ে দুজনের বক্তব্য যদিও এখনো অনেকটাই পরস্পরবিরোধী ও ঝাপসা। অন্যদিকে ন্যাক্রোপলিটিক্স পুঁজিবাদী বিকারের আপাত সর্বশেষ চিত্র আমাদের সামনে হাজির করছে;—যা হয়তো আগামীতে এর ভবিতব্য কেমন হতে যাচ্ছে, সেই আভাস রেখে যায়।
আফ্রিকার জলহাওয়ায় বেড়ে ওঠা ঐতিহাসিক ও রাষ্ট্রচিন্তক আচিল এমবেম্বে (Achille Mbembe), আর বঙ্গসন্তান শুভব্রত ববি ব্যানার্জির (Subhabrata Bobby Banerjee) নাম সেখানে উঠবেই। নতুন শতাব্দীর গোড়ায় এমবেম্বে ন্যাক্রোপলিটিক্স (Necropolitics) নামে একখানা বই বাজারে ছাড়েন। আফ্রিকা মহাদেশে জন্ম নেওয়ার কারণে যেসব তিক্ত অভিজ্ঞতার চাপ তাঁকে জীবনভর সইতে হলো, ন্যাক্রোপলিটিক্সকে এর সারনির্যাস ভাবা যেতে পারে। এমবেম্বে তাঁর বইয়ে এই ধারণায় উপনীত হলেন,—কেবল আফ্রিকা নয়, সমগ্র বিশ্ব রাজনৈতিক ক্ষমতায়ণের ফাঁদে বন্দি হয়ে আছে। মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে পারে এরকম রাষ্ট্র গঠনের বাহানায় রাজনৈতিক ক্ষমতায়ণকে সার্বভৌম শক্তির প্রতীক করে তোলা হয়েছে। রাজনৈতিক ক্ষমতার মধ্য দিয়ে জনকল্যাণ নিশ্চিত করার ভুয়া বয়ানকে কাজে লাগিয়ে কতিপয় মানুষ সেখানে বাদবাকিদের ওপর একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ কায়েম করছে প্রতিনিয়ত।
একটি দেশে নাগরিকরা কীভাবে জীবন কাটাবে তার সবটাই রাজনৈতিক ক্ষমতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত-নির্ধারিত হওয়ার ফলে গণতান্ত্রিক স্বাধিকার ও স্বায়ত্তশাসনকে উপহাস ভাবা ছাড়া উপায় থাকছে না। রাষ্ট্রকে রাজনৈতিক ক্ষমতায়ণের গুঁটি রূপে ব্যবহার করায় তার কোনো স্বকীয়তা ও সর্বজনীনতা পৃথিবীর কোথাও চোখে পড়ে না। পরিণাম স্বরূপ মানবদেহের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রাজনৈতিক ক্ষমতাকে ব্যবহার করতে পটু লোকজনের দখলে চলে গেছে। প্রতিটি দেশ এভাবে দুটি অংশে ভাগ হয়ে আছে। একটি অংশ হলো মৃত, এবং অন্য অংশটি জীবিত। মৃত অংশে যারা রয়েছে তারা জীবিত অংশের দ্বারা শতভাগ নিয়ন্ত্রিত ও নির্ধারিত।
যেমন ধরা যাক, রাজধানী ঢাকার উত্তর অঞ্চল বা উত্তর পাড়াকে বিবিধ কারণে আমরা ক্ষমতাকেন্দ্র হিসেবে বিবেচনা করি এখন। সেখানে জাতীয় সংসদ রয়েছে। সেনানিবাস আছে। বিদেশি দূতাবাস সার বেঁধে অবস্থান করছে। সমাজের বিত্তবান ও প্রভাবশালীর বিরাট অংশ উত্তর পাড়ার অভিজাত এলাকায় বাড়িঘর তোলে বসবাস করছেন। দেশ পরিচালনায় কোনো-না-কোনোভাবে সম্পৃক্তদের বৃহৎ অংশ উত্তরে কেন্দ্রীভূত। অঞ্চলটিকে সুতরাং রাজনৈতিক ক্ষমতায়ণের ঘাঁটি হিসেবে মানুষ বুঝে নিয়েছেন। এমবেম্বের ছক অনুসারে ঢাকায় অবস্থিত উত্তর পাড়া জীবিত ও অস্তিত্বশীল। অন্যদিকে উত্তর পাড়ার বাইরে শহর জুড়ে ছড়ানো অঞ্চলগুলো, এমনকি উত্তর পাড়ায় মাথা গুঁজে থাকা মিরপুর-মোহাম্মদপুর ছাড়াও বস্তিঅঞ্চলে যারা বসবাস করেন,—তারা কেউই ক্ষমতায়ণের অংশ না। উত্তর পাড়ায় সক্রিয় ক্ষমতাচক্র তাদেরকে শিকার করে অবিরত। অত্র অঞ্চলসীমায় যেসব মানুষজন কাজেই থাকছেন,—বাস্তবে জীবিত দেখালেও তারা আসলে মৃত!
এই লোকগুলোর দেহ নিজের নয়। উত্তরপাড়া সেই দেহের ওপর কায়েমি ঠিকাদারি নিয়ে নিয়েছে। মানবসমাজের বৃহৎ অঞ্চলকে এভাবে গোরস্থানে পরিণত করা হয়েছে। মানুষগুলো কেউ যেখানে জীবিত নেই। তাদেরকে আমরা কবর থেকে উঠে আসা জম্বি ভাবতে পারি। জম্বিদের ব্যবহার করে জীবিতরা যেখানে নিজের আয়ু বাড়িয়ে নিচ্ছে। সুতরাং রাষ্ট্র গঠনের রাজনীতিকে ন্যাক্রোফেলিয়া ভাবা যেতেই পারে। এই রাজনীতি মৃতদের নিয়ে রাজনীতি করে। রাষ্ট্র পরিচালনায় কে বসবে, কীভাবে বসবে, কেমন করে দেশ চালাবে ইত্যাদি যেভাবে ঠিক করে দেওয়া হয়, সেই ছক মেনে গোরস্থানবাসীরা স্রেফ ব্যবহৃত ব্যবহৃত ব্যবহৃত, এবং ব্যবহৃত হতেই থাকে। খেলাটিকে এমবেম্বে ন্যাক্রোপলিটিক্স ছাড়া ভিন্ন কিছু ভাবতে নাচার।
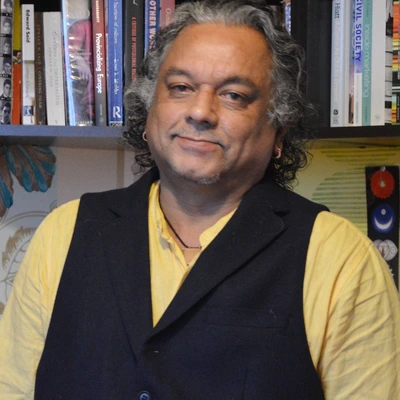
এমবেম্বে যেখানে দাঁড়ি টেনেছেন, শুভব্রত ববি ব্যানার্জি শুরুটা করেছেন সেখান থেকে। বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন ধরে ব্যবসা প্রশাসনের সবক দানে নিয়োজিত অধ্যাপক এমবেম্বের বই পড়ে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন প্রথম। যদিও ন্যাক্রোপলিটিক্সকে তিনি ভিন্নচোখ দিয়ে দেখেছেন। তাঁর মতে, বর্তমান যুগবিশ্বে রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক দল-গোষ্ঠী ইত্যাদি সমাজে কারা বেঁচে থাকবে আর কারা জম্বি হিসেবে পণ্যায়িত হবে ইত্যাদি নির্ধারণের মাপকাঠি নয়। সাংগঠনিক একক হিসেবে রাষ্ট্র, আদালত, সংসদ, এবং রাজনৈতিক দলের হয়ে সরকার পরিচালনায় নিয়োজিত এজেন্টরা পুরোদস্তুর বহুজাতিক কোম্পানির পোষা প্রাণীতে রূপান্তরিত হয়েছে।
পুঁজিবাদের ধারাবাহিক আবর্তনে এর জন্ম ও বিকাশ নিশ্চিত হচ্ছে সর্বত্র। মুনাফানির্ভর বহুজাতিক অর্থনীতির মেরুদণ্ড হিসেবে সমাজে সক্রিয় নিজেকে সক্রিয় করেছে। মেরুদণ্ডখানা যদিও তাদের নিজস্ব নয়। অন্যকে ব্যবহারের ভিতর দিয়ে গঠিত এই মেরুদণ্ডই তাদের দেহকে খাড়া রাখছে। বহুজাতিক কাজেই এমন এক উৎপাদনশীল সত্তা, যার সঙ্গে দাসপ্রথা, কৃষিজমি নির্ভর জমিদার ও রায়ত অথবা উপনিবেশের ভিতর দিয়ে আসা পণ্য উৎপাদন পদ্ধতির পার্থক্য রয়েছে। বহুজাতিক শাসিত ন্যাক্রোপলিটিক্স দৃশ্যত অত্যাচারী নয়;— অত্যাচার পয়দা করার পন্থায় তার কৌশল বর্তমান মানব-সমাজে অভিনব ও যুগান্তকারী।
বহুজাতিকের ছত্রছায়ায় বিকশিত কারখানা মানে হচ্ছে অনেক লোকের কর্মসংস্থান। কারখানা মানে অর্থনীতির চাকা। পণ্য সেখানে উৎপাদিত হচ্ছে। বাজারে বিবপণন করা হচ্ছে, এবং একইসঙ্গে বাইরের দেশগুলোয় বাজার বাড়ানোর লক্ষ্যে রপ্তানিও করা হয়। অবিরত নতুন ও সময়-উপযোগী পণ্যের প্রবাহ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বহুজাতিকের ভূমিকা সমাজে যুগান্তকারী। মানব-সমাজে করে খাওয়ার সক্রিয়তা মিল-কারখানা ছাড়া টিকিয়ে রাখা কিছুতেই সম্ভব নয়। এখানে মালিক থেকে আরম্ভ করে শ্রমিক সকলেই উৎপাদনশীল ও কর্মঠ। ফিটনেস ছাড়া ময়দানে অস্তিত্ব রক্ষা সহজ নয়। জমি থেকে শুরু করে পণ্য উৎপাদনের সবটাই যে-কারণে নিখাদ লাভক্ষতির হিসাবে বাঁধা থাকে। সুতরাং বহুজাতিক একাধারে পুঁজিচক্রের প্রবৃদ্ধি ও অর্থনীতির নিয়ামক, অন্যদিকে পণ্য উৎপাদন ও মুনাফার ক্ষেত্রে তার নৈতিক অবস্থান সমাজকে বিচিত্র পরস্পরবিরোধী অবস্থানে সংঘাতমুখর রাখে। ন্যাক্রোপলিটিক্স মূলত এসব ঘটনার ফলাফল।
কারখানা যখন বড়ো হতে থাকে, বড়ো হতে-হতে বহুজাতিকে মোড় নিতে থাকে, তখন সেখানে যারা কর্তৃত্ব করছেন, তাদের হাতে সামগ্রিকভাবে পণ্যের মালিকানা ও বিপণন কুক্ষিগত হয়। তারা ঝুঁকি নিচ্ছে, ঝুঁকি থেকে মুনাফা বের করে আনছে, এবং এভাবে এমন একটি বাজার গড়ে তুলছে, যেখানে সামর্থ্য অনুযায়ী সকলেই ক্রেতা ও বিক্রেতা। যারপরনাই বহুজাতিকের সঙ্গে খোদ রাষ্ট্র, আইনি সংগঠন, মিলিটারি, রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠী থেকে অরম্ভ করে ক্ষমতাচক্রের যাবতীয় অংশীদারগণ আপসরফায় বাধ্য থাকেন।
জনস্বার্থ এভাবে রূপ নিয়েছ কর্পোরেট ইন্টারেস্ট বা বহুজাতিক স্বার্থে। আচিল এমবেম্বে বলেছিলেন,—আধুনিক রাষ্ট্র কেবল জীবনের রক্ষাকর্তা নয়, বরং সে নির্ধারণ করে কে বাঁচবে আর কে মরবে। শুভব্রত ববি ব্যানার্জি এখন একে বহুজাতিক পরিসরে টেনে নিচ্ছেন। তিনি দেখাচ্ছেন,—বহুজাতিক স্বার্থ রক্ষায় কীভাবে মধ্যপ্রাচ্যের তেলের খনিগুলোয় নিজের কর্তৃৃত্ব কায়েমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছক সাজায়। আরো দেখাচ্ছেন,— ফিলিস্তিনিদেরকে নিজভূমি থেকে উচ্ছেদ কিংবা আমাদের এখানে সংখ্যালঘু ও পাহাড়ি জনগোষ্ঠীকে ভূমিহীন করার নেপথ্যে বহুজাতিক মুনাফার হিসাব-নিকাশ কী ভূমিকা নিভাচ্ছে এখনো। কল্যাণমূলক ও ভর্তুকি নির্ভর শিক্ষা বা চিকিৎসা ব্যবস্থার সমান্তরালে অ-সরকারি ও ব্যয়বহুল শিক্ষা এবং চিকিৎসাব্যবস্থা কেন বিশ্ব জুড়ে গড়ে তোলা হয়েছে? জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে যেয়ে বহুজাতিক স্বার্থের ছক শুভব্রত গবেষণায় তুলে এনেছেন। কর্পোরেট মুনাফার হিসাব তাতে পুরোমাত্রায় সক্রিয় থাকছে।
শুভব্রত যে-কারণে বহুজাতিক ঈশ্বরকে একমাত্র জীবিতসত্তা ও বাকিদেরকে মৃত বা জম্বি ভাবছেন। সেইসঙ্গে পুঁজিবাদের এই নববিকৃতিকে তিনি ন্যাক্রোক্যাপিটালিজম নামে কয়েনাইজ করলেন তাঁর রচনায়। একুশ শতকের প্রথম দশকে শেষ প্রান্তে অভিসন্দর্ভটি প্রকাশ করলেন এই বঙ্গসন্তান। অভিসন্দর্ভের সংক্ষিপ্ত মুখবন্ধে তিনি লিখেছেন :
অভিসন্দর্ভে আমি ন্যাক্রোক্যাপিটালিজমকে একটি ধারণা হিসেবে তুলে ধরেছি। আমাদের সময়ে প্রতিষ্ঠানগুলোর সঞ্চয়বিন্যাসকে এখানে সংজ্ঞায়িত করেছি; এবং দেখানোর চেষ্টা করেছি,— এটি কীভাবে মরণ পয়দা করার ক্ষমতায় জীবনকে দখল ও বশীভূত করায় নিয়োজিত। ক্ষমতার প্রাতিষ্ঠানিক, বস্তুগত ও আলোচনামূলক বিভিন্ন রূপগুলো রাজনৈতিক অর্থনীতিতে কীভাবে কাজ করে ও তার মধ্য দিয়ে সহিংসতা ও দখল ঘটে থাকে, সেটি আমি যাচাই করেছি।
সাংগঠনিক সঞ্চয়বিন্যাসের কতিপয় স্বরূপ তুলে ধরেছি, যাদের সঙ্গে দখল ও মৃত্যু জড়িত, সুতরাং এগুলোকে ন্যাক্রোক্যাপিটালিজমের অনুশীলন হিসাবে বর্ণনা করা যেতে পারে। যেমন, উন্নয়নশীল দেশগুলোয় সম্পদ রূপে গণ্য উৎসগুলোর প্রভাব ও যুদ্ধ, এবং সামরিক বাহিনীর অ-সরকারীকরণ। কীভাবে এসব প্রতিরোধ করা যেতে পারে তার কতিপয় দিক নিয়েও ভেবেছি, যা ভবিষ্যতের গবেষণায় কাজে লাগবে।
শুভব্রতকে কাজেই ন্যাক্রোক্যাপিটালিজম সংক্রান্ত তাত্ত্বিক প্রস্তবনার অগ্রদূত বলা যেতে পারে। তাঁর রচনাটি পাঠ করলে বেশ বোঝা যায়, ভারোফাকিস ও জিজেকের মতো তিনিও পুঁজিবাদের মধ্যে উৎপাদনশীল থাকার সম্ভাবনা দেখছেন না। এখন তাকে টিকে থাকতে হলে নতুন কোনো ব্যবস্থায় মোড় নিতে হবে, অথবা মৃত্যুকে পুঁজি করে টিকে থাকতে হবে। তাঁর মতে, উৎপাদনের মাধ্যমে নয় বরং ধ্বংস করার মাধ্যমে তাকে টিকে থাকতে হবে। টিকে থাকার কৌশলটি কি অদ্য দেখছি না আমরা?
জীবন নয় বরং মৃত্যুই এখন সম্পদ ও পুঁজিবিন্যাসে নতুনত্ব এনে দিচ্ছে। যুদ্ধ, প্রকৃতির বিনষ্টি ও মানবসৃষ্ট বিপর্যয়, রাজনৈতিক ও জাতিগত সংঘাত, গৃহযুদ্ধ ইত্যাদির অবিরত উৎপাদন ছাড়া পুঁজিবাদের পক্ষে আচিল এমবেম্বে বর্ণিত জীবিত ও মৃত বা জম্বি অধ্যুষিত বিভাজনকে টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। তাঁকে তাই বলতে হচ্ছে : Contemporary forms of capitalism increasingly organize the subjugation of life to death for accumulation. (Banerjee, 2008)
ওপরে উদ্ধৃত বাক্যটির মর্মার্থ সরল। আধুনিক পুঁজিবাদ এমনভাবে গঠিত, জীবনের ওপর মৃত্যুকে চাপিয়ে দিয়ে সে লাভ তুলে আনতে চায়। দশকের-পর-দশক ধরে এই-যে এতোসব যুদ্ধবিগ্রহ বিশ্ব দেখেছে, যার সিংহভাগ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো পরাশক্তির মদদ ও ইন্ধনে সৃষ্ট, এর নেপথ্য কারণ শুভব্রতের বাক্যে ধরা পড়েছে। কথা একটাই সেখানে,—মুনাফাচক্রে যে-জীবন নিজের ভূমিকা নেভাতে পারবে না, তাকে ছেটে ফেলো।
আচিল এমবেম্বের ন্যাক্রোপলিটিক্সের বয়ানে মিশেল ফুকোর বায়োপাওয়ারের (biopower) প্রভাব সুস্পষ্ট। যৌনতা, শৃঙ্খলা ও শাস্তির ইতিহাস লিখতে বসে ফুকো শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। বায়োপাওয়ারকে ব্যবহার করে সৃষ্ট বায়োপলিটিক্সকে (Biopolitics) এখন জৈবক্ষমতা বা জৈবরাজনীতি বলা কতখানি যুক্তিসংগত হবে, এই ব্যাপারে আমি সন্দিহান। ফুকো যা বোঝাতে চেয়েছেন, সেটি বোধকরি জৈবক্ষমতা দিয়ে বোঝানো কঠিন। দেহ ও জনসংখ্যার ওপর দখল কায়েমে প্রতিষ্ঠান, নজরদারি ও একে স্বাভাবিক অভ্যাসে পরিণত করা বায়োপাওয়ার ছাড়া সম্ভব হতো না বলে মত দিয়েছেন ফুকো। মধ্যযুগে রাজতন্ত্র ও গির্জাতন্ত্রে সক্রিয়ারা ছিলেন সে-ক্ষমতার ধারক-বাহক।
কারা বেঁচে থাকবে, কারা গ্যালিলিওর মতো জীবন্মৃত হয়ে বাঁচবে অথবা ব্রুনো কিংবা মনসুর হাল্লাজের মতো বেঘোরে জান খোয়াবে, কাদের আচরণকে নৈতিক ধরা হবে, আর কারা হবে শেকসপিয়রের নাটকে উচ্চকিত ডাইনি, প্লেগ অথবা ইনকুইজিশনের বলি,—তার সবটাই ধরায় ঈশ্বরের ছায়া বলে সম্মানিত রাজা ও তাঁর সঙ্গে একীভূত গির্জাপ্রধানরা মিলে ঠিক করতেন। ঈশ্বরকে হটিয়ে ছায়াঈশ্বরের এই কর্তৃৃত্ব পুনরায় অভিনীত হতে দেখছি আমরা। ভারোফাকিস ও জিজেক প্রযুক্তি-সামন্তবাদকে সেই ছায়াঈশ্বর হিসেবে দেখছেন। এমবেম্বে দেখছেন রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক ক্ষমতার বিন্যাসের মধ্যে, আর শুভব্রত একে সরাসরি দেখছেন বহুজাতিকশাসিত মধুচক্রে বিরাজিত ভ্রমরদের মাঝে।
আচিল এমবেম্বে তাঁর বইয়ে বলেছিলেন : To kill or to let live: that is the logic of sovereignty. (Mbembe, 2003)। অর্থাৎ, সার্বভৌম যুক্তির অর্থ হলো মেরে ফেলবে নাকি বাঁচিয়ে রাখবে,—সেটি ঠিক করা। শুভব্রত সেখানে বলছেন : Capitalism thrives not despite but because of war, dispossession, and death. (Banerjee, 2008)। কথাটির আক্ষরিক অনুবাদে আমি যাচ্ছি না। মোদ্দা কথায় শুভব্রত বলতে চাইছেন,—যুদ্ধ, উচ্ছেদ ও মৃত্যুর কারণে পুঁজিবাদ ধ্বংস হয় না, বরং তারাই তাকে ফুলেফেঁপে উঠতে সাহায্য করে।
মানবসমাজ এখন একটি বাজারের অধীনে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, যেখানে মরণফাঁদ তৈরি করা সবচেয়ে লাভজনক বিনিয়োগ। এর পরিণাম বিয়ং-চুল হান তাঁর পর্যবেক্ষণে তুলে ধরেছেন, আর শুভব্রতরা একে সরাসরি ন্যাক্রোফেলিয়ায় আক্রান্ত ব্যাধি হিসেবে ব্যাখ্যা করছেন। যার ফিকশনাল বা কাল্পনিক স্বরূপ আমরা SCP Foundation নামে অনলাইনে সক্রিয়দের কাজে খানিকটা দেখতে পাচ্ছি এখন।
SCP Foundation হচ্ছে একটি কাল্পনিক বিশ্ব। বাস্তবে বিরাজিত উইকিলিক্সের কাল্পনিক সংস্করণ বলা যেতে পারে তাকে। জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জ ও তাঁর দলবল মিলে নরওয়েতে একখানা পাতালঘর তৈরি করেছিলেন। সেই পাতালঘরে তথ্য হ্যাক করার যন্ত্রপাতি বসিয়েছিলেন অ্যাসাঞ্জ। আর সেখানে বসেই সরকার, বহুজাতিক ও অংশীদারদের রসায়নে ঘটতে থাকা কুকীর্তির দলিল-দস্তাবেজ হ্যাক করতেন। গোয়েন্দা নজরদারি এড়াতে লেডি গাগার গানের সিডিকে যেমন ওইসব দলিল-দস্তাবেজ সিডিতে স্থানান্তর ও পরে সংবাদমাধ্যমে পাচার করতে তাঁরা ব্যবহার করেছিলেন। কৌশলটি অভিনব ছিল!
এসসিপি কাল্পনিক পন্থায় একই কাজে লিপ্ত। এটি একটি সাংকেতিক নাম, যার অধীনে রহস্যময়, ভয়াবহ, বা অসম্ভব সব কুকীর্তিকে নথিবদ্ধ করা হয়। ন্যাক্রোক্যাপিটালিজমকে তুলে ধরার ভাবনা থেকে কাল্পনিক মহাবিশ্বটি জন্ম নিয়েছিল। ইউটিউবে রিলিজ ভিডিওগুলোয় SCP-3914 বা এরকম সাংকেতিক শব্দ তারা ব্যবহার করে। এর মাধ্যমে এটি বোঝোনো হচ্ছে,—ন্যাক্রোক্যাপিটালিজম হলো ঐশ্বরিকসত্তা; যে কিনা মৃত্যুকে তার খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করছে। এই ঈশ্বর হলেন Keter-level entity, অর্থাৎ এমন এক জীবিত সত্তা যার মধ্যে মৃতদেহ ভক্ষণের বাসনা রয়েছে, এবং একে নিরোধ করা সম্ভব নয়।
আমাজনকে নিয়ে বিরচিত তাদের কাল্পনিক তথ্যচিত্রে যেমন দেখানো হচ্ছে, মৃত্যুর চাহিদা তৈরি হওয়ার পর আমাজন তাকে কীভাবে বিপণন করে। মানুষ আমাজনের মোড়কে বন্দি মরণপণ্য কিনছে সমানে। কেন আমাজন? এর উত্তর পেতে হলে বাস্তবের বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানটির দিকে একপলক তাকাতে হবে।
আমাজন একটি দানব আকৃতির পণ্য ডেলিভারি প্রতিষ্ঠান। বিশ্ব জুড়ে সক্রিয় তার পরিধি। কাজেই বিনিয়োগ ও মুনাফা দুটোই সেখানে অতিকায় বৃহৎ। তো এরকম একটি প্রতিষ্ঠানে এই-যে বিচিত্র সব চাহিদা মিটাতে টন-টন পণ্য মজুদ ও পরে যথাস্থানে ডেলিভারি দেওয়া হয়, সেখানে প্রতিষ্ঠানটিকে আগাগোড়া যন্ত্রের মতো নিখুঁত হতেই হচ্ছে। এছাড়া বাজারে টিকে থাকা তার পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং আমাজন যে-শ্রমশক্তিকে গুদামঘরে কাজ করার জন্য নিয়োগ দিয়ে থাকে, সেখানে তাদের কাজের পদ্ধতি ও সময় নিখুঁত করাটা তার কাছে জরুরি।
আমাজনের মতো প্রতিষ্ঠানে যারা শ্রম দিচ্ছে, লক্ষ করলে দেখা যাবে, টানা আট-দশ ঘণ্টা একছন্দে কাজ করে চলে। গার্ডিয়ান-এর এক প্রতিবেদন জানাচ্ছে,—আমাজনের গুদামঘরগুলোকে আধুনিক উপায়ে নির্মিত কয়েদখানা বলাটা সবচেয়ে যুক্তিসংগত। শ্রমিকরা সে-জেলখানায় টানা কাজ করে যায়। অন্যকিছু ভাবা ও গালগল্প দূরের বিষয়, অনেকসময় বাথরুমে যাওয়ার উপায় থাকে না। অনেকে সঙ্গে বোতল রাখেন এবং সেটিতে প্রস্রাব করেন। pee in bottles-এর বাধ্যবাধকতা এজন্য যে,—বাথরুমে গিয়ে প্রস্রাব করলে সময় ও কাজের ছন্দ বিঘ্নিত হতে পারে।
শক্ত নজরদারির মধ্যে যান্ত্রিক ছন্দে শ্রমিকরা কাজ করে ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা। এরকম শত-শত প্রতিষ্ঠান একই ছকে বিশ্ব জুড়ে কাজ আদায় করে নেয়। বাংলাদেশে গার্মেন্টস শ্রমিকরা সেলাই কাজ টানা চালিয়ে যেতে থাকেন, যেখানে বিরতি নির্ধারিত, এবং এর মাঝখানে অবসর অকল্পনীয়। এতে যা হয়, একজন শ্রমিকের নিজস্বতাকে এসব বহুজাতিক গিলে ফেলে।
It devours the dreams of the warehouse workers. It feeds on their expiration. (SCP-3914 archives)। কথাটির মানে দাঁড়াল,— আমাজন শুধু পণ্য ডেলিভারি করছে না, বরং একটি দানবীয় বহুজাতিক ঈশ্বরে নিজেকে পরিণত করেছে। এই ঈশ্বর চাহিদা তৈরি করে, তারপর সে-চাহিদা মিটানোর জন্য মানুষকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। শ্রমিকরা সেখানে Ucontainable Death Events-এর অংশ। গার্ডিয়ান-এর প্রতিবেদন তথ্য দিচ্ছে,—শ্রমিকর কখনো-কখনো অতিরিক্ত কাজের চাপে ভেঙে পড়ে। ছুটি কপালে জোটে না। মৃত্যুকে এখানে প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। কারণ মৃত্যু স্বয়ং পণ্যের অংশ হয়ে গেছে।
আমাজনের গুদামঘরে শ্রমদানের পদ্ধতি কাজকে নিখুঁত ও সময়ানুগ করার কাঠামোগত ফলাফল। মানবদেহ এভাবে পৃথিবী জুড়ে ব্যবহৃত, শোষিত ও পচে যাচ্ছে। পোশাক কারখানায় শত-শত দেহ পচে যাচ্ছে প্রতিদিন। পচে যাওয়া ও মরণ এখানে ব্যক্তির একলার নয়। শুভব্রত একে সামাজিক মৃত্যু হিসেবে দেখছেন। সংগতকারণে নিদান হেঁকেছেন : Necrocapitalism is not about killing per se, but letting die—of exhaustion, of invisibility, of uselessness. ব্যাংক, হাসপাতাল, কারখানা থেকে আরম্ভ করে হেন প্রতিষ্ঠান নেই যেখানে এই গণমৃত্যুর মিছিল চলছে না। সুতরাং বলা যেতেই পারে,—মানব প্রজাতির অতিকায় অংশটি ইতোমধ্যে মৃত ও জম্বি রূপে সর্বত্র খাটনি দিয়ে চলেছে, আর ক্ষুদ্র একটি অংশ দেহকে তরতাজা রাখতে বিচিত্র কসরতে ব্যস্ত। যার উপহাসমুখর বিবরণ সুইডিশ চলচ্চিত্রকার রুবেন অস্টলুন্ড তাঁর Triangle of Sadness-এ তুলে ধরেছিলেন।
জীবনকে মৃত্যুর অধীনস্থ করার ক্ষমতায় গরিয়ান বহুজাতিক হচ্ছে এখন ও আগামীদিনের অলিগার্কি;—যাদের হাতে ধরার ভূতভবিষ্যৎ আমরা জিম্মা করে বসে আছি। কে বাঁচবে আর কে মরবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা হারানোর ইতিহাস আজো না বদলানোর কারণে, বিয়ং-চুল হান ওই-যে মৃত্যুকে অনুভব করার মতো আধ্যাত্মিক পরিসর চাইছেন,—মানুষের পক্ষে সেটি অর্জন করা সম্ভব নয়।
. . .
. . .






One comment on “ন্যাক্রোপলিটিক্স ও মানবজাতির মরণবিকার”