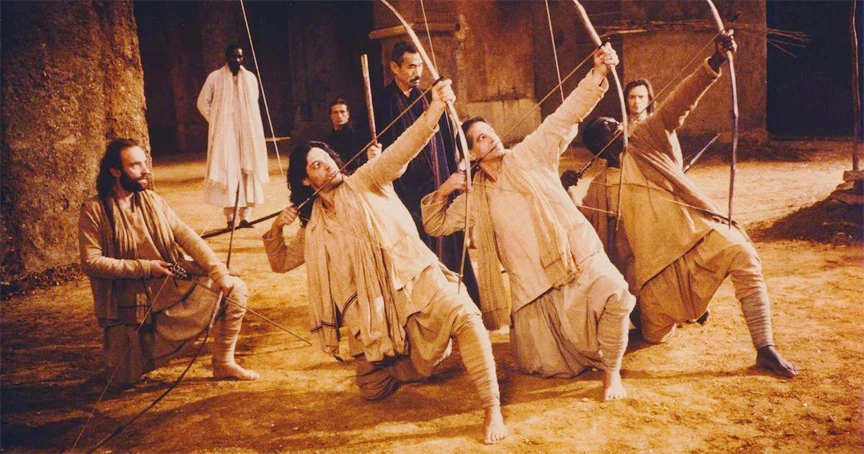কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস সংকলিত মহাভারতকে রবি ঠাকুর ভারতবর্ষের ইতিহাস তালাশের চাবি বইলা বুঝতেন। এখন মহাভারতের সময়কাল কিন্তু ইউনিক। এমন এক কালপর্বে মহাগ্রন্থটি রচিত হইতেছে যখন কিনা কিতাব রচনা ও সংকলনে ব্যক্তিস্বত্বের বালাই ছিল না। ব্যাদবেসের নাম আমরা পাইতেছি কিন্তু উনার একলার পক্ষে এরকম একখান জাম্বুবান রচনার সংকলন কি আদৌ সম্ভব? বিশেষজ্ঞদের বৃহৎ অংশ সেই সম্ভাবনা মোটামুটি নাকচ করে দিতেছেন। ভারত রাজবংশের ইতিহাস নামে বিদিত মহাগ্রন্থ নির্দিষ্ট কারো পক্ষে রচনা ও সংকলনের কোনোটাই সম্ভব নয়;- এটা হইতেছে উনাদের মত।
মহাভারতের মতো কিতাব স্বত্ববন্দি ব্যক্তির পক্ষে রচনা সত্যি সম্ভব নয়। সামষ্টিক রচনাপদ্ধতি ছাড়া সম্ভব নয় বিধায় তার মালিকানা বা স্বত্বের দাবি অবান্তর। মহাভারত, রামায়ণ বা এরকম যত কিতাব বিশ্বে জীবিত… তার সবটাই অগত্যা কপিলেফট। স্বত্ব যদি কারো থাকে সেইটা হইতেছে ওই ভূঅঞ্চলে বিরাজিত জাতির। সামষ্টিক রচনা ও সংকলন প্রক্রিয়ায় গমনের মাধ্যমে উৎকৃষ্ট দুইখান আকরগ্রন্থ তারা আমাদেরকে উপহার দিয়া গেছেন। মহাভারত বিরচনের ইতিহাস নিয়া যদি চলচ্চিত্র হইত, আমরা হয়তো পরিষ্কার বুঝতে পারতাম কী কারণে রবি ঠাকুর এই গ্রন্থকে ভারতবর্ষের জনমানস বোঝার চাবি বইলা গণ্য করছিলেন।
মহাগ্রন্থটি ধ্রুপদি বিবেচিত হওয়ার বড়ো কারণ তার ব্যাপ্তি। এক্সটেন্ডেড বা সম্প্রসারিত হওয়ার অতুল ক্ষমতা মাথায় রাখতে হইতেছে। ফ্লেক্সিবিলিটি বা নমনীয়তাকে উপেক্ষার সুযোগ নাই। গ্রন্থটি এমন এক তরিকায় রচিত, যেখানে অবিরত ইনপুট দিতে সেকালে লোকজন কুণ্ঠা বোধ করে নাই। শত-শত বছর ধরে কাহিনির শাখা-প্রশাখা অবিরত তার দেহে বিস্তার লাভ করছে। কাহিনিগুলা পরস্পর সংযুক্ত এমন নয়, অন্যদিকে তাদেরকে পৃথক ভাবাও কঠিন। ছিমছাম সাড়ে আট হাজার পদ্যশ্লোকে ঠেসেঠুসে লক্ষাধিক, মতান্তরে দুই লক্ষাধিক শ্লোক সেখানে স্থান পাইছে। দানবীয় এই বিস্তার সত্ত্বেও পাঠক কিন্তু ভাবে না,- ইস আরো পরিপাটি হইলে দারুণ হইত! এত মেদ কেন যুক্ত সেখানে!
মহাভারতের সারানুবাদ রাজশেখর বসু করছিলেন। কবীন্দ্র পরমেশ্বর বিগত হওয়ার প্রায় তিনশো বছর পর কালীপ্রসন্ন সিংহকে মহাভারত ভাষান্তরের সুকঠিন যজ্ঞে নিবেদিত দেখতেছি। ততদিনে যদিও পদ্যানুবাদে গাঁথা কাশীরাম দাসের মহাভারত ঘরে-ঘরে ব্যাপক সমাদৃত। কাশীরামী মহাভারত মোটের ওপর পূর্ণাঙ্দিগ হলেও কবীন্দ্র পরমেশ্বর কৃত কাব্যানুবাদটি ছিল সংক্ষিপ্ত। সুলতান পরাগল খানের সভাকবি তত্ত্বালাপগুলা বাদ দিয়া তর্জমা করছিলেন। তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল মহাভারত জুড়ে ছড়ানো কাহিনি ও কুরু-পাণ্ডবে সংঘটিত কুরুক্ষেত্রের উপাদেয় বিবরণ সুলতান সমুখে পেশ করা। কালীপ্রসন্ন সিংহ এইবেলা মহাভারতকথা পদ্যের পরিবর্তে গদ্যে ভাষান্তর করলেন। সুনীল গাঙ্গুলীর সেই সময় উপন্যাসে যার বিবরণ আমরা পাইতেছি। ঊনবিংশ শতকের কলকাতা, যেখানে একদিকে কথ্যবুলির রসে চোবানো হুতোমপ্যাঁচার নকশায় কালীপ্রসন্ন সাংবাদিক কড়চা লিখতেছেন, অন্যদিকে তৎসমবহুল পুরাতনী বাংলায় মহাভারত নামাইতেছেন। বেঁচে ছিলেন সাকুল্যে বছর ত্রিশ। ভাবলে গায়ে কাঁটা দিয়া ওঠে। কী দম ছিল এসব লোকের। বাপরে!
সময়ের সঙ্গে মহাভারতের সংক্ষিপ্ত সব সংস্করণ আমরা পাইতেছি। এখন এসব সংস্করণে মহাভারতের স্বাদ পাই ঠিক আছে, কিন্ত তার বিস্তার ও বিচিত্র দিকে গমনের মাহাকাব্যিক দ্যোতনা কি পাই? অল রোড গো টু রোম বা মক্কার মতো কুরুক্ষেত্রে এসে বিচিত্র দিকে ছড়ানো কাহিনির শাখা-প্রশাখার একত্রে জড়ো হওয়ার নাটকীয়তা কি জীবিত পাই সেখানে? না, পাই না। আসলি পাঠ ছাড়া তার দেখা পাওয়া সম্ভবও না। রাজশেখর বসুর অতুলনীয় সারানুবাদ সহজ স্বচ্ছন্দ ও পরিপাটি, উপেন্দ্রকিশোরের হাতের ছোঁয়ায় তার সংক্ষিপ্ততম রূপ উপাদেয়, কিন্তু কালীপ্রসন্নের তৎসমবহুল গদ্যে সে এমন এক সামগ্রীতে মোড় নিতে থাকে যার ওজন বাটখারা দিয়া মাপবার নয়। সেখানে গমন করলে এই মহাগ্রন্থের প্রকৃত সমবায়ী রচনাপদ্ধতি আমরা টের পাইতে থাকব। স্বত্ববিহীন চরিত্র রূপে ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় এই গ্রন্থের প্রভাববিস্তারী আবেদনের মাহাত্ম্য তখন খানিক খোলাসা হয়। কালীপ্রসন্ন কাজেই অনন্য;- অনুপম ও তুলনারহিত!

এখন এই ঢাউস কিতাব সময় নিয়ে পাঠ বিরাট ঝক্কি। তার ওপর আছে অজস্র রেফারেন্স। রাজবংশের বর্ণনায় চলে যাইতেছে জেনোলজির গভীর তলদেশ। এক রাজার কাহিনি ফাঁদতে বসে তার চৌদ্দগুষ্টি নিয়া টান দিতেছে। সেখান থেকে আবার অলৌকিক অতিরঞ্জনের জগতে ধাইছে অবিরত। মহাভারত স্বয়ং যদি অতিকল্পনার সমষ্টি হয়, এখন সেখানে আবার দেবলোক, নরলোক হতে আরম্ভ করে সমুদয় একখান জগৎ বিরচনে তারে ব্যস্ত দেখে পাঠক। তার মধ্যে আবার ভারতবর্ষে বিরাজিত জনপদের আবছায়া চকিতে ঝিলিক দেয় সেখানে। বাস্তবে বিদ্যমান ভৌগলিক অঞ্চলেকে ধারণ করে সে। মহাভারতে যে-কারণে ভারতবর্ষে সক্রিয় জলবায়ু সুতীব্র। আপাত অবাস্তব কল্পলোক ওই জলবায়ুমাঝে সঞ্চরণশীল। এক কাহিনির লেজ ধরে পরবর্তী কাহিনি… এভাবে উদ্দেশ্যহীন যাইতেছে, কোথায় যাইতেছে, কোনখানে থামবে তার আন্দাজ পাওয়ার উপায় নাই, তথাপি বিজড়িত থাকতে কোনো অসুবিধা ঘটে না পাঠকের। এই ধরনের রচনাপদ্ধতি একালে সুকঠিন।
তলস্তয়ের ওয়ার এন্ড পিস পাঠের বড়ো অন্তরায় তার জেনোলজি। বিচিত্র সব চরিত্রের নামধাম ও সম্পর্কের প্যাঁচে পড়ি আমরা। মহাভারতে ধারাটি যথারীতি বহমান, কিন্তু আটকায় না বিশেষ। আলাদা করে প্রতিটা চরিত্রের ঠিকুজি ইচ্ছা করলে সেখান থেকে নিতে পারতেছি আমরা। নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী যেমন বের করে আনছেন। দিস্তা-দিস্তা বই লিখছেন এই পুরাণ বিশেষজ্ঞ। মহাভারত একাধারে আখ্যান ও মহাকাব্য উভয় স্রোত ধরে প্রবাহিত। প্রধান চরিত্ররা বিচিত্র কাহিনি পরম্পরায় সেখানে বিবর্ধিত হইতে থাকে। তাদের দেহ, মনমেজাজ ও ভিতরসত্তার টানাপোড়েনের সবটা ধৃত যেখানে। আধুনিক আখ্যানের সঙ্গে প্রভেদ বলতে চরিত্রগুলা নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করেও করতে পারে না। তারা কাহিনিপটে সাজানো গুঁটি। তাদের বিবিধ বৈশিষ্ট্য ও অনন্যতা উক্ত ছক মেনে পাঠকের কাছে অবিরত উন্মুক্ত হয়। কোনো চরিত্রের ব্যাপারে একপেশে রায় ঠোকার অবকাশ যে-কারণে অবান্তর। চরিত্ররা ভালো ও সমভাবে মন্দ। তারা দোষী ও সমভাবে নির্দোষ। প্রায় সকল চরিত্রের ক্ষেত্রে ছকটি সর্বজনীন। পাঠক এখন সেই ছকে বসে তাদেরকে অবলোকন করে। কর্মফলের গতি ও পরিণাম বুঝাইতে মহাভারতকার নির্দয়ভাবে এক-একটি চরিত্রকে যেখানে ব্যবহার করেন।
মোহ কি আর মোক্ষ কোনপথে এই নৈতিক মীমাংসায় পৌঁছাইতে মহাভারতের চরিত্ররা একে-একে কুরুক্ষেত্রে শহিদ হয়। শান্তিপর্বে ধু ধু শ্মশান। কেবল আহাজারি, রোনাজারি আর অনুতাপ! সেখান থেকে বাণপ্রস্থে গিয়া অবসান। এই হইতেছে জীবন। এই হইতেছে সংসার-মহারণ্যে জীবের গতি। মা ফলেষু কদাচন। তুমি যা করো তার ওপর তোমার হাত থাকতে পারে, কিন্তু করার পর যে-ফল পাইতে থাকবে, এখন সেই ফলটারে ফিরানো বা অন্যখাতে প্রবাহিত করার উপায় রুদ্ধ। মহাভারত যে-কারণে ট্রাজিক। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের ক্ষণে ভীম দুর্যোধনের উরুভগ্ন করার কসম কাটে। ভীমকে যেসব কাহিনির ভিতর দিয়া আমরা গমন করতে দেখি, সেখান থেকে তার দেহ-মনের গতিক বুঝতে গাড্ডায় পড়তে হয় না। স্বভাবচরিত্র পরিষ্কার ধরা যায়। সে কখন কী করতে পারে, তার শক্তি ও সীমাবদ্ধতা পাঠক আন্দাজ করতে পারেন বৈকি। তার মধ্যে সংগোপন কিছু বিষয় থাকে যার আভাস এইবেলা পাঠকমনে ভীমের প্রতি সকরুণ আবেগ জাগায়। দানব সমতুল শৌর্যের অধিকারী ভীম আদতে বালক;- এই অনুভব পাঠককে প্রতিপদে তাড়া করে ফেরে সেখানে। এমন এক চরিত্র যে কিনা দ্রৌপদীর প্রতি অন্ধ অনুরাগ প্রদর্শনের ভাষা আজো রপ্ত করতে পারল না! দ্রৌপদী সেটা টের পেয়েও তাকে অবহেলা করেন। বেশি হলে নিজ স্বার্থ হাসিলের মতলবে দানবের ইমোশনকে সময় বুঝে কাজে লাগান পাঞ্চালী। ভীম এখন চালাকিটা টের পেয়েও পায় না। বুঝেও উপেক্ষা করে এই তঞ্চকতা। দ্রৌপদীকে একলা পাইতে চাওয়ার বেদন কেবল তারে নীরবে দহে সেখানে।
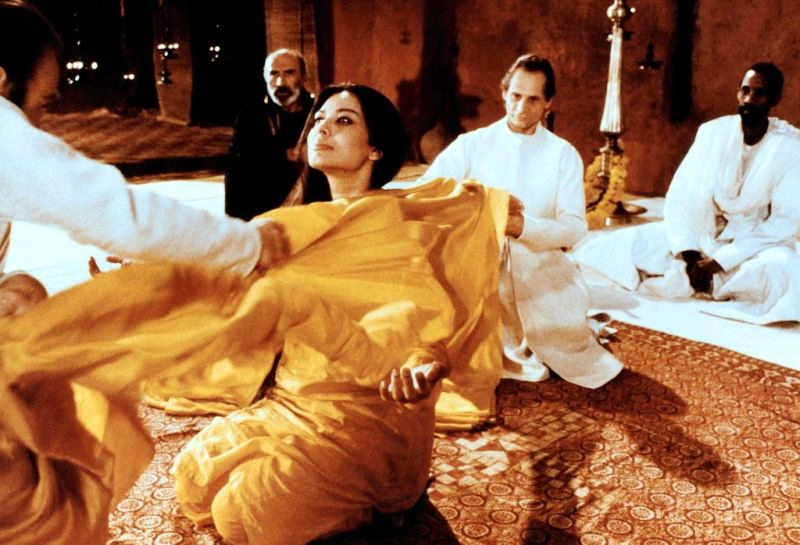
এত অজস্র চরিত্র! ছোটবড়ো পরিসরে তারা ব্যপ্ত! চরিত্রগুলো কিন্তু কোনোভাবে কোথাও হারায়া যায় না! ইনসিগনিফিকেন্ট ভাবার অবকাশ পাঠককে তারা দিতে নারাজ। সামষ্টিক রচনা হওয়া সত্ত্বেও ব্যালেন্সটা সেকালে কীভাবে সম্ভব করে তোলা হইছিল সেকথা ভাবলে অবাক যাইতে হয়! আদি মহাভারত তো মোটা দাগে সাড়ে আট হাজারের মতো কবিতাপঙক্তি বা শ্লোকের সমষ্টি। ব্যাদবেস শিষ্য বৈশম্পায়ন চব্বিশ হাজারে নিয়া গেলেন। গুপ্ত যুগে এসে মহাভারত সংকলিত হইতে থাকে। শ্লোকসংখ্যা ততদিনে লক্ষাধিকের ওপর ঠেকছিল। বোঝা যাইতেছে, রামায়ণ ও মহাভারতের মতো অতি প্রাচীন কিতাব নিছক রাজবংশ অথবা ভগবান-অবতারের কীর্তি বর্ণনায় সীমিত থাকেনি। প্রাচীন ভারতবর্ষের ভৌগলিক পরিসীমার অজস্র খুঁটিনাটি ধারণের অতুল সক্ষমতায় একলাই একশো হইতে তারা জন্ম নিয়েছিল।
আধুনিক যুগে ব্যক্তি বিরচিত রচনার মাহাত্ম্য বোঝাইতে আমরা ধ্রুপদি, মহাকাব্যিক ইত্যাদি ট্যাগ ব্যবহার করি ঠিক আছে, কিন্তু মহাভারতকে মাথায় নিলে বিশেষণগুলাকে অসার আর আলঙ্কারিক মনে হইতে থাকে। মহাভারতকে যেসব জায়গা হইতে আমরা ধ্রুপদি ও মহাকাব্যিক বইলা বুঝি তার মাহাত্ম্য সম্পূর্ণ আলাদা! আধুনিক কালসীমায় দেখা দেওয়া শ্রেষ্ঠ রচয়িতার পক্ষে এই পর্যায়ের কিছু জন্ম দেওয়া আকাশকুসুম কল্পনা। একলা ব্যক্তির পক্ষে এরকম বহুমাত্রিক উৎসকে একত্রে জড়ো করে কিছু রচনা নিতান্ত অবাস্তব। সম্ভব নয় একদম। সমষ্টি এবং স্বত্ববিহীন রচনাপ্রক্রিয়াই কেবল মহাভারতের মতো আকরগ্রন্থ প্রসবের শক্তি রাখে। আমরা যে-যুগ বাস করি সেখানে এটা কোনোভাবে সম্ভব নয়। এমনকি অনেকজন মিলেও যদি এরকম কিছু লিখতে নামেন, দশকের-পর-দশ ধরে লেখনক্রিয়া জারি থাকে, একটা প্রসঙ্গের লেজ ধরে শত প্রসঙ্গ যুক্তও হয়, তথাপি মহাভারত সম্ভব নয়। যে-কালপর্বকে ধারণ করতে এই মহাগ্রন্থ বিরচিত, এবং সেখানে যেসব উপাদান সক্রিয়, তার মধ্যে ছিল মহাকাব্যিক ধ্রুপদি বিস্তারের সূত্র। অদ্য এর কমতি পড়ায় ওয়ার এন্ড পিস পর্যায়ের কিছু সৃষ্টি হইতে পারে, রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়াড, ওডিসি অথবা আরব্য রজনীর মতো সাহিত্য নাহি সম্ভব।

নাজুক ও অবিরত পরিবর্তনশীল সময়স্রোতে এই মানের স্টোরিটেলিং কঠিন। আমরা যা পারি এবং পারতেছিও, সেটা হইতেছে,- এইসব ধ্রুপদি মহাকাব্যিক কিতাবে বিস্তারিত জীবনবেদের খণ্ডাংশ নিয়া বিচিত্র মাত্রায় নিজেকে আবিষ্কার করা। বোঝার চেষ্টা করা যে আমরা কোথায় আছি! জয়েস যেমন ইউলিসিস লিখছেন। এলিয়টরা গ্রিক ধ্রুপদি সাহিত্যের রেফ্রেন্স কাজে লাগাইছেন। আমাদের এখানে মধুসূদন, রবি ঠাকুর, বুদ্ধদেব বসুরা রামায়ণ ও মহাভারত থেকে নানা সূত্র আহরণ করে নতুন সাহিত্য রচনায় ওস্তাদি ফলাইতে চেষ্টায় ত্রুটি রাখেননি।
আমাদের সাধ্য এটুকু, কারণ ব্যাপকভাবে বিস্তারিত কর্মযজ্ঞ মুখরিত সময়ে বসবাসের কারণে আমাদের পক্ষে এর সবটা ধারণ করা সম্ভব নয়। আজকের পৃথিবী পৌরাণিক পৃথিবীকে ছাপিয়ে এতটাই অতিকায় আর জটিল, এখন তাকে একসুতোয় গেঁথে মহাকাব্যিক জীবনসংবেদে ভাষা দেওয়া সম্ভব নয়।
. . .
. . .