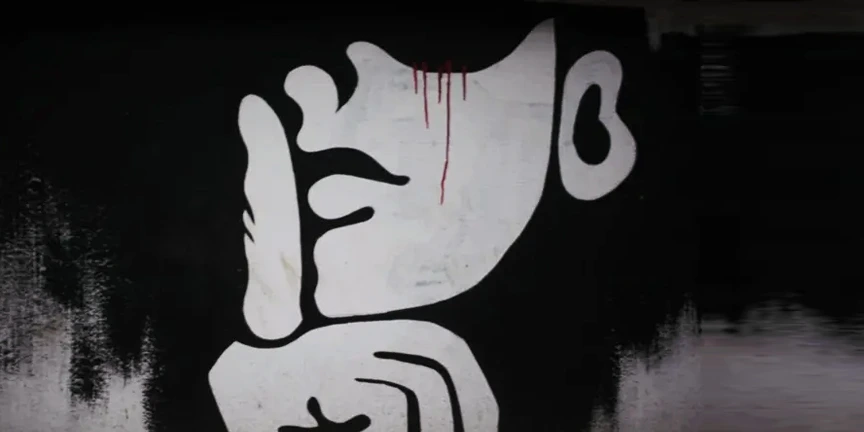. . .
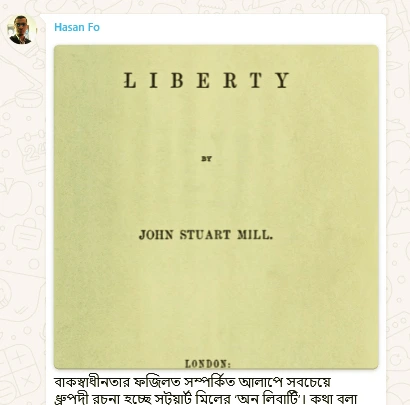
বাকস্বাধীনতার ফজিলত সম্পর্কিত আলাপে সবচেয়ে ধ্রুপদি রচনাটি হচ্ছে জন স্টুয়ার্ট মিলের অন লিবার্টি। কথা বলা বা মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিয়ে লিখিত এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৫৯ সালে।
. . .
বাকস্বাধীনতার ফজিলত ও বিপদ
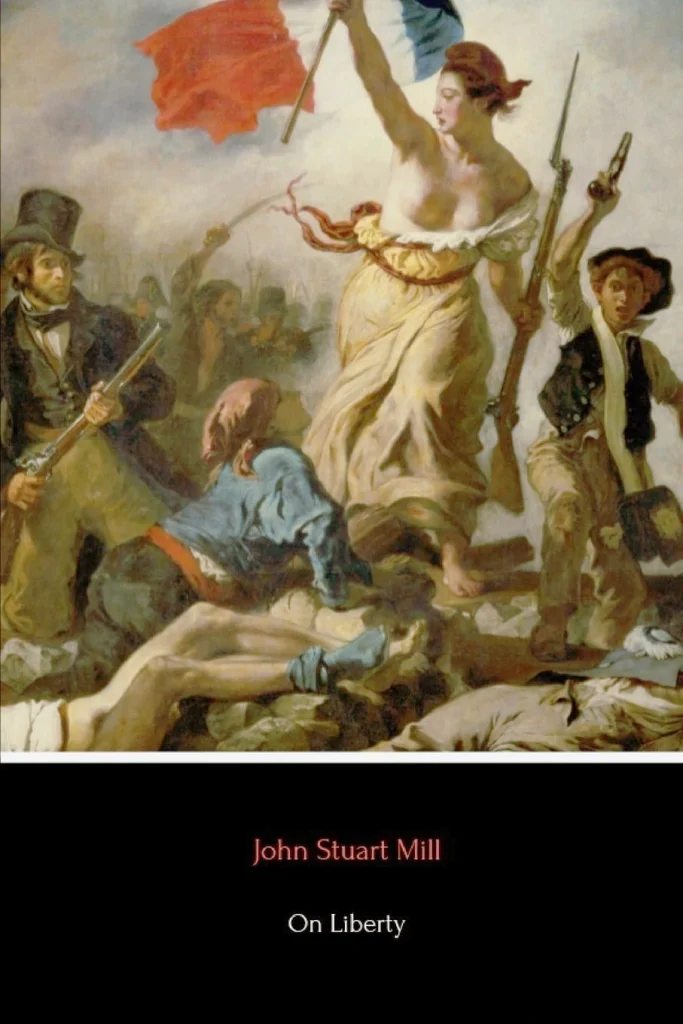
বাকস্বাধীনতার সপক্ষে জন স্টুয়ার্ট মিল যে-ওকালতি করে গেছেন, সেখানে এর দুটো দিক ছিল বলে জানি। প্রথমত, মন খুলে নিজের কথা বলতে পারাটা হচ্ছে মানুষের সহজাত অধিকার। পরিবার থেকে রাষ্ট্র সকলে তাকে সেটি দিতে বাধ্য। দ্বিতীয়ত, নিজের কথা নিংসংকোচে বলতে পারা ও মতাপ্রকাশের মূল উদ্দেশ্য হবে সত্য যেন অবরুদ্ধ না হয় তা নিশ্চিত করা। জন স্টুয়ার্ট মিলের মতে, কারো কণ্ঠ চেপে ধরার মানে হলো সত্যকে আমরা রুদ্ধ করতে চাইছি। এখন সত্য যদি আংশিক বা খণ্ডিতও হয়, তাতে অসুবিধে নেই। আংশিক সত্যকে তর্ক-বিতর্ক ও সংলাপের সাহায্যে পূর্ণতা দান সম্ভব। বাকস্বাধীনতার সুযোগ কাজে লাগিয়ে এমনকি ডাহা মিথ্যা কথা কেউ হয়তো বলবে;—নিজের অভিসন্ধি পূরণে মিথ্যার সপক্ষে বানোয়াট বয়ান সে হাজির করবে সেখানে। তার এই মিথ্যাকে কেউ-না-কেউ তখন প্রতিহত করার দায় বোধ করবে। যার ফলে মিথ্যা শেষ পর্যন্ত উন্মোচিত হতে থাকবে আর সত্যের দেবী প্রকাশিত হবেন স্বমিহমায়।
মিল এসব ভেবেটেবে ব্যক্তি-স্বাধীনতার সঙ্গে বাকস্বাধীনতাকে একীভূত করেছিলেন নিজের কিতাবে। রাষ্ট্র বা সমাজ প্রদত্ত অধিকার নয়, বরং ব্যক্তিকে জন্মসূত্রে প্রদানকৃত পাওনা হিসেবে একে গণ্য করা উচিত। অর্থাৎ মানবসন্তান যে-সমাজে জন্ম নিলো, সেখানে বাকস্বাধীনতার পরিসর আদায়ের জন্য আলাদা করে লড়াই করতে হবে না তাকে। সমাজ তার জন্য সেটি নিশ্চিত করতে বাধ্য, যেন কোনোপ্রকার ভয়ভীতি ও নিষেধাজ্ঞা ছাড়া সে এই স্বাধীনতা উপভোগ করতে পারে। বাস্তবে এরকম সমাজের অস্তিত্ব মানবগ্রহে কদাপি ছিল না।
যদি থাকত তাহলে সক্রেটিসকে হেমলক পানে জীবন দিতে হয় না। মনসুর হাল্লাজের শিরশ্ছেদের দাবি উঠত না নিশ্চয়। তর্কে পরাস্ত রাজপর্ষদ বরাহ স্বয়ং পুত্র মিহিরকে খনার জিহবা কর্তনের আদেশ জারি করতেন না। ব্রুনোকে আগুনে পুড়ে মরতে হতো না। গ্যালিলিওকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে অপদস্থ ও গৃহবন্দি করার সিদ্ধান্ত আদালত নিতেন না তখন। একালে পরিস্থিতি খুব-যে পালটেছে এমন নয়। তবে হ্যাঁ, বাকস্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের অধিকারকে রুদ্ধ করার পথগুলো অতীতের তুলনায় আরো সূক্ষ্ম ও পরিশীলিত করে তোলা হয়েছে। যেখানে পৃথিবীর উন্নত রাষ্ট্রগুলো একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে আপাতদৃষ্টে স্বাধীন পরিসর তৈরি করেছে, যদিও শতভাগ বাকস্বাধীনতা পৃথিবীর কোথাও নেই। মিল নিজেও যে-কারণে হার্ম প্রিন্সপলকে আমলে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। অর্থাৎ, আমার বলার স্বাধীনতা যখন অন্যের অনিষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়াবে, সেখানে এই স্বাধীনতায় সীমানা বা নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা বাধ্যতামূলক।
যেমন, পিনাকী বা ইলিয়াসের যা মন চায় বলার মানে এটি হতে পারে না,—সমাজে নজিরবিহীন নৈরাজ্য তারা পয়দা করতে থাকবে। রাশ টানতে হবে এখানে;—নতুবা সর্বনাশের কিছু বাকি থাকবে না। জন মিল্টনও যে-কারণে অ্যারিওপ্যাজিটিকায় প্রেস ফ্রিডমের সপেক্ষ সর্বোচ্চ ওকালতি করা সত্ত্বেও সীমারেখার প্রস্তাবনা দিতে বাধ্য হয়েছিলেন।
এসব কারণে মিলের বাকস্বাধীনতা নিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে সত্যকে উন্মোচিত রাখার প্রস্তাব আমার কাছে অনেকসময় ঝামেলার মনে হয়। সত্য নগ্ন ও খোলামেলা থাকুক,—এটি আমাদের চাওয়া। বাকস্বাধীনতার নাম করে যদি সত্যকে অহরহ মিথ্যা পয়দার কাজে ব্যবহার করা হয়, তাকে সবসময় প্রতিহত করা সম্ভব নাও হতে পারে। বাংলাদেশকে যার সেরা উদাহরণ গণ্য করা যেতে পারে। আমাদের সমাজ আগাগোড়া লাই ম্যাট্রিক্সের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। সত্যকে যেখানে অজস্র মিথ্যার সাহায্যে অবলীলায় বদলে ফেলা যায়, এবং মানুষ তা বিশ্বাস করে। এর পেছনে সক্রিয় রাজনীতিতে পরিবর্তন না এলে জন স্টুয়ার্ট মিলের অন লিবার্টি আমাদের জন্য খামোখা।
তাঁর থিয়োরি সেই সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য প্রযোজ্য, যেখানে সমাজবিকাশ পরিণত জায়গায় পৌঁছেছে। যেমন ইউরোপ বা আমেরিকার কথা আমরা হয়তো বলতে পারি। সেখানেও আবার সূক্ষ্মভাবে বিস্তর মিথ্যা হামেশা পয়দা করা হয়, এবং বাকস্বাধীনতার নামে সেগুলো সত্য বলে প্রতিষ্ঠাও পায় সমাজে। ভারতবর্ষের প্রণম্য ভাষাদার্শনিক ভর্তৃহরির লায়ার প্যারাডক্স মাঝেমধ্যে তাই নির্মম সত্য মনে হয়। ভাষার সীমাবদ্ধতা বোঝাতে ভর্তৃহরি ‘আমি মিথ্যা বলেছি’ এই বাক্যটি নিয়েছিলেন। বক্তা যেখানে নিজমুখে জানাচ্ছে,—সে মিথ্যা বলেছে। লোকটি এখানে এই সত্য স্বীকার করে নিচ্ছে,—সে মিথ্যা কথা বলেছে। সত্যটি স্বীকার করায় তাকে আর মিথ্যেবাদী ভাবা যাচ্ছে না। সুতরাং সকল অবস্থায় আমরা যা কহি তার সবটাই মিছেকথায় ভরা।
মিথ্যা বাক্য থেকে সত্যকে নিষ্কাশিত করা মানে এরকম বয়ান হাজির করা, যেটি মিথ্যাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে পারে। বাকস্বাধীনতাকে যারপরনাই আমার কাছে প্রহেলিকা মনে হয়। আমরা মন খুলে বলতে চাই ঠিক আছে, কিন্তু বলার মাত্রা কী হবে তা গুরুতর বিবেচনায় নিতে হয়। আবার এমনভাবে নেওয়া প্রয়োজন যেন সেন্সরশিপ চলে না আসে। আর এই বর্ডারলাইন নির্ধারণ জগতের সবচেয়ে দুরূহ কর্ম।
. . .
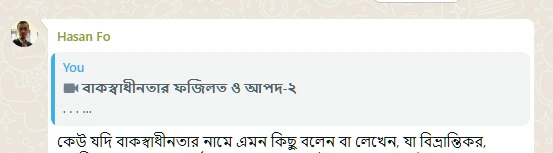
কেউ যদি বাকস্বাধীনতার নামে এমন কিছু বলেন বা লেখেন, যা বিভ্রান্তিকর, কুৎসিত, সত্য নয় বা অর্ধসত্য, এবং যে- কথার উদ্দেশ্য হচ্ছে কাউকে ব্যক্তিগত আক্রমণ হানা, সেটি নিশ্চয় বাকস্বাধীনতা নয়। বাকস্বাধীনতায় থাকতে হবে সত্য, সুন্দর ও সাবলীল মতপ্রকাশের অধিকার। সংবাদপত্র, সামাজিক মাধ্যম, রাজনৈতিক সমাবেশ, টকশো—সকল ধারায় এর সঠিক ব্যবহার বাঞ্ছনীয়। একবার যিনি বাকস্বাধীনতার জন্য আওয়াজ তুলবেন, পরক্ষণে তিনি যেন বাকস্বাধীনতা হরণের চেষ্টা না করেন। ইউনূস সাহেব যেমন এখন সেটি করছেন। আমাদের দেশের বাস্তবতায় বাকস্বাধীনতার বিপদ ভালোভাবে বিদ্যমান। মৌলবাদ বা পরাজিত শক্তি ফ্রিডম অব স্পিচের কথা বলে যে-প্রোপাগান্ডা, মিথ্যাচার ও ইতিহাস বিকৃতির মতো জঘন্য কাজগুলো করছে, সেটি বাকস্বাধীনতার নৈতিক অবস্থানকে প্রশ্নবিদ্ধ করে না?
. . .
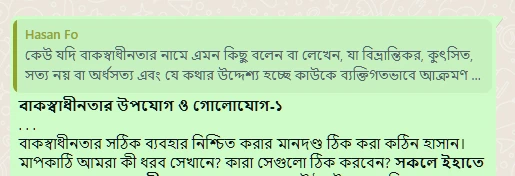
বাকস্বাধীনতার সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করার মানদণ্ড ঠিক করা কঠিন হাসান। মাপকাঠি আমরা কী ধরব সেখানে? কারা সেগুলো ঠিক করবেন? সকলে ইহাতে সম্মত;—আমরা তা কীভাবে বুঝব? প্রশ্নগুলো উঠবেই। তথাকথিত সভ্যজগতে বাকস্বাধীনতার মাত্রা ও পরিমাপ নিয়ে কাজেই ক্যাচালের শেষ নেই। দেশকাল ভেদে স্বরূপও বিচিত্র। ঝামেলা এড়াতে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বাকস্বাধীনতার সনদকে গোনায় ধরেন সকলে। কোনো জাতিরাষ্ট্রকে যদিও আজ পর্যন্ত সনদে লিপিবদ্ধ মাপকাঠির আক্ষরিক অনুসরণ করতে আমরা দেখিনি।
বাকস্বাধীনতার সঙ্গে উপযোগের সম্পর্কটি এখানে বেশ নিবিড়। জেরেমি বেন্থাম ও জন স্টুয়ার্ট মিলরা যেমন সেইসময় সুখের মধ্যে সামাজিক ন্যায্যতা দেখতে পাচ্ছিলেন। বেন্থাম বিশ্বাস করতেন, সমাজে সুখ-দুঃখের হিসাব নেওয়া সম্ভব। একটি সমাজে যেসব নিয়ম ও বিধি-বিধান চালু রয়েছে, এখন সেগুলোর কারণে মানুষের সুবিধা-অসুবিধার পরিসংখ্যান যদি নেওয়া যায়, তাহলে তার সুখদুখের মাত্রা আন্দাজ করা কঠিন কিছু নয়। মাত্রা আন্দাজ করতে পারলে উপযোগ সহজেই বের করা সম্ভব।
বেন্থাম এসব কারণে বাকস্বাধীনতাকে আবশ্যক বলে রায় দেননি। তাঁর মতে, বাকস্বাধীনতা নির্ভর করছে সমাজে এর প্রয়োগে মানুষ কতখানি সুখী বোধ করছে,—তার ওপর। যদি দেখা যায় এটি সংখ্যাগরিষ্ঠের অধিকার ও সুখ বৃদ্ধি করছে তাহলে ফাইন। এবং এটি তখন ওই সমাজের জন্য অপরিহার্য গণ্য করা উচিত। পক্ষান্তরে বাকস্বাধীনতা যদি সমাজকে অস্থির, অসুখী ও নাজুক করে তোলে,—বেন্থামের রাষ্ট্রদর্শন তাকে জায়গা দিতে রাজি নয়। মিল অবশ্য অতটা নিরস পন্থায় উপযোগ পরিমাপে গমন করেননি। ব্যক্তিস্বাধীনতার অন্যতম অনুষঙ্গ রূপে বাকস্বাধীনতাকে সকল অবস্থায় জরুরি গণ্য করেছেন তিনি। এবং সেখানে এর মাত্রা বলতে অন্যের অনিষ্ট যেন না ঘটায়, সেদিকটা বিবেচনায় রাখতে বলেছিলেন।
হেভিওয়েট দুই রাষ্ট্রচিন্তকের পরামর্শ মেনে আজকের দুনিয়ায় আমরা করে খাচ্ছি তা নয়। তবে হ্যাঁ, পৃথিবীর সকল জাতি-রাষ্ট্র-সমাজ সংখ্যাগরিষ্ঠের জন্য সর্বাধিক সুখ নিশ্চিত করাকে প্রগতি বলে ভাবে। বাস্তবে যদিও এই গ্রগতির হদিশ পেতে মাথার চুল ছিঁড়তে হয়। স্টিভেন পিঙ্কার অবশ্য তথ্য-প্রমাণ ও যুক্তিসহকারে দেখিয়েছেন,—প্রাচীন ও মধ্যযুগের তুলমায় বর্তমান পৃথিবী অনেকবেশি সুস্থির ও প্রাগ্রসর। এমনকি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধসহ শত-শত যুদ্ধ সত্ত্বেও সহিংসতার মাত্রা ক্রমশ নিম্নগামী হচ্ছে। এর পেছনে প্রবৃত্তির দিক দিয়ে অতি মাত্রায় পাশব মানব প্রজাতির মধ্যে যুক্তি-বুদ্ধির চর্চা, দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, প্রতিবাদ ও আন্দোলন ছাড়াও আইনের প্রয়োগ বড়ো ভূমিকা রেখেছে বলে পিঙ্কার জানাচ্ছেন। অর্থাৎ এসব উপযোগ সমাজে সহিংসতার মাত্রা ও প্রকৃতি কমিয়ে আনার ঘটনায় অবদান রাখছে বেশ।
বাকস্বাধীনতাও এরকম একটি উপযোগ। রাষ্ট্র ও সমাজের ব্যাপারে নিজ মতপ্রকাশের অধিকার সে দিচ্ছে। আধুনিক জীবন প্রণালিতে তার উপযোগ কাজেই স্বীকার করতে হবে। আর, অপব্যবহার সম্ভাবনা দুদিক থেকে ঘটার সম্ভাবনা রাখছে। যিনি এই উপযোগ ব্যবহার করছেন, সেখানে তার পক্ষে অপব্যবহার বিচিত্র নয়। অন্যদিকে রাষ্ট্র বা সরকারের মতো কাঠামো যারা অপারেট করে, তারা মওকা বুঝে একে দমিয়ে রাখতে চাইবে ও নিজ মতলব হাসিলে নকশা বানাবে,—সম্ভাবনাগুলো অতীতে ছিল, এখনো আছে, এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। কারণ এখানে রাজনীতি গভীরভাবে ক্রিয়াশীল।
এখন টিভির সাংবাদিক বর্ণাকে চটচজলদি উদাহরণ হিসেবে আমরা নিতে পারি এখানে। শুয়োর গালিটি হজম করে হাসনাত তাকে চাকরিতে বহাল রাখতে টিভি চ্যানেলকে বলেছে। সেলিম রেজা নিউটনের মতো হাজার-হাজার লোকজন অনলাইন দাপিয়ে বেড়ায়, তারা কিন্তু এটিকে হাসনাতের মহানুভব ও গণতান্ত্রিক আচরণের পরাকাষ্ঠা গণ্য করে তৃপ্তির ঢেকুর তুলবেন। এরা এমন এক বয়ানে নিজেকে জিম্মি করেছেন, যেখানে সত্য ও নৈতিকতা থেকে আরম্ভ করে কাণ্ডজ্ঞানের কিছু কাজ করে না। সত্য ও নৈতিকতার মামলায় কাজেই তারা অন্ধ ও একরৈখিক। গতকাল এক ডিডিওতে দেখলাম, ইনকিলাব মঞ্চের ব্যানারে সৃষ্ট মবদের একজন প্রকাশ্যে মঞ্চে দাঁড়িয়ে বলছে,—মব হিসেবে তারা গিভ অ্যান্ড টেক নীতিতে বিশ্বাস করে। মাল ফেলবেন, তারাও মিশন সাকসেস করবে। মিশন বুঝে টাকার অঙ্ক এদিক-সেদিক হবে, তবে দশ লাখের কম হলে তারা তাণ্ডবে নেই।
ভিডিওটি, কথার কথা, সেলিম রেজা নিউটনের মতো বিপ্লবঅন্ধরা দেখার পরেও শূন্য থেকে যুক্তি খাড়া করবেন। অনাচারকে জাস্টিফাই করতে পিছপা বোধ করবেন না। বাকিরা আবার ওই পথে যাবে না। তারা একে হাসনাতদের রাজনীতি হিসেবে ভেবে নেবে। হাসনাত প্রমাণ করতে চাইবে,—শেখ হাসিনার আমলে ঘটনাটি ঘটলে বর্ণাকে কেবল চাকরি নয়, আরো অনেক ঝুঁকি সইতে হতো। হাসনাতরা সেখানে তাদেরকে গালি দেওয়ার অধিকার এলাউ করছে। বাকস্বাধীনতা এভাবে সকল যুগে রাজনীতির মধ্যে আবর্তিত হয়েছে।
আমাদের কাছে পিনাকীর কাজকারবার দেশবিরোধী ষড়যন্ত্র ও সার্বভৌমত্ব বিপন্ন করে বদ মতলব হাসিলের উদাহরণ গণ্য হচ্ছে। পিনাকী কাজেই আমাদের কাছে অবৈধ ও অনৈতিক। কিন্তু তার ভক্ত ও অনুসারীদের কাছে এসব অনাচারের সবটাই বিপ্লবের অংশ, এবং সে-কারণে বৈধ ও নৈতিক। নৈতিকতার প্রশ্ন তোলে বাকস্বাধীনতার যেমন খুশি প্রয়োগের বিপদ যে-কারণে আটকানো যাবে না। তার সীমারখো কাজেই নৈতিকতা দিয়ে নয়, বরং রাজনৈতিক পন্থায় স্থির করতে হবে।
. . .