
শর্ট ইন্ট্রো : আফ্রিকা মহাদেশের বরেণ্য লেখক চিমামান্দা এনগোজি আদিচি আজ থেকে প্রায় এক দশক আগে টেড টক-এ হাজির হয়ে সিঙ্গেল স্টোরির বিপদ নিয়ে বক্তব্য রেখেছিলেন। চিমামান্দার বক্তব্যটি আলোচনার ঝড় তোলে তখন। আফ্রিকার গণ্ডি ছাপিয়ে তাঁর নাম বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর বলা কতঅগুলো যে এখনো সময়-প্রাসঙ্গিক তার প্রমাণ দিতেই যেন-বা মোস্তাফিজুর রহমান জাভেদ থার্ড লেন হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে তাঁকে নিয়ে আলাপের সূত্রপাত করেন। সদস্যদের মধ্যকার আলাপটি পরে একতরফা গল্পের বিপদ শিরোনামে নেটালাপ-এ গ্রন্থিত হয়। থার্ড লেন হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে তার সারসংক্ষেপসহ লিংক শেয়ার দিলে হাসান পুনরায় আলাপ জোড়েন;- বিশেষ করে কালোমানুষ ও আফ্রিকা সম্পর্কে নমস্য দার্শনিক ফ্রেডরিখ হেগেলের একতরফা গল্পের সীমাবদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন হাসান। এই সুবাদে গ্রুপে একতরফা গল্পের বিপদ প্রসঙ্গে দ্বিতীয় দফার আলাপ একতরফা গল্পের বিপদ-২ শিরোনামে নেটালাপ-এ আমরা গ্রন্থিত করছি। সবাইকে পাঠের আমন্ত্রণ থাকল।
. . .
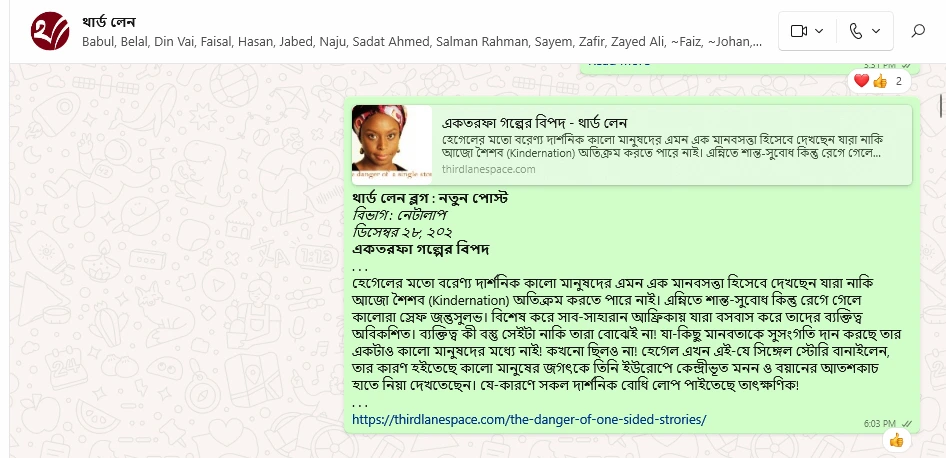
হেগেলের মতো বরেণ্য দার্শনিক কালো মানুষদের এমন এক মানবসত্তা হিসেবে দেখছেন যারা নাকি আজো শৈশব (Kindernation) অতিক্রম করতে পারে নাই। এম্নিতে শান্ত-সুবোধ কিন্তু রেগে গেলে কালোরা স্রেফ জন্তুসুলভ। বিশেষ করে সাব-সাহারান আফ্রিকায় যারা বসবাস করে তাদের ব্যক্তিত্ব অবিকশিত। ব্যক্তিত্ব কী বস্তু সেইটা নাকি তারা বোঝেই না! যা-কিছু মানবতাকে সুসংগতি দান করছে তার একটাও কালো মানুষদের মধ্যে নাই! কখনো ছিলও না! হেগেল এখন এই-যে সিঙ্গেল স্টোরি বানাইলেন, তার কারণ হইতেছে কালো মানুষের জগৎকে তিনি ইউরোপে কেন্দ্রীভূত মনন ও বয়ানের আতশকাচ হাতে নিয়া দেখতেছেন। যে-কারণে সকল দার্শনিক বোধি লোপ পাইতেছে তাৎক্ষণিক!
. . .
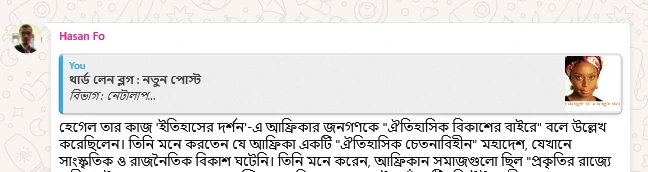
হেগেল তাঁর কাজ ইতিহাসের দর্শন-এ আফ্রিকার জনগণকে ঐতিহাসিক বিকাশের বাইরে’ বলে উল্লেখ করেছিলেন। তিনি মনে করতেন যে আফ্রিকা একটি ঐতিহাসিক চেতনাবিহীন’ মহাদেশ, যেখানে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বিকাশ ঘটেনি। আফ্রিকান সমাজ তাঁর মতে প্রকৃতির রাজ্যে বন্দি ছিল, তাই সেখান থেকে আত্মার মুক্তি ও প্রগতির সম্ভাবনা নেই। হেগেলের দৃষ্টিভঙ্গি ইউরোপীয় সভ্যতাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। ঐতিহাসিক বিকাশের কেন্দ্রে ইউরোপকে রেখে আফ্রিকা ও এশিয়া মহাদেশকে প্রান্তিক বিবেচনা করেছেন এই দার্শনিক। আধুনিক দর্শন-চিন্তক ও সমালোচকরা হেগেলের দৃষ্টিভঙ্গিকে ইউরোসেন্ট্রিক ও বর্ণবাদ প্রসূত বলে মত দিয়ে থাকেন। বড়ো মাপের চিন্তক হলেও আফ্রিকার ইতিহাস ও সংস্কৃতির গুরুত্বকে তিনি খাটো করে দেখেছেনG
আফ্রিকার ইতিহাস, সংস্কৃতি ও সামাজিক বাস্তবতা বৈচিত্র্যপূর্ণ, এবং একইসঙ্গে গভীর। আফ্রিকান জীবনধারা ও সভ্যতা মূলত তাদের সংগ্রামী ইতিহাস, প্রাকৃতিক পরিবেশ আর বৈচিত্র্যময় জাতিগোষ্ঠীর দ্বারা বিবর্তিত হয়েছে। আফ্রিকার শিল্পকর্ম (যেমন মুখোশ ও ভাস্কর্য) তাদের আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক বিশ্বাসের প্রতিফলন। চিনুয়া আচেবের মতো লেখকরা আফ্রিকার সংগ্রামী জীবনের প্রতিচ্ছবি বিশ্বের তুলে ধরেছেন। দীর্ঘদিন ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে থাকায় তাদের স্বাতন্ত্র্য ও সংস্কৃতির ওপর এর ক্ষতিকর প্রভাব গভীর হয়েছে। আফ্রিকা হচ্ছে সংগ্রাম ও সৃজনশীলতার সংমিশ্রণ। এই মহাদেশের জাতি ও জনগোষ্ঠীরা সংগ্রামী জীবনধারা থেকে উৎসারিত সংস্কৃতির অনন্যতা তোলে ধরে। হেগেল এর কোনোকিছুকে গুরুত্ব সহকারে ব্যাখ্যা করেননি।
. . .
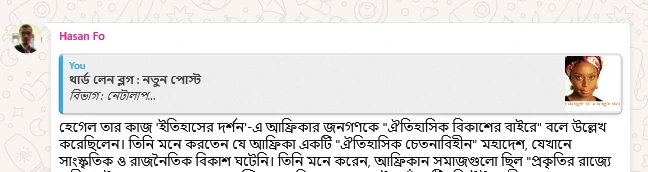
হেগেল অতিকায় মাপের দার্শনিক হইতে পারেন হাসান, কিন্তু কালো মানুষদের ব্যাপারে সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠতে তিনিও বিফল হইছেন। দার্শনিক ফ্রেমে মানব প্রজাতিকে বিবেচনা করছিলেন তখন। চিন্তা ও জ্ঞানকে প্রাগ্রসর রাখতে যারা ভূমিকা রাখছেন তাদের নিরিখে জাতি-গোষ্ঠী-সমাজকে বিবেচনা করছেন হেগেল। বিশ্ব জুড়ে ইউরোপীয় উপনিবেশের বিস্তার তখন ঘটতেছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞান-মননশীলতার পাশাপাশি মানবগ্রহের বিস্তীর্ণ অঞ্চল শ্বেতাঙ্গদের পদানত হয়। কালো মানুষদের গল্প তারা যেভাবে হাজির করছে, হেগেল এখানে বিনাবাক্যে সেগুলা বিশ্বাস যাইতেছেন! সিঙ্গেল স্টোরি বা একতরফা গল্পের সমস্যা থেকে নিজেকে মুক্ত করার দায় জার্মান ভাবুকে পরিলক্ষিত হইতে আমরা দেখি না।
আফ্রিকার কালো মানুষদের অরণ্য ও গোত্রকেন্দ্রিক সংস্কৃতি যে-বয়ান দাঁড় করায়, যেইটা আমরা অনেক পরে চিনুয়া আচেবে, এম এ সেজেয়ার, লিওপোল্ড সেঙ্ঘর, আমোস টুটুওলা বা ওলে সোয়েঙ্কাদের বরাতে পাইতেছি, হেগেলের সময় এরকম কালো মানুষরা ছিলেন না যাঁরা কিনা বয়ানটা তাঁর চোখের সামনে তুলে ধরতে পারবেন। কালো মানুষের জীবনাচার ও মূল্যবোধের জগৎকে ভিন্নদৃষ্টিতে নজর করার মতো পর্যাপ্ত বয়ান তাঁর হাতের নাগালে কখনো আসে নাই। আফ্রিকান সংস্কৃতি ও জীবনবোধের কিচ্ছু উনি জানত না। এই ব্যাপারে গভীর কোনো ধারণা তাঁর ছিল না। সিঙ্গেল স্টোরি যে-কারণে সবসময় বিপজ্জনক। চিমামান্দা তাঁর বয়ানে যা খুব ভালোভাবে ব্যাখ্যা করছিলেন।
হেগেলের কাছে কালো আদমি মানে হইতেছে বন্য-অসভ্য ক্রীতদাস। অ্যালেক্স হ্যালি তাঁর রুটস উপন্যাসে দাস চালানের ভিতর দিয়া আফ্রিকার কালো মানুষদের আমেরিকা যাত্রার যে-সত্য ও মর্মন্তুদ কাহিনি বর্ণনা করছিলেন, এখানে সাদা সায়েবদের অহং ভিতরে পুষে হেগেল সেই চোখ দিয়া কালো মানুষকে দেখতেছেন। একদিকে উনি কংক্রিট উনিভার্সিলিটির কথা বলতেছেন, যেখানে আবার কালোরা স্থান পাইতেছে না!
বড়ো চিন্তক সকল ব্যাপারে সংকীর্ণতা হইতে মুক্ত থাকতে পারেন না। হেগেলও পারেন নাই। জাক দেরিদা যেমন কোনো এক আলাপচারিতায় নারীদের এই বইলা আন্ডারমাইন করছিলেন,- নারীদের মধ্যে গভীর দার্শনিকতায় ঘাটতি আছে। সভ্যতার ইতিহাসে বড়ো মাপের নারীচিন্তক যে-কারণে আসে নাই। গার্গীর কথা বাদ দিতেছি। এই বিদূষী যাজ্ঞবল্ক্যর মতো পর্বতপ্রায় তার্কিককে যুক্তির খেলায় ওইসময় পরাস্ত করছিলেন। দেরিদা তাঁর নাম নাও শুনে থাকতে পারেন। মিশরে হাইপেশিয়ার কথা তো তাঁর অজানা ছিল না, তবু বলতেছেন। কারণ, হেগেলের কংক্রিট উইনিভার্সিলিটি তাঁকেও কবজায় রাখতেছে সেখানে।
সভ্যতায় আফ্রিকান তথা কালো মানুষদের অবদান বলে শেষ করার নয়। আজকের আমেরিকার দিকে যদি একবার তাকাই, আধুনিক সভ্যতার মক্কা আমেরিকান সংস্কৃতির ষোল আনার আটারো আনা আফ্রিকা হইতে আসা সংস্কৃতির প্রভাবে বর্ণাঢ্য। পোশাক, নাচাগানা, খেলাধুলা হইতে হেন উপাদান নাই যেখানে আফ্রিকা ছাপ রাখে নাই। বর্ণবাদী রাজনীতির কারণে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ক্ষমতাকেন্দ্রে কালোরা এখনো প্রবল হইতে পারেন নাই, কিন্তু লড়াই জারি আছে।
হেগেল যে-সময়ের মানুষ তখনো এই তথ্যটি বিজ্ঞান তাঁর হাতে তুলে দেয় নাই,- আজকের হোমো সেপিয়েন্স সেপিয়েন্সরা আফ্রিকা থেকে মাইগ্রেট করছিলেন আস্ট্রেলিয়ায়, এবং সেখান থেকে ভারতবর্ষ ও মধ্যপ্রাচ্যে তারা ছড়াইতে থাকেন। আমরা সবাই আফ্রিকার জলবায়ু ও প্রকৃতিকে রক্তে বহন করি। বড়ো কথা, মানুষকে আমরা এবং অপর-এ ভাগ করে দেখার খাসলত সকল অনাসৃষ্টির মূল কারণ। হেগেলের মতো উচ্চস্তরের ভাবুক এই সংক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পুরোপুরি ব্যর্থ হইছেন!
. . .
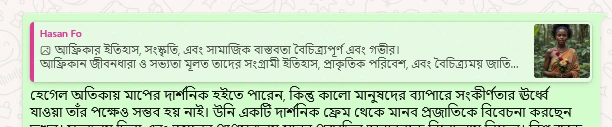
আফ্রিকায় ইউরোপীয় উপনিবেশবাদ গভীর ও দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব রেখেছে। সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতিতে যার ছাপ আজো দৃশ্যমান। উপনিবেশবাদ আফ্রিকার প্রাকৃতিক সম্পদ লুট, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও সামাজিক বিভাজনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ইউরোপীয় শক্তিগুলি আফ্রিকার প্রাকৃতিক সম্পদসহ খনিজ পদার্থ লুট করেছে। উপনিবেশ স্থাপনের প্রধান লক্ষ্যই ছিল আফ্রিকার অর্থনৈতিক সম্পদ দখলের মাধ্যমে ইউরোপকে শিল্পবিপ্লবের জ্বালানি সরবরাহ করা। দাসপ্রথার মাধ্যমে লক্ষ-লক্ষ আফ্রিকাবাসীকে ইউরোপ ও আমেরিকায় নিয়ে যাওয়া হয়। দাস চালানের নাম করে সস্তায় শ্রমশোষণ আফ্রিকার জনসংখ্যার উপর দীর্ঘমেয়াদে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। ঔপনিবেশিক দাসত্ব থেকে মুক্তিলাভ করলেও মহাদেশটি এখনো ইউরোপীয় শক্তি ও আন্তর্জাতিক সংস্থার ছলনার শিকার। ঋণের বোঝা, শর্তযুক্ত সাহায্য আর বাণিজ্য-কাঠামোয় একচেটে শোষণের কারণে আফ্রিকার সার্বভৌমত্বকে আজো ভঙ্গুর দেখায়।
. . .
কথা সত্য হাসান। আমরা যেমন এখনো পুরোপুরি ঔপনিবেশিক মনোজগৎ থেকে বাহির হইতে পারি নাই, আফ্রিকার ক্ষেত্রে এর প্রভাব আরো মর্মান্তিক। পুরো মহাদেশ আরণ্যিক সভ্যতায় ঘেরা ছিল। অসংখ্য গোত্র ও তাদের নিজস্ব বিধিনিয়মে মহিয়ান আফ্রিকাকে কাজেই সভ্যতার কেন্দ্রস্থলে পৃথক সভ্যতা রূপে আমরা বিবেচনা করতে বাধ্য। মিশর কিংবা ইথওপিয়া প্রাচীন সভ্যতাগর্বে গরবিনী হইতে পারে, কিন্তু আফ্রিকার অন্য অঞ্চলে তার প্রভাব গভীর হইতে পারে নাই। চিনুয়া আচেবে গোত্রশাসিত জীবনের যে-ছবি নিজ আখ্যানে তুলে ধরছিলেন, মহাদেশটি সেখানে পরিতৃপ্ত ও তরঙ্গিত থেকেছে সদা।
সাদা সায়েবদের বিশ্বজয়ী অভিযান প্রকৃত অর্থে ভাগ্য বদলানোর তাগিদ থেকে শুরু হয়। তারা যখন আফ্রিকার দুর্গম পরিসরে ঢোকে, তাদের চোখে সম্পদ দোহনের বাসনা ছাড়া দ্বিতীয় কিছু ছিল না। গোত্রকেন্দ্রিক প্রাকৃতিক জীবনধারাকে যে-কারণে তারা তছনছ করতে দুবার ভাবে নাই। সেইসঙ্গে আফ্রিকার জনগোষ্ঠীকে সভ্যতা বহির্গত জীব হিসেবেও তারা চিহ্নিত করে। ইউরোসেন্ট্রিক বয়ানের ভার আফ্রিকার ঘাড়ে চাপায় তারা। এখন এর প্রভাব এতটাই মারাত্মক,- সময়ের সঙ্গে আফ্রিকার কালো মানুষরা স্বয়ং এই বয়ানকে বিশ্বাস করার ফাঁদ হইতে এখনো মুক্ত নয়। যে-কারণে উপনিবেশের কবল থেকে বাহির হওয়ার পরে একটি দেশও নিজেকে শাসন করতে পারতেছে না।
চিনুয়া আচেবে যে-ধসের বিবরণ তাঁর আখ্যানে হাজির করছিলেন, এখন স্বাধীন নাইজেরিয়া বা অন্য দেশের পক্ষে ধস থেকে পুনরায় চিরাচরিত প্রাকৃতিক জীবনধারায় ফেরত যাওয়া অবস্তব কল্পনার শামিল। ধসটা এখানে মিসিং লিংক, চেষ্টা করলেও যারে ফেরত আনার উপায় নাই। আমাদের এখানকার মতো আফ্রিকা মহাদেশকেও সাদা সায়েবরা নেটিভ সায়েব আর বাদবাকিতে ভাগ করতে সফল ছিল। আফ্রিকায় যে-শাসনব্যবস্থা চালু আছে,- ঔপনিবেশিক আদলকে তা আজো জীবিত রাখতেছে। কেবল সাদা সায়েব নয়, সায়েবরা আফ্রিকায় গমনের আগে ইসলামের যে-সম্প্রসারণ সেখানে ঘটছিল, সেইটাও আখেরে আফ্রিকার মানুষদের স্বাতন্ত্র্য ও প্রাকৃতিক জীবনধারায় ক্ষতিকর প্রভাব রেখে গেছে।
ওসমান সেমবেন তাঁর ছবিতে এই ক্ষতটা তুলে ধরছিলেন। এখান থেকে যেমন লিওপোল্ড সেঙ্ঘরের মতো শিক্ষিতজনরা নেগ্রিচ্যুড (Négritude) মুভমেন্টের জন্ম দিতে বাধ্য হলেন। নিগ্রো তো আদতে গালি হিসেবে সায়েবরা ব্যবহার করত। এখন তাকে স্বকীয়তার ও আত্মপরিচয়ের ভাষ্য করলেন তাঁরা। এতকিছুর পরেও আফ্রিকা এখনো পশ্চিম হইতে প্রবাহিত ক্ষমতাছকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত।
নাইজেরিয়া তথা সমগ্র আফ্রিকায় পপগুরু হিসেবে স্বীকৃত আফ্রোবিটের জনক ফেলা কুটিকে আমরা একসময় পাশ্চাত্য উপনিবেশিকায়নকে সদম্ভে প্রত্যাখান করতে দেখছি। কেবল গানের মধ্যে নয়, ফেলা কুটি তাঁর প্রতিটা কথা ও আচরণে পরিষ্কার বুঝিয়ে দিতেন, একজন আফ্রিকান হিসেবে তিনি ইসলাম, খ্রিস্টান এবং সায়েব-গোলার্ধ হইতে আসা ইংরেজি ভাষাসহ গণতন্ত্র বা আরো যা-কিছু আছে, তার কোনোটাই ধারণ করতে বাধ্য না। Teacher, don’t teach me nonsense;- ফেলা কুটির এইটা ছিল মূল প্রতিপাদ্য। স্বচ্ছল পরিবারের সন্তান হিসেবে লন্ডনে ডাক্তারি পড়তে গিয়া মিউজিকে আবিষ্ট হন ফেলা, এবং তাঁর ভিত্রে আফ্রিকানসত্তার জাগরণ ঘটে। গানের ভাষা ও পরিবেশনায় এই রাজনীতি ফেলা কুটি করে গেছেন মারা যাওয়ার আগে অবধি। Democracy-কে আফ্রিকান ঢংয়ে বদলে নিছিলেন তিনি। Demo Crazy বা উনার ভাষায় Demonstration of craziness বইলা আঘাত হানতেন অহরহ। একাধিক রমণীসঙ্গীকে পরিষ্কার ভাষায় আফ্রিকান সেক্সিজম বইলা ঘোষণা দিতেও অকুতোভয় ছিলেন সদা। ভোটেও খাড়াইছিলেন, আফ্রিকার অনেকের কাছে নবি গণ্য পপসম্রাট।
ফেলা কুটির এহেন রাজনীতির মূলে ছিল আফ্রিকাকে তার আত্মপরিচয় ইয়াদ বিলানো, যেন নিজের স্বকীয়তা সে বুঝতে পারে, যেটি কিনা জাতিসত্তা গঠনের বনেদ বইলা তিনি গণ্য করছেন সবসময়। ফেলার এই পলিটিক্স হয়তো সময়ানুগ ছিল না, কিন্তু এর ভিতরে সেই বারুদ ছিল যা আফ্রিকার কোনো দেশ এখন আর ধারণ করে না। আফ্রিকানিটি প্রকৃতপক্ষে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ নয়, বরং এক মিসিং লিংকের তালাশ, যাকে ছাড়া আফ্রিকার জনগোষ্ঠীর পক্ষে নিজস্ব বনেদে দাঁড়ানো সম্ভব হইতেছে না।
. . .
. . .






2 Comments on “একতরফা গল্পের বিপদ-২”