তারাপদ রায়ের কবিতা আরো অনেকের মতো আমারও পড়তে বেশ লাগে। তাঁকে যখন পাঠ করি তখন তিনি প্রধান না গৌণ কবি ছিলেন, এসব ভ্যানতারায় যোগ দিতে মন চায় না। পড়তে ভালো লাগার অনুভূতি সব ছাপিয়ে যায়। কেন ভালো লাগে এই প্রশ্নের উত্তর কাজেই সঠিক বলতে পারব না। কবিতা অনেকরকম হয়, এটুকু কেবল জ্ঞাতব্য সেখানে। তারাপদের কবিতা উক্ত রকমফেরের অন্যতম বটে।
কবিতা অনেকভাবে লেখেন কবি। কেউ ঘোরপ্যাঁচ দিয়ে লেখেন। কেউ আবার সোজাসরল ঝেড়ে দেন। কারটা কখন ভালো লাগবে, পাঠকের পক্ষেও কিনারা করা কঠিন। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত অনেকের ভালো লাগে না। আমার তাঁকে পড়তে বেশ লাগে। তৎসমবহুল শব্দ ব্যবহারে ওস্তাদ ছিলেন। এজন্য কি ভালো লাগে? দার্শনিক বিভূতি সঞ্চার করতেন কবিতায়? এজন্য কি তাঁকে পাঠ করি এখনো? তাঁর কবিতায় যে-গভীর সাংগীতিক লয় তরঙ্গিত,—সেজন্য কি তিনি পড়তে ভালো? উত্তর দিতে পারব না ঠিকঠাক। পড়তে ভালো লাগে;—কেবল এটুকু বলতে পারি নিঃসঙ্কোচ। ওদিকে আবার জীবনানন্দ, বিনয়, শক্তির মতো কবিগণ রয়েছেন। সর্বজনীন পাঠক তাঁদের কবিতা পড়তে ভালোবাসেন। আমিও বাসি, কিন্তু কেন ভালোবাসি তার উত্তর কি জানি সঠিক? আপাতদৃষ্টে সহজ মনে হলেও যথেষ্ট জটিল ছাদে কবিতার জমিনে লাঙল ঠেলেছেন তাঁরা। পাঠের সময় তার কিছুই মাথায় থাকে না! পড়তে ভালো লাগছে;—এই অনুভূতি দামি হয়ে ওঠে।
রবি ঠাকুরের কথাই ধরা যাক। একসময় দিব্যি সহজ ঠেকত তাঁকে। এখন উলটো। সরলতায় ঠাসা দুর্বোধ্যতার প্রতিমা মনে হয়,—যখন ঠাকুরে রাখি চোখ। কাঁচা বয়সে সহজপাঠ্য রবি ঠাকুরের চেয়ে আজিকার দুর্বোধ্য রবি ঠাকুরকে কেন জানি পড়তে ভালো লাগে! বাংলাদেশের কবিতায় আল মাহমুদ সর্বজনীন পছন্দ। আমিও আছি সেই দলে। ভালো লাগে আল মাহমুদ। যেমন ভালো লাগে শহীদ কাদরী বা আবুল হাসানের মতো কবিজনকে। শামসুর রাহমানকে অনেকের ইদানীং পাত্তা দিতে মন ওঠে না। কবিকে পাঠ যাওয়ার আগ্রহে ভাটা নেমেছে। আমার কিন্তু মন্দ লাগে না রাহমান। ব্যক্তিসত্তার একলা যাপনের বিচ্ছিন্ন অনুষঙ্গ তাঁর কবিতায় অনুরণিত, এবং মনকে তা দখলে রাখে বেশ!
দেশ-বিদেশে ছড়ানো-ছিটানো অগণিত কবির নাম বোধহয় নেওয়া যাবে, যাঁদের কবিতা বিচিত্র কার্যকারণে পড়তে ভালো লাগে। ভালো লাগার মাত্রায় কমিবেশি থাকে অবশ্য। কোনো-কোনো কবির সঙ্গে অনেকদূর যেতে ইচ্ছে করে। কারো সঙ্গে কিছুদূর যাওয়ার পরে কাট্টি দিতে মন চায়। তা-বলে তাঁদের কাউকেই আগের মতো গৌণ ও গুরুত্বহীন ভাগাড়ে ছুঁড়ে ফেলতে মন সায় দেয় না। সুতরাং কার কবিতা কী কারণে ভালো লাগছে তার নিখাদ ব্যাখ্যা দেওয়া কঠিন। পাঠক তা সম্যক জানে বলে এখন আর একিন হয় না।
কবিতা কি মহৎ? কবিতা কি মন্ত্র? কবি কি দ্রষ্টা? কবিতাই কি মানুষের আন্তরতম শুদ্ধ উচ্চারণ? এসব প্রশ্ন কোনো একসময় মাথায় গিজগিজ করত। উত্তর খুঁজতে বসে অংবংছং কত কী ভেবেছি তখন! আজ ওসব কথা ভাবলে হাসি পায়। পাগল বিনয় মজুমদারের কবিতা-ফয়সালা বরং মাঝেমধ্যে সঠিক লাগে। যেসব কবিতা পাঠক অনেকদিন মনে রাখতে পারে, অনর্গল মুখস্থ আওরাতে পারে, বিনয়ের বিবেচনায় সেগুলো হচ্ছে মহৎ কবিতা। অন্যদিকে যে-কবিতারা একাধিকবার পাঠ করা সত্ত্বেও স্মরণে থাকে না,—সেগুলো পচা। নজরুলের বিদ্রোহী, সুধীন দত্তের শাশ্বতী ও উটপাখি, জগন্নাথ ভট্টাচার্যের ভাষান্তরে টি. এস এলিয়টের পোড়োজমির বেশ আর্ধেক, আল মাহমুদের সোনালী কাবিন-এর সনেটগুচ্ছ;—এরকম কত কবিতা যুবাকালে মস্তিষ্কে জায়গা নিয়েছিল। এখনো স্মরণ আছে দেখে মাঝেমধ্যে বেশ অবাক যাই! গড়গড় আবৃত্তি করা যায় সেগুলো। বিনয়ের সংজ্ঞা মেনে নিলে এগুলো মহৎ কবিতা। মেমোরিতে তারা স্থায়ীসঞ্চারী। ভ্যানিশ হয়ে যায়নি।
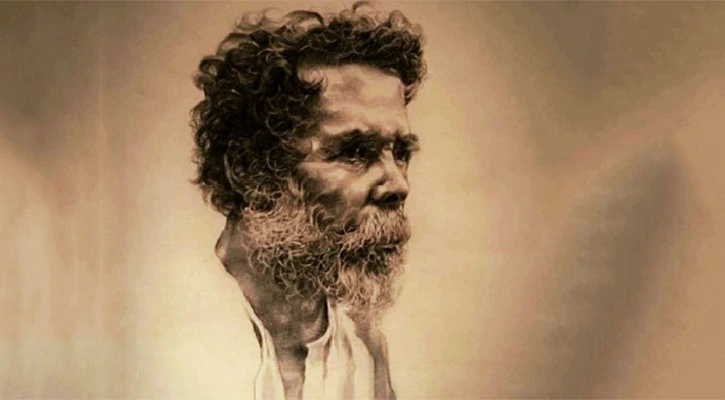
ভালো… বেশ ভালো! জীবনানন্দ দাশের কী হবে তাহলে? খোদ বিনয় অথবা শঙ্খ-শক্তি-অলোকরঞ্জনের মতো কবিদের নিয়ে কী করা যেতে পারে? সিকদার আমিনুল হক বা এরকম আরো-আরো কবি… তাঁদের কী গতি হবে সেখানে? যদি আগে বাড়ি,—আমার সময়ে বসে যারা লিখছেন, তাঁদের কবিতা কি তাহেলে ফেলনা? লাইন দিয়ে দাঁড়ানো কবিদের কবিতা তো কমবেশি পড়েছি বা পড়ে চলেছি এখনো! একটাও ছাই মনে থাকে না! অথচ পড়তে তো ভালোই লাগে তাঁদেরকে! পড়তে-পড়তে বহুত খুব বলতে মনে দ্বিধা থাকে না। তাঁরা কি তবে মহৎ কবি না?
বিনয় বেঁচে থাকলে উত্তরটি দিতে পারতেন হয়তো। অঙ্কের মাথা ভীষণ ক্ষুরধার ছিল তাঁর। ধারণা করি, অঙ্ক দিয়ে তিনি বিচারটি করেছিলেন। গণিতের সঙ্গে শুনেছি কবিতা নিবিড়ছন্দ। গণিত যখন বিমূর্তের দিকে ধায়,—কবিতায় লয় ঘটে তার। ফরহাদ মজহার বিষয়টি নিয়ে তিমির জন্য লজিকবিদ্যায় বেশ জমিয়ে লিখেছিলেন। মজহার অবশ্য ধ্রুপদি পাশ্চাত্য সংগীতের সঙ্গে পদার্থবিদ্যা ও গণিতের যোগ খুঁজে ফিরেছেন সেখানে। ধ্রুপদি সংগীত তো প্রকারান্তরে কবিতায় লীন বলে মত দিয়ে থাকেন কত না মহাজন! কবিতা ও সংগীত একে অন্যের মাঝে সমাহিত ও পূর্ণ হয়। বৈদিক মন্ত্র আর উপনিষদের স্তোত্র শুনলে যা বিলক্ষণ টের পাওয়ার কথা। সুর এখানে কবিতাকে, নাকি কবিতা সুরকে নির্ধারণ করছে,—বুঝে ওঠা দায় হয় অনেকময়!
এসব ভজকটের কারণে কবিতার ভালোমন্দ মাপজোক এখন আর মনকে টানে না। তবে হ্যাঁ, যে-কবিতাই পড়ি, সেখানে নিজের অনুভূতি ও ভাবনার ঝিলিক দেখতে পেলে ভালো লাগে। মানুষ মাত্রই নিজেকে নিয়ে ভাবে। তার ভালো লাগা ও খারাপ লাগা থাকে। মন ভালো ও খারাপ হওয়ার কারণরা চারপাশে গিজিগিজ করছে। নিজের জীবনদর্শন এসব থেকে শুষে নেয় তারা। বয়সের সঙ্গে যেগুলো আবার রূপ বদল করে অহর্নিশ।
সেদিন চায়ের স্টলে এক মহাবয়স্ক মুরব্বি বসা ছিলেন। দেখতে শক্তপোক্ত মনে হলেও মুখের বলিরেখা বুঝিয়ে দিচ্ছিল মুরব্বির বয়স হয়েছে। চায়ে চুমুক দিয়ে থু করে ফেলে দিলেন। চাওয়ালা মনে হলো তার পরিচিত। তড়িৎ তাকে পুছ করে,—কিতাবা মুরব্বি, চা কিতা ভালা অইছে নানি? মুরব্বির মুখের রেখায় রাজ্যের বিতৃষ্ণা জমা হয়েছে ততক্ষণে। আমার দিকে তাকিয়ে উত্তর করেন,—টেস পাইনারেবা। আগের টেস নাই জিভে। সব তিতা লাগের। মুরব্বির কথায় নিমেষে বুঝে গেলাম,—তার কাছে জীবন এখন পুরাই বিস্বাদ। দুনিয়া ছেড়ে পালাতে পারলে বাঁচেন। আল্লামিয়া হুকুম দিচ্ছেন না দেখে কোনো সুরত বাইছেন দেহতরী। মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে/ মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।—ছেলেবেলায় মুখস্থ ঠাকুরের কবিতাচরণ মুরব্বির সামনে আওরানো বিপজ্জনক! ঝাড়ি খাওয়ার সম্ভাবনা ছিল বিলক্ষণ। ধাম করে হয়তো বলে উঠতেন,—হেটামারানির জীবন! কিগুয়ে লিখছে ইতা?
চায়ের স্টল থেকে অনতিদূরে ফার্স্ট ফুডের দোকানের সামনে একদল চ্যাংড়াকে দেখলাম মহা উল্লাসে বার্গারে কামড় দিচ্ছে। তাদের জীবনদর্শন আপাতত রঙিন। তারা পার করছে রংয়ের জীবন। মুরব্বি পেরুচ্ছেন হেটামারানির জীবন। কবিতা কি তবে সেরকম কিছু? দেহে যখন জোয়ার আসে, তখন সে রংয়ের অশানাইয়ে মন মাতায়। ভাটার দিনে হেটামারানির সুরত ধরে। সুতরাং কোন কবিতা মহান আর কোনটা নগণ্য,—এসব নিয়ে ভাবনা করা বৃথা!
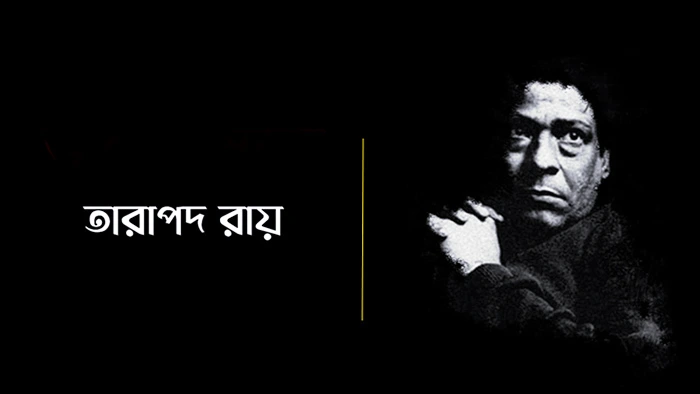
তারাপদ রায়কে দিয়ে শুরু করেছিলাম। তাঁর কাছে আবার ফেরত যাই। তাঁকে সুযোগ পেলে পড়ি? কেন পড়ি? উত্তরে মনে হচ্ছে কিছু কথা যুক্ত করা প্রয়োজন। তারাপদকে পাঠ যাওয়ার কারণ কি এই,—তিনি পড়তে সহজ? সোজাসরল ভাষায় কবিতা লিখেন। একবসায় টানের টান পড়ে ফেলা যায়। এরকম আরো অনেক কবি ছিলেন বা এখনো আছেন। তাঁরাও সহজ ভাষায় লেখেন, কিন্তু সবারটা পড়তে ইচ্ছে করে না। তারাপদের বেলায় ঘটনা বিপরীত। তাঁকে পড়তে ইচ্ছে করে। মানে দাঁড়াচ্ছে,—সহজ ভাষায় লেখার কারণে তাঁকে পড়ছি না। অন্যকিছু সেখানে থাকে বলেই পড়া। কী হতে পারে সেটি? ভাবতে বসে মনে হচ্ছে,—কবিতা লিখতে বসে তারাপদ কিছু একটা ঘটান, যার প্রভাবে চট করে নানান ছবি চোখে ভেসে ওঠে। স্মৃতি ও স্মৃতিকাতরতা দুটোই সক্রিয় হয় তাৎক্ষণিক। তাঁকে পড়তে কাজেই মন টানে।
এই যেমন বৃষ্টি নিয়ে শত-শত কবিতা বাংলা ও অন্যান্য ভাষায় লেখা হয়েছে! বৃষ্টিগন্ধি কবিতায় বিশ্ব ভরপুর। স্যাঁ-জন পের্স আনাবাজ লিখে গেছেন। রবি ঠাকুর বৃষ্টি নিয়ে অজস্র লিখেছেন। অমিয় চক্রবর্তীরা লিখেছেন। শহীদ কাদরীসহ কত শত নাম! কে লেখেননি খুঁজতে বসলে বিপদে পরবে অনুসন্ধানী। বৃষ্টিকে নিয়ে রচিত কবিতামালায় তারাপদের বৃষ্টি কবিতাটি অতিশয় দীনহীন। গোনায় আসবে না, অথচ কবিতার লাইনগুলো বেশ মনে থাকছে। পুরোটা না থাকলেও বৃষ্টিকে নিয়ে কবির সোজাসরল ভাবকুতা মনকে ভালোই বিমনা করে যায়।
কবি মনে করাচ্ছেন,—বৃষ্টির কোনো ঠিকঠিকানা নেই। কখন কীভাবে আসবে তার আগাম আন্দাজ করা কঠিন।তবে হ্যাঁ, ঝমঝম বৃষ্টি তারাপদ বেশ টের পেতেন ছেলেবেলায়। মফস্বল শহরে টিনের ঘরে শব্দ করে ঝরত দিন অথবা রজনী জুড়ে। সেই অনুভূতিকে ফেরত পাওয়ার পথ খোলা নেই। বৃষ্টি এখন ইটকাঠের দালান বেয়ে ঝরে অথবা চুঁইয়ে নামতে থাকে। তথাপি একথা সত্য,—বৃষ্টি সরল নয় একটুও। তার আচরণ বেশ জটিল। বোঝা দায় কখন সে ঝমঝমিয়ে আসবে, কখন ঝিরঝিরি বইতে থাকবে, কখন আবার ঘরে ডাকাত পড়ার মতো কিংবা পাগলা মোষ হয়ে তাড়া করবে ঘরদোর। কবি সারসংক্ষেপ টানছেন :
কিছুই বোঝা যায় না
কিছুই টের পাওয়া যায় না
হঠাৎ টের পাই,
বৃষ্টি এসে গেছে।
[বৃষ্টি : তারাপদ রায়]
সিম্পল, কিন্তু ভেবে দেখলে সুগভীর এই অনুভূতি,—বৃষ্টির মতোই আমাদের জীবন অবিরত মুড সুইং করে। কখন কোনদিকে কেমন মোড় নেবে বোঝা দায় হয় মাঝেমধ্যে! আচ্ছা, সে নাহয় বোঝা গেল। এ-কারণে কি তাঁকে পড়তে আরাম? বানান নিয়ে তাঁর লেখা কবিতাটি অদ্য মনে পড়ছে। কবিতার শেষ স্তবকে এসে এক গ্রাম্য কবির বরাতে কবি লিখছেন,—কবিবরটি তাঁর নাম তারাপদ না লিখে তাড়াপদ লিখতেন। সত্যিই তো, ভেবে দেখলে মানুষ তারার ছাইভস্ম থেকে জন্ম নেয়, ওদিকে জন্ম নেওয়ার পর থেকে তাকে আমরা তাড়া আর তাড়ার চোটে কেবল ছুটতে দেখি! পা দুখানা তাড়ায় চলছে সারাখন! রংয়ের জীবনে হাবুডুবু খাওয়ার তাড়া থেকে সে আচমকা পা দিয়ে বসে টেস নাইয়ের হেটামারানি জীবনে। তারপর বলাকওয়া নেই,—ভ্যানিশ! তারায় গিয়ে মিশে বোধহয়। রঙ্গচ্ছলে গভীর কথা যে-কবি বলতে পারেন তাঁকে ভালো তো লাগবেই!
আপাতত একটি উত্তর পাওয়া গেল। তারাপদ রায়ের কবিতা ভালো লাগার পেছনে আর কী কারণ থাকতে পারে? মনে হলো একথা বোধহয় বলা যায়,—তাঁর উচ্চারণ অলঙ্কারহীন সুন্দর। শঙ্খ ঘোষে যেটি সর্বদা পায় পাঠক। তারপদের কবিতায় তা আরো খোলামেলা ও নগ্ন হয়ে ফোটে। কোনো আড়ম্বর নেই। ভান-ভণিতা নেই। ঢেঁড়া পিটিয়ে নিজেকে ঘোষণা দেওয়ার মহাকাব্যিক তোড়জোর নেই। রসেবশে জীবনকে জড়িয়ে দিব্যি লিখছেন ভদ্রলোক। গল্প লিখছেন। মাতালকে নিয়ে গদ্য লিখছেন। সবটাই রসে চোবানো রসগোল্লা। পড়তে ঝাক্কাস লাগে মাইরি। সৈয়দ মুজতবা আলীর মিনি সংস্করণ যেন! সৈয়দের পাণ্ডিত্যমাখা রসে ডুবডুবা বুলির জায়গা নিয়েছে কবির সহজাত সচেতনা আর চারপাশকে নজরবন্দি করার অভ্যাস থেকে উঠে আসা শব্দরাশি। কী অনায়াস বলে দিচ্ছেন :
এই সেদিন পর্যন্ত ভেবেছি, সব ঠিক হয়ে যাবে।
কবে কখন কেমন করে, কি ভাবে ঠিক হবে,
এবং সত্যি সত্যি কি ঠিক হবে, এবং ঠিক না হলেই বা কি হবে,
সে বিষয়ে অবশ্য কোনো চিন্তা করিনি
কোনো ধারণাও ছিলো না।
শুধু কোথায় কেমন একটা আলগা বিশ্বাস ছিলো,
মনে মনে ধরে রেখেছিলাম,
একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে।
একটা ক্ষীণ ভরসা ছিলো এই সেদিন পর্যন্ত,
যেভাবে এইসব ঘটে, এই সব ঘটে যায়
সেইভাবে একদিন সব ঠিকঠাক হবে।
আমার কিছু করণীয় নেই, শুধু বসে থাকার অপেক্ষা।
[সব ঠিক হয়ে যাবে : তারাপদ রায়]
পঙক্তিলো নিয়ে যত ভাবতে যাবো, মনে হবে কবিরা এই জায়গায় এসে আলাদা হয়ে ওঠেন। মোটা কিতাব লিখে যা বোঝায় পণ্ডিত, গভীর অনুধ্যানে ডুবে থেকে দার্শনিক যার অর্থ করেন,—বোঝাবুঝির ওসব মামলাকে কেবল কবিরা এভাবে ঝটকা টানে তামাদি করে সত্যিটি বলে দিতে পারেন। তারাপদ যেমন পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন,—সবকিছু ঠিকঠাক হওয়ার আশা হচ্ছে এমন এক অপেক্ষার নাম যেটি কখনো পূরণ হওয়ার নয়। কবিকে ভালো লাগার মস্ত কারণ এখানে আছে মনে হয়। আটপৌরে শব্দের গাঁথুনিতে যে-ছবি তাঁর কবিতা জাগিয়ে তোলে, সেখানে কবিতার চিরাচরিত অন্তরাল রহস্য তা-বলে খোয়া যাচ্ছে না।
নিজের লেখা কবিতায় এক বন্ধুর কথা স্মরণ করছেন কবি। তার নাম ছিল শত্রুজিৎ। কার এখন ঠেকা পড়েছে তাকে শত্রুজিৎ নামে ডাকার! শত্রুজিৎ না ডেকে সবাই তাকে সংক্ষেপে শত্রু নামে ডাকা শুরু করেছিল। কাউকে বোঝানোর উপায় থাকল না,—শত্রুকে জয় করার বাসনায় বাপমা তার নাম শত্রুজিৎ রেখেছিল। আদিনাম বেচারা নিজেও ভুলে গেল বেমালুম। জীবন হচ্ছে এরকম তামাশার নাম। তাকে জয় করতে নেমে উলটো নিজেই শত্রু বনে যেতে হয়! সহজসরল প্রবচনঘন আবেশ মিশিয়ে জীবন নামের তামাশাকে নিরন্তর লিখে গেছেন তারাপদ রায়। এখন বলতে পারি,—তাঁর কবিতায় নিজ জীবন মুকুরিত দেখতে পাই বলে হয়তো তাঁকে পড়তে ভালো লাগে। সহজ কথা যায় না লেখা সহজে;—রবি ঠাকুরের কথাকে তারাপদ মিথ্যা প্রমাণ করেছেন। গভীর কথাকে সহজ করে লিখেছেন আজীবন।
আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেছে;—কবিতাটি কে না পড়েছেন! কে না কোট করেন যখন-তখন! তো এই কবিতাচরণে যে-পালাবদলের ছবি অভাসিত দেখি সেটি চিরন্তন! সময় বদলায়, মানুষ পালটায়, তার সঙ্গে গভীর হয় জখম। আমরা টের পাই ভালো করে সবকিছু বুঝে ওঠার আগে চারপাশ কতটা বদলে গেছে! অচেনা লাগে সব! তার মধ্যে রংয়ের জীবন থেকে হেটামারানির জীবনে ধাবমান তারাপদ অনায়াস বলতে পারেন :
একটি হিমেভরা রাত একা একা
হাল ছেড়ে দেওয়া গাছের ডালে
টিকে থাকতে যে সাহস লাগে,
সেই সাহস সকলে বুঝতে পারে না,
সকলের বোধগম্য নয়।
[সেই সাহস : তারপদ রায়]
এই অনুভব যিনি কবিতায় অনায়াস করে তুলতে পারেন তাঁকে না পড়ে উপায় আছে?
. . .
. . .





