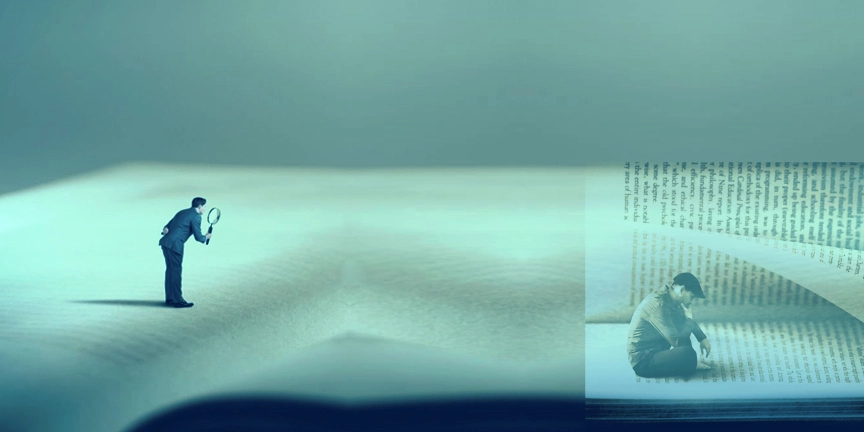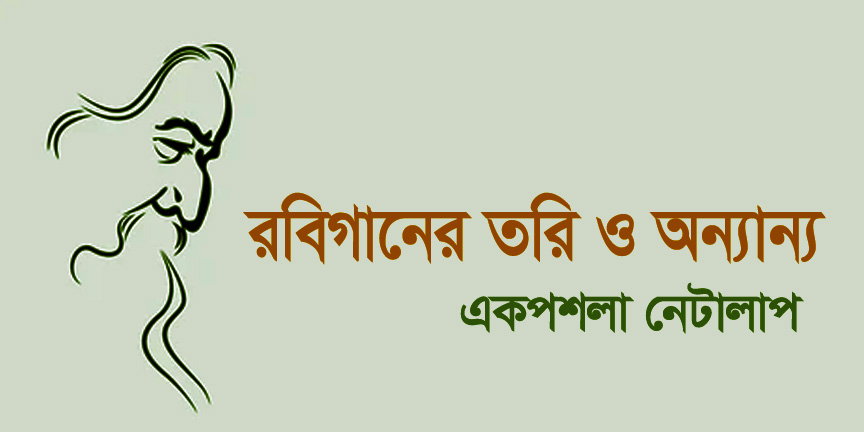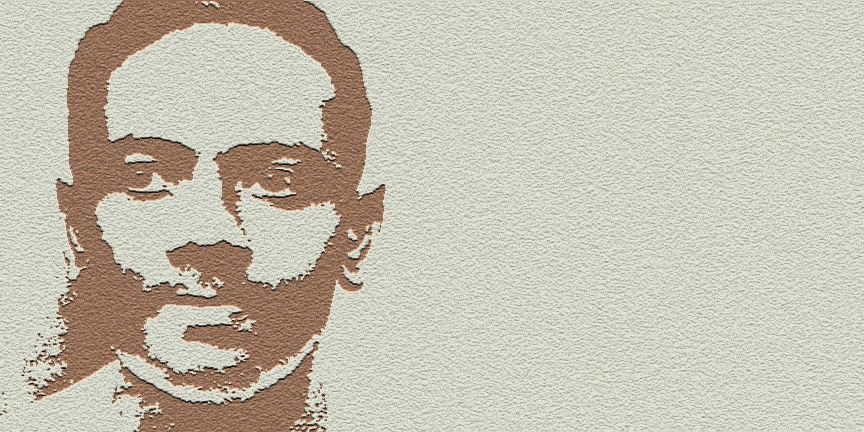বইপ্রেমীরা কি আসলেও বই পাঠ করে? আমার মনে হয়, জরিপ করলে ভিমড়ি খাওয়ার মতো তথ্য পাওয়া যাবে। দেখা যাবে,—আকাটের দল বই জমায়, কিন্তু পড়ে না। পড়া ও পড়ার ভান করা পৃথক ঘটনা। তবে এই-যে তারা পড়ে না, তাতে আমি আনন্দিত। সভ্যতা এতো-এতো বেশি বইয়ে বোঝাই হয়ে আছে, মানুষের হয়তো প্রয়োজন আছে পুনরায় মূর্খ হওয়ার। মূর্খতা নিয়ে আসতে পারে অজ্ঞতা ও সারল্য। সেইসঙ্গে পতন। সেখান থেকে পুনরায় শুরু করতে পারবে মানুষ। মন্দ নয় যদি তা ঘটে ভবিষ্যতে।
-
-
পাঠক টের পান—যা লেখা হয়নি, তার মাঝেই নিহিত থাকে পাঠের সবচেয়ে গভীর অর্থ। অলিখিতই হয়ে ওঠে জাগ্রত বাক্য। অবশেষে আসে এক নীরব উচ্চতা—যেখানে শব্দ ফুরিয়ে যায়, অর্থ ঝরে পড়ে, কেবল অনুভবের আলো জেগে থাকে। পাঠক বুঝে নেন—পাঠের চূড়ান্ত অর্থ কোনও উত্তর পাওয়া নয়, বরং উত্তরহীনতার সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করা। টের পান, প্রতিটি বই আসলে একটিই বই; মহাকালের প্রান্তরজুড়ে ছড়িয়ে থাকা এক অসীম, অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি।
-
কেবল পপ নয় তাহসিন ভাই, নির্ভেজাল রক মেজাজেও-যে সবসময় খারাপ লাগে শুনতে, তা কিন্তু নয়। রবীন্দ্রনাথ তো আসলে এমন সামগ্রী, তাঁকে নানাভাবে ভাঙা জরুরি হয়ে দাঁড়ায়। ঠাকুরের গানের ভাণ্ডারে বিচিত্র গান যেহেতু রয়েছে, একালের মেজাজ বুঝে নিরীক্ষা হতে পারে ও হওয়া উচিত।
-
এইখানে আলবেয়ার কামু জরুরি হয়ে ওঠেন। কামু দেখান,—ঈশ্বর থাকুন বা না-থাকুন, মানুষের দুঃখ বাস্তব। তাই নৈতিকতার ভিত্তি অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ বা পরকাল নয়; নৈতিকতার ভিত্তি হলো এই মুহূর্তের অন্যায়। আমরা ঈশ্বরের অপেক্ষায় বসে থাকি না। ঈশ্বর থাকলেও আমরা তাঁর ‘প্রতিনিধিত্ব’ দাবি করি না। অন্যায়ের সামনে নিজে দাঁড়াতে চাই;—এটাই মানুষ হিসেবে আমার নৈতিক অবস্থান।
-
জীবনানন্দ এর থেকে নিষ্ক্রমণ খুঁজেছেন এমন এক প্রাকৃতিকতায়, যেটি নিজে ক্লিয়ার করে দিচ্ছেন,—পৃথিবীতে এর অস্তিত্ব স্বপ্নের মতো পৌরাণিক। তাঁর রচনায় আমরা একসময় দালি ও অঁদ্রে ব্র্যতোঁদের তৈরি পরাবাস্তব ইশতেহারে খুঁজে নিয়েছি। এখন তা অবান্তর লাগে নিজের কাছে। কারণ, জীবনানন্দের মধ্যে পরাবাস্তবতা নয়, বরং সক্রিয় থেকেছে ডিল্যুশন!