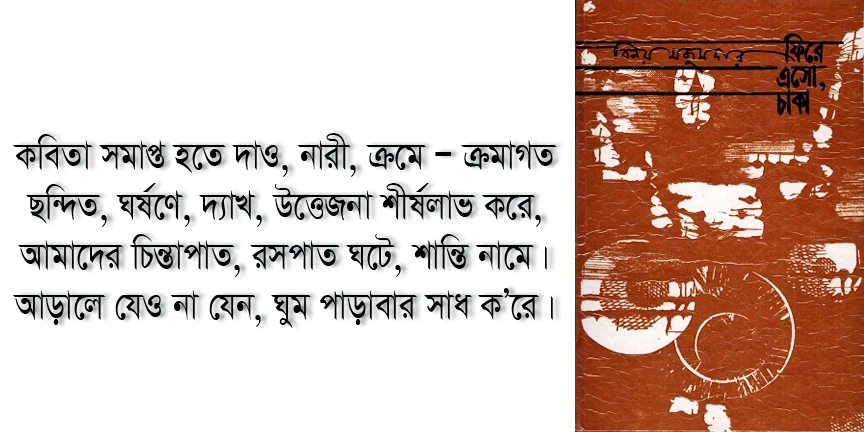মানবিক বিদ্যায় যুগান্তকারী অবদান রাখায় কিছুদিন আগে দুইহাজার পঁচিশ সনের হলবার্গ পুরস্কার পেয়েছেন গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক। মানবিক বিদ্যার প্রধান কিছু ক্ষেত্র যেমন শিল্পকলা, সমাজবিজ্ঞান, আইন ও ধর্মতত্ত্বে যেসব গুণীজন অবদান রাখছেন, তাঁদের জন্য নোবেল অথবা সমমানের পুরস্কার প্রচলিত ছিল না। ঘাটতি পূরণে নরওয়ে সরকার এগিয়ে আসেন। প্রখ্যাত লেখক লুডভিগ হলবার্গের নামে স্বীকৃতিটি তারা চালু করেছেন। হলবার্গ প্রাপ্তদের নিয়ে নোবেলজয়ীদের মতো হইচই না হলেও পুরস্কারটিকে নোবেলের সমতুল্য ধরা হয়। অর্থমূল্যও নোবেলের কাছাকাছি রেখেছেন নরওয়ে সরকার।
গায়ত্রী চক্রবর্তী পুরস্কারটি পাওয়ায় সমাজমাধ্যমে অনেকে তাঁকে নিয়ে পোস্ট দিয়েছিলেন। হলবার্গের নামখানা সেই সুবাদে সকলের কাছে কমবেশি পৌঁছেছে। এপার-ওপার দুই বাংলা জুড়ে বাঙালির যে-ভয়াবহ অধঃপতন অব্যাহত রয়েছে, সেখানে বাঙালিজীবনে একসময় দেখা দেওয়া আলোকায়নের শেষ উত্তরসূরি হিসেবে গায়ত্রী এখনো বেঁচেবর্তে আছেন। তাঁর প্রজন্মের অনেকে বিদায় নিয়েছেন ধরা থেকে। যে-শূন্যতা এর ফলে তৈরি হচ্ছে, সেটি পূরণ করার মতো ব্যক্তিত্বের আকাল চলছে বাংলায়।
পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব এশিয়া ছাড়াও ভারতবর্ষের দক্ষিণ ভারত থেকে এই অঞ্চলে বসবাস করতে আসা জাতিগোষ্ঠীর ডিএনএ বাঙালি তার দেহে বহন করছে। বৈচিত্র্য ও ভিন্নতায় অনন্য হয়ে উঠতে এই বংশগতি কোনো একসময় নীরব ভূমিকা নিভিয়েছিল। বর্তমান পরিস্থিতি সেদিক থেকে সুবিধার নয়! কালের লিখনে বাঙালির সুদিন ফুরিয়েছে। ফতুর ছাড়া তাকে অন্য নামে ডাকা আসলেও কঠিন! সীমিত বা সর্বজনীন আকারে সহসা নতুন কোনো আলোকায়নের ছটায় উদ্ভাসিত হওয়ার সম্ভাবনা শূন্য। গায়ত্রীর মতো হাতেগোনারা শেষ আলোকরশ্মি হিসেবে কেবল বিকিরিত হচ্ছেন। তাঁরা বিদায় নিলে অমাবস্যা আটকানো যাবে বলে মনে হচ্ছে না।
গায়ত্রী নিজে অবশ্য জাতিত্বের সংকীর্ণ গণ্ডিতে কখনো অবরুদ্ধ থাকেননি। তরুণ বয়স থেকে জাতি-সম্প্রদায়-রাষ্ট্রকে ঘিরে চলতে থাকা জাতীয়তাবাদ ও সাম্প্রদায়িক মাতনের বাইরে তাঁর বিচরণ চলেছে। তা-বলে বাঙালি-নাড়ির সঙ্গে সংযোগ বেমালুম ভুল মেরে বসেছেন,সেকথা বলা যাচ্ছে না। বিশ্বজননীতার সঙ্গে স্থানিকতাকে কীভাবে মননে ধরেছেন বিদূষী, সেটি উপলব্ধির সময় বোধহয় বাঙালির হয়েছে। তাঁকে নিয়ে চর্চাকে যে-কারণে অবান্তর ভাবার সুযোগ নেই। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নবীকরণে অসমর্থ বাঙালি জাতিসত্তার পক্ষে এছাড়া সামনে আগানো কঠিন হবে। গায়ত্রীর হলবার্গে সম্মানিত হওয়াটা কাজেই প্রেরণা ও গুরুত্ব বহন করছে।
উত্তর-আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির গবাক্ষ এই অঞ্চলে যাঁরা উন্মুক্ত করছিলেন, তাঁদের মধ্যে গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক অন্যতম। নিম্নবর্গ নিয়ে আলাপে রণজিৎ গুহ যদি সাক্ষাৎ মহীরুহ হয়ে থাকেন, গায়ত্রী সেই মহীরুহরসে পরিপুষ্ট বটে। তাঁর সুবাদে সারা বিশ্ব জ্যাক দেরিদাকে ভালোভাবে চিনেছিল। অব গ্রামাটোলজির ইংরেজি ভাষান্তরে চোখ রাখলে গায়ত্রীর দীর্ঘ মুখবন্ধে পাঠক প্রবেশ করে। মুখবন্ধটি যেখানে দেরিদার পাশাপাশি অনুবাদকের মননশীল গভীরতা টের পেতে তাকে সহায়তা করে ব্যাপক। অব গ্রামাটেলজির মতো জটিল বইয়ের ভাষান্তরে গায়ত্রীর সাবলীল স্বাচ্ছন্দ্য একাধারে উপভোগ্য ও বিস্ময়কর বটে!
নবনীতা দেবসেন, কেতকী কুশারী ডাইসন ও গায়ত্রী চক্রবর্তী একদিন কলকাতা মাতিয়ে রেখেছিলেন। রূপের সঙ্গে বিদ্যার ধারে বিদ্বৎসমাজ কাঁপিয়েছেন তিনজন। জনশ্রুতি রয়েছে,—বাংলার পাগল কবি বিনয় মজুমদার গায়ত্রীবাণে জখম হয়েছিলেন বেশ। এর সত্যতা নিয়ে সন্দেহ ও বিতর্ক অবশ্য জারি থেকেছে সবসময়। কবিমনে জায়গা নেওয়া গায়ত্রী আর পরে দেরিদা-ভাষ্যকার ও ভাবুক হয়ে ওঠা গায়ত্রীকে ঘিরে বাদানুবাদ সাহিত্যমহলে অনেকদিন ধরে চলেছে। বিনয় মজুমদার পরে যেন-বা ইচ্ছা করে আরো ঘোলাটে করেছেন এই জনশ্রুতি। তিনি যে-গায়ত্রীশরে একদা জখম হয়েছিলেন, এর সঙ্গে প্রেসিডেন্সি ও পরে বিশ্ব কাঁপানো বিদূষী গায়ত্রীর সম্পর্ক নেই;—কবি নাকি কথাচ্ছলে কথাটি বলেছেন সময়-সময়। হতেও পারে!
জনশ্রুতির প্রভাব এই-যে, অপলাপকে সত্য ভাবার আবেশ মনে স্থায়ী হয় তাতে। মিথ্যা জেনেও কেন জানি একে আঁকড়ে ধরে মানুষ। বিনয়ের গায়ত্রীবাসনার কাহিনি সেরকম কিছু হলেও হতে পারে। তিনি যে-গায়ত্রীবাণে শরবিদ্ধ হওয়ার কথা পরে বলেছেন, এখন সেই নারীকে কারো মনে নেই। ভুবনবিদিত গায়ত্রী চক্রবর্তীর মাঝে তার বিলয় ঘটেছে। বিনয়ের নামের সঙ্গে ঘুরেফিরে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র পড়ানো ডাকসাইটে বিদূষী গায়ত্রীর নামখানা অবিচ্ছেদ্য জুড়ে গিয়েছে।
ফিরে এসো চাকার ঘোরলাগা পঙক্তির মধ্যে ভুবনবিদিত গায়ত্রীকে যে-কারণে ছেটে ফেলা সম্ভব হয়নি। সে যাইহোক, বইখানা কিন্তু বিনয় মজুমদার জনৈক গায়ত্রী চক্রবর্তীকে উৎসর্গ করেছিলেন। গায়ত্রী নামে শীর্ণ একখানা কবিতাবই তিনি ছাপেন ওইসময়, যেটি পরে ফিরে এসো চাকার বর্ধিত কলেবরে রূপ নিয়েছিল। সুনীলের নীরার মতো বিনয়ের গায়ত্রীও হয়তো বাস্তবে দেখা, এবং পরে কবিতায় রহসময়ী প্রতীকে পরিণত কোনো নারী। তাকে যেখানে বাস্তবের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে কবি স্বয়ং অনিচ্ছুক থেকেছেন পরে! সুতরাং এই নারী প্রতিমাকে ঘিরে জল্পনা ও তর্কঝড়কে গবেষকের জিম্মায় রাখাটাই অনেকে উত্তম বলে ভাবেন।
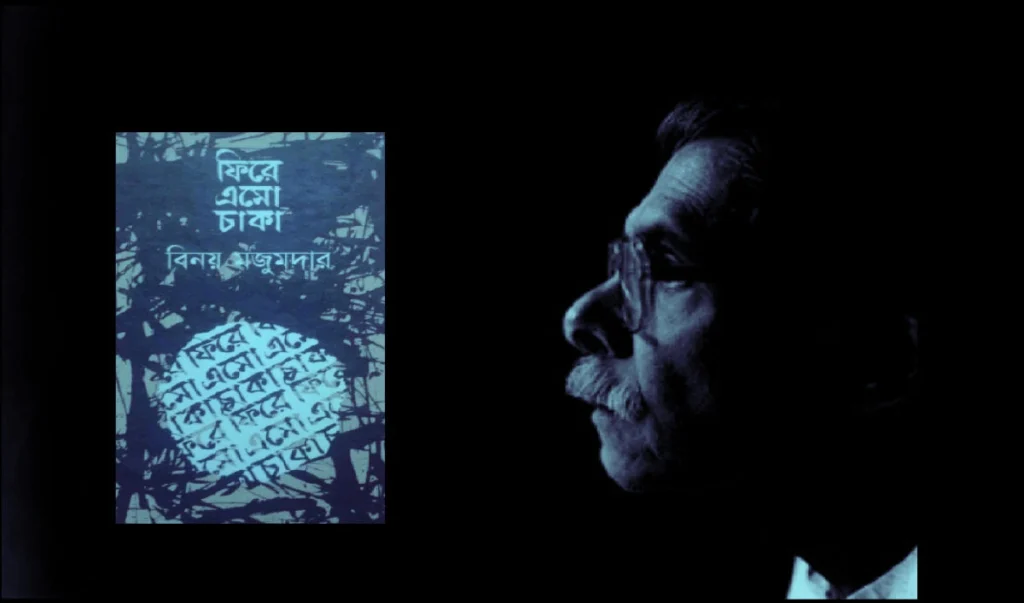
কথাটি তথাপি সত্য,—ফিরে এসো চাকার আশ্চর্য কবিতা-সমষ্টি প্রেরণাদায়ী আবেশে লেখা, যার নেপথ্যে নারীশক্তির ছায়া সক্রিয় ছিল। সংকলিত কবিতারা যে-ঘোরগ্রস্ত চিত্রকল্পে বিস্তারিত করে নিজেকে, এখন এর অর্থ ও ব্যাপকতা নিয়ে আমি বলার কেউ নই। পাঠকরা যথেষ্ট জানেন বিনয় মজুমদার কী কাণ্ড ঘটিয়েছেন সেখানে। জনশ্রুতির প্রভাবে হবে হয়তো,—বইয়ের কবিতাগুলোকে গায়ত্রীর সঙ্গে মিল করে পড়তে কেন জানি বেশ লাগে। এভাবে পাঠ করলে মনে হয় কবিতার ধোঁয়াশাঢাকা উচ্চারণ ধরতে পারছি। এছাড়া বইটি উদগ্র মাংসলোভী কবির অবচেতন থেকে উঠে আসা হেঁয়ালির সাংগিতিক লহরির বাইরে অতিরিক্ত আবেদন জাগ্রত করে না।
ষাটের দশকে প্রথম দুটি বছরের মধ্যে সবগুলো কবিতা লিখেছেন বিনয়। তখনো তিন অফুরন্ত যুবা। প্রকৌশলী হওয়ার সম্ভাবনা ধরে রেখেছেন। ইচ্ছে করলে নামকরা গণিতবিদ হতে পারতেন অনায়াস। আর্যভট্ট, ভাস্করাচার্য ও রামানুজনের পরে আমরা হয়তো আরেকজন ভারতীয় গণিতবিদ পেতাম। শক্তি-সুনীল আর হাংরিদের পাল্লায় পড়ে সব লাটে উঠেছিল। গণিতবিদ হওয়ার বাসনায় জলাঞ্জলি দিয়ে বিনয় নিজেকে বন্দি করলেন কবিতায়। সর্বনাশা যে-সম্মোহন তাঁকে ক্রমশ সমাজ থেকে নির্বাসিত উন্মাদ করে দিয়েছিল।
ফিরে এসো চাকার কবিতাগুলো যখন লিখছেন ঘোরগ্রস্ত বিনয় মজুমদার,—গায়ত্রী চক্রবর্তী ততদিনে কলকাতায় প্রেসিডেন্সির পালা চুকিয়ে পাড়ি জমিয়েছেন আমেরিকায়। বিশ্বমঞ্চে তারুণ্যদীপ্ত বুদ্ধিজীবীর উত্থান-সম্ভাবনা রচিত হলো তাতে। পড়ন্ত বয়সে সুনীল স্মরণে আয়োজিত কবিতালাপে গায়ত্রী বলেছেন সেসব কাহিনি। কলকাতা লিটারারি মিট-এ তাঁকে বলতে শুনেছি,—প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরেজি সাহিত্যের পাঠ নেওয়ার সময় পরীক্ষা কীভাবে পাস দিতে হয় সে তাঁর খুব ভালো জানা ছিল। আমেরিকায় এসে দেখলেন পরীক্ষা ভালো দিতে জানেন ঠিক আছে, কিন্তু কীভাবে চিন্তার জাল বুনতে হবে, এই ব্যাপারে তিনি বিলকুল আনাড়ি! চিন্তা করার পন্থা দেশে থাকতে জানাবোঝার সুযোগ ঘটেনি।
চিন্তা করার পন্থা বিষয়ে যে-অজ্ঞতার আলাপ গায়ত্রী তুলেছেন, এর পেছনে ভারতবর্ষের দায় অনেকখানি। গুছিয়ে চিন্তা করার পদ্ধতি অতিকায় ভূবর্ষে একসময় মজুদ ছিল। কালের স্রোতে এর সবটা খোয়া যাওয়ার কারণে ভারতবাসী ফকিরের জাতে পরিণত হয়েছেন। অজ্ঞতা ও মূঢ়তার কূপে বসবাস তাদের নিয়তি এখন! তা-সত্ত্বেও খণ্ডিত বা আংশিক আলোকায়নের শিখা ঊনবিংশ শতকে বাংলায় জ্বলে উঠেছিল। পরিবার সূত্রে গায়ত্রী এর আঁচ পেয়েছিলেন। চিন্তানির্ভর বয়ান তৈরিতে আঁচটি যদিও তাঁকে সাহায্য করেনি। টালমাটাল যেসব পরিস্থিতির ভিতর দিয়ে ভারতবর্ষকে পরবর্তীতে দুফাঁক হতে হলো, সেখানে চিন্তা করার পরিসর ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েছিল। গায়ত্রী কাজেই সাহিত্যপাঠে ঋদ্ধ হলেন, ইংরেজিটা মাতৃভাষার মতো রপ্ত করলেন ষোলআনা, কিন্তু পরবর্তী ধাপে গমনের তাগিদ ইংরেজের রেখে যাওয়া কলকাতা তাঁকে দিতে পারল না!
মৈত্রেয়ী দেবী যেমন অভিজাত পরিবারের মেয়ে হওয়ার সুবাদে রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে নামজাদা সব বাঙালিকে ঘরের উঠানে দেখে বড়ো হয়েছেন, গায়ত্রীর বেড়ে ওঠা প্রায় অনুরূপ ধরা যেতে পারে। বনেদি পরিবার তাঁর জন্ম। আলোকায়নের ছটা তিনি না চাইলেও তাঁর ওপর আপনা থেকে পড়ত বৈকি। তো সেই গায়ত্রী পাড়ি জমালেন আমেরিকায়। ইংরেজি তো ছিলই, তার সঙ্গে ফরাসি শিখলেন। দেরিদার কিতাব তর্জমা করে চমকে দিলেন বিশ্ব! সেইসঙ্গে নিজে হয়ে উঠলেন বিশ্বমঞ্চে রাজ করতে থাকা প্রথমসারির বুদ্ধিজীবীদের একজন। তাঁর এই জার্নির কাছে বিনয়ের কারুবাসনাকে সামান্য মনে হওয়া অবান্তর নয়। ভাবনাটি অবশ্য ভুল। গায়ত্রী তাঁর নিজ মেধায় আমাদের মুখ যে-পরিমাণে উজ্জ্বল করেছেন, বিনয় তাঁর কবিতা দিয়ে মন কেড়েছেন বাঙালির।
বিমলকৃষ্ণ মতিলাল দেশে থাকতে গায়ত্রী কিছুদিন তাঁর সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। তরুণীর মধ্যে তীক্ষ্মতা ঠার করতে মতিলালের অসুবিধা হয়নি। এমন এক তীক্ষ্মতা যেটি কেবল ধারে নয়, ভারেও কাটছে! তাঁর সঙ্গে দর্শনের আলাপ করে বেশ আনন্দ পেতেন মতিলাল। গায়ত্রী এভাবে ক্রমশ অন্যগ্রহের মেয়েতে পরিণত হলেন। বিনয় ওদিকে ততদিনে ছেপে ফেলেছেন ফিরে এসো চাকার প্রথম সংস্করণ। বইয়ের প্রথম স্তবক বুঝিয়ে দিচ্ছিল এই কবির পাগল হতে অধিক দেরি নেই :
একটি উজ্জ্বল মাছ একবার উড়ে
দৃশ্যত সুনীল কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে স্বচ্ছ জলে
পুনরায় ডুবে গেলো—এই স্মিত দৃশ্য দেখে নিয়ে
বেদনার গাঢ় রসে অপক্ক রক্তিম হ’লো ফল
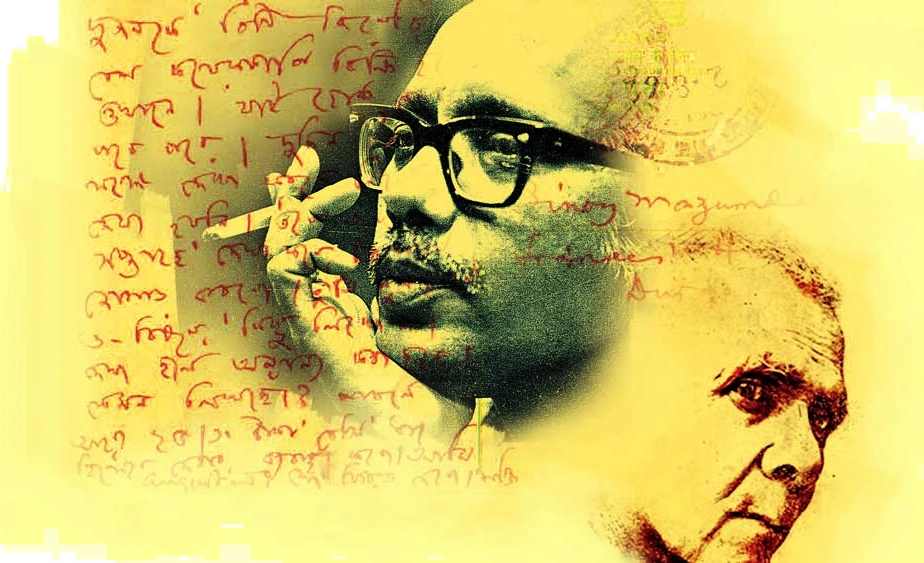
স্তবকটির ব্যাখ্যা অনেকে অনেকভাবে করে থাকেন বলেই জানি। আমার কেবল ঘুরেফিরে গায়ত্রীকে মনে পড়ে! বিনয় যেন চুপিসারে আলোকসামান্য তরুণীকে লুকিয়ে-চুরিয়ে দেখছেন কবিতায়! তাঁর এই দেখাটা দালির ক্যানভাসে ঘনীভূত পরাবাস্তব দৃশ্যের মতো তাকলাগা বিভূতিতে ভাস্বর। উজ্জ্বল মাছ জলফুঁড়ে আকাশমুখী হয়ে চারপাশটা দেখে নিচ্ছে একবার। নিমেষে বুঝে গিয়েছে,—জলের ঊর্ধ্বে বহতা জীবনের সঙ্গে তার যোগ থাকলেও সেটি পারস্পরিক নয়। জলের ঊর্ধ্বে বহমান জীবনরস পলকে দেখে নিয়ে ফের জলের গভীরে ডুব দেওয়াতে আছে পরিতোষ। পরস্পর থেকে দূরে অবস্থান করলেই শুধু একে অন্যের কাছে আসার আকুলতা সার্থক হয়!
তরুণ বিনয় টের পেয়ে গেছেন,—অবক্ষয় হচ্ছে আস্তিত্বের সারকথা। প্রোজ্বল কোনো গায়ত্রীকে যে-কারণে ইহজন্মে তাঁর পাওয়া হচ্ছে না। না মুখ ফুটে বলতে পারবেন,—ভালোবাসি! দেখাটাই একমাত্র নিরাময় সেখানে। বলতে যেয়েও না বলতে পারার আকুতি ফিরে এসো চাকার অন্তিম সার্থকতা নির্ধারণ করে যায়। বিভূতিবিবশ কবি যেখানে বলছেন :
বিপন্ন মরাল ওড়ে, অবিরাম পলায়ন করে ,
যেহেতু সকলে জানে তার শাদা পালকের নিচে
রয়েছে উদগ্র উষ্ণ মাংস আর মেদ;
স্বল্পায়ু বিশ্রাম নেয় পরিশ্রান্ত পাহাড়ে-পাহাড়ে;
সমস্ত জলীয় গান বাষ্পীভূত হয়ে যায়, তবু
এমন সময়ে তুমি, হে সমুদ্রমৎস্য, তুমি… তুমি…
কিংবা, দ্যাখো, ইতস্তত অসুস্থ বৃক্ষেরা
পৃথিবীর পল-বিত ব্যাপ্ত বনস্থলী
দীর্ঘ-দীর্ঘ ক্লান্তশ্বাসে আলোড়িত করে;
তবু সব বৃক্ষ আর পুষ্পকুঞ্জ যে যার ভূমিতে দূরে-দূরে
চিরকাল থেকে ভাবে মিলনের শ্বাসরোধী কথা।
শেষ দুটি লাইন যতবার পড়ি, আমার চোখ গায়ত্রীকে দেখে। কোন গায়ত্রী? মেধাসুন্দরী চপলা কোনো নারী? শ্যামাঙ্গিনী আবেশ ছড়ানো কেউ? ছাইপাশ প্রশ্ন কবিতাচরণ পাঠের সময় মাথায় থাকে না। মনের তারে কেবল গায়ত্রীমন্ত্রের মতো নিঝুম এক গায়ত্রীর আনাগোনা চলে ক্ষণিক। পলকে মিলিয়েও যেতে দেখি তাকে! পরে হয়তো একথা মনে ভাসে,—বিনয় মজুমদার ও গায়ত্রী চক্রবর্তী নামধারী মানব-মানবী হতভাগা বাঙালিকুলে গর্বের ধন। দুজনে কি হতে পারতেন দুজনার? রূপ, গুণ আর বিদ্যায় সরস্বতী গায়ত্রীর পাশে বিনয়কে কি মানাত সঠিক? হয়তো মানাত! হয়তো মানাত না ঠিকঠাক! কবিতাপাঠের তাৎক্ষণিক আবেশ কাটিয়ে উঠার পর এই-যে ভাবনা মনে জাগে, এর কোনো যৌক্তিকতা নেই, তবে এরকম ভাবতে মন্দ লাগে না তখন।
অন্তর্মুখীতা কবিকে সম্পদবান যেমন করে, শাস্তি স্বরূপ তার থেকে কেড়ে নেয় ততোধিক। তাকে কয়েদ রাখে সঙ্গহীন জেলখানায়। অনেকানেক গায়ত্রীকে কবি কামনা করছে, কিন্তু মুখ ফুটে তার বাসনাকে ভাষা দিতে বিফল হয় বারবার। দ্বন্দ্বটি অগত্যা কবিতার ভাষায় কৌণিক বিচ্ছুরণ হয়ে ফেরত আসে। ফিরে এসো চাকার কবিতারা সেরকম। এখানে যে-কবিসত্তাকে পাচ্ছি, তার ভিতরটা বেদনায় পরিপক্ক জখম অনুভব করে বিদীর্ণ। কবি সেখানে বলছেন :
ঘন অরণ্যের মধ্যে সুর্যের আলোর তীব্র অনটন বুঝে
তরুণ সেগুন গাছ ঋজু আর শাখাহীন, অতি দীর্ঘ হয়;
এত দীর্ঘ যাতে তার উচ্চ শীর্ষে উপবিষ্ট নিরাপদ কোনো
বিকল পাখির চিন্তা, অনুচ্চ গানের সুর মাটিতে আসে না।
এই স্তবক পাঠ করলে এক-একসময় মনে হয়, প্রেসিডেন্সির গেটের বাইরে অথবা হতে পারে ওরকম কোনো জায়গায় দাঁড়িয়ে কোনো এক গায়ত্রীকে প্রাণপণ দেখার চেষ্টা করছেন কবি বিনয়। বাস্তবে কাজটি হয়তো তিনি ভুলেও করতে যাননি কখনো। তবু মনে হয়,—তিনি তা করেছেন বিলক্ষণ! কবি বিনয়ের জন্য গায়ত্রী সেই তখন থেকে অতিক্রম করা যায় না এরকম এক উচ্চতার শিরোনাম। দূর থেকে উচ্চতাকে দেখতে বেশ লাগে! কাছে যাওয়া অবান্তর ভাবছে মন। বিনয় কি তা-বলে উচ্চ নয়? আলবত উচ্চ। শতবার উচ্চ। কিন্তু নিজের উচ্চতাকে পরিণতি দানে ব্যর্থ এই কবি! মুখচোরা হওয়ার কারণে তাঁর কণ্ঠস্বর অনুচ্চই থাকে সবসময়। স্বপ্নে তিনি গায়ত্রীচূড়ায় বসে থাকা পাখি, সেখান থেকে গলা তুলে তাকে ডাকছেন, কিন্তু তার কণ্ঠস্বর মাটিতে পৌঁছায়নি কখনো।
জীবনানন্দ দাশের খ্যাপাটে সংস্করণ কবি বিনয় মজুমদার। প্রেসিডেন্সির ইংরেজি সাহিত্য পড়ুয়া ঝকঝকে তারুণ্যে উচ্ছল গায়ত্রীর পাশে এমন এক আদমসন্তানকে দেখছি, যে তার জীবনের উদ্দেশ্য নিয়ে মহা তােলগোলে আছে। কবি না ইঞ্জিনিয়ার হওয়া ভালো সেটি ঠিক করতে সময় লাগছে তার। তথাপি কল্পনা করা যাক, তিনি ও গায়ত্রী বসে গল্প করছেন, যেখানে তরুণ কবি আচম্বিত তরুণীকে শুনিয়ে দিচ্ছে আসন্ন কবিতার দুচরণ :
বিনিদ্র রাত্রির পরে মাথায় জড়তা আসে, চোখ জ্ব’লে যায়,
হাতবোমা ভ’রে থাকে কী ভীষণ অতিক্রান্ত চাপে।
প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাগুলি ক্রমে জ্ঞান হয়ে ওঠে।
এ-সকল সংখ্যাতীত উদ্ভিদ বা তৃণ, গুল্ম ইত্যাদির মূল
অন্তরালে মিশে গিয়ে অত্যন্ত জটিলভাবে থাকা স্বাভাবিক।
কোনো পরিচিত নাম বলার সময় হলে মাঝে মাঝে দেখি
মনে নেই, ভুলে গেছি; হে কবিতারাশি, ভাবি ঈষৎ আয়াসে
ঠিক মনে এসে যাবে, অথচ…অথচ…হায়, সে এক বিস্মিত,
অসহ্য সন্ধান, তাই কেউ যদি সে-সময়ে ব’লে দেয় তবে
তপ্ত লৌহদণ্ড জলে প্রবিষ্ট হবার শান্তি আচম্বিতে নামে।
পঙক্তিগুলো শুনে তরুণীর অনুভূতি কী দাঁড়াতে পারে তা কল্পনার চেষ্টা করছি। বিনয়আত্মা তো বোদলেয়ারের মতো অশান্ত ছিল। অস্থির, উন্মূল চরিত্র হয়ে কলকাতায় বন্ধুমহলে তার দিনরজনি কেটেছে তখন। শক্তি-সুনীল থেকে হাংরি তো বটেই, ঋত্বিক ঘটকের মতো পাগলা জগাইয়ের দেখা যেখানে মিলেছে ঘনঘন। শাণিত মেধার সঙ্গে মদের অফুরন্ত ভাণ্ডার একচুমুকে খালি করা যাঁর কাছে ব্যাপার নয়। এসব পাগলামোয় তাল দিয়ে চলা বিনয়ের জন্য মোটেও সহজ ছিল না।
জগতের সঙ্গে ক্লায়কেশে সংযোগ রেখে চলার তালে থেকেছেন হতচ্ছাড়া কবি। নিজেকে এরকম কোনো তপ্ত লৌহদণ্ড বলে ভেবেছেন, যাকে জলে প্রবিষ্ট করালে তবে সে শীতল হবে! জুড়াতে পারবে উদগ্র বাসনা ও সমাহিত সমাধির টানাপোড়েন। গায়ত্রী কি সেই জল ছিলেন? বিনয়ের উদগ্র অস্থিরতা নেভানোর মতো দৃশত সুনীল কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে স্বচ্ছতোয়া জল হওয়ার শক্তি তার ছিল কি? কেন জানি সন্দেহ হচ্ছে! প্রেসিডেন্সি পড়ুয়া গায়ত্রীর পক্ষে ওরকম হওয়াটা অবান্তর ঠেকছে নিজের কাছে। তাঁকে নিয়ে বিনয়ের কাব্য করার বাসনাকে নাকচ করতে মন সায় দিচ্ছে প্রবল।
ফিরে এসো চাকার পুরোটা আমি পাঠকের কাছে এক সাইকিজার্নি। বিনয়ের অবচেতন থেকে উঠে আসা প্রত্যাখ্যানের মর্মর উচ্চারণ ছিল এসব কবিতা। তার কতটা বাস্তবের কোনো গায়ত্রীকে ভেবে তিনি লিখেছেন, আর কতটা কল্পনায় গরিয়ান গায়ত্রীর জন্য নিবেদন, তার বিন্দুবিসর্গ অনুমানের সাধ্য আমার নেই। সে-আগ্রহ কখনো ভিতরে তীব্র হয়নি। তবু কেন মনে হচ্ছে,—এর সবটাই হে দেবী, কেবল তোমারে লক্ষ করে! বিনয়ের পক্ষে প্যাথলজিক্যাল লায়ার হওয়া সম্ভব নয় বলে পাগল হয়েছিলেন। বলা ভালো, ফিরে এসো চাকায় পাগলামির বীজ আগেভাগে বপন করেছেন কবি। কলম ফেটে বেরিয়ে এসেছিল এরকম স্তবকগুচ্ছ :
কী উৎফুল্ল আশা নিয়ে সকালে জেগেছি সবিনয়ে।
কৌটোর মাংসের মতো সুরক্ষিত তোমার প্রতিভা
উদ্ভাসিত করেছিলো ভবিষ্যৎ, দিকচক্রবাল।
সভয়ে ভেবেছিলাম সম্মিলিত চায়ের ভাবনা,
বায়ুসেবনের কথা, চিরন্তন শিখরের বায়ু ।
দৃষ্টিবিভ্রমের মতো কাল্পনিক ব’লে মনে হয়
তোমাকে অস্তিত্বহীনা, অথবা হয়তো লুপ্ত, মৃত।
অথবা করেছো ত্যাগ, অবৈধ পুত্রের মতো, পথে।
জীবনের কথা ভাবি, ক্ষত সেরে গেলে পরে ত্বকে
পুনরায় কেশোদ্গম হবে না; বিমর্ষ ভাবনায়
রাত্রির মাছির মতো শান্ত হ’য়ে রয়েছে বেদনা-
হাসপাতালের থেকে ফেরার সময়কার মনে।
মাঝে-মাঝে অগোচরে বালকের ঘুমের ভিতরে
প্রস্রাব করার মতো অস্থানে বেদনা ঝ’রে যাবে।
দৃষ্টিবিভ্রমের মতো যাকে কাল্পনিক, অস্তিত্বহীন, লুপ্ত ও মৃত ভাবছেন কবি,—সে তাহলে কোন পাষাণী? নাকি কবির খেয়ালি মনোজমিনে পাষাণী জন্ম নিয়েছিল সদ্য? অস্তিত্বের প্রলোভন ও শঠতাকে একত্রে পাঠের বাতিক বিনয়ের মধ্যে সহজাত। কবি সেই তরুণ বয়সে বুঝে গেছেন, মহৎ প্রলোভন পরিশেষে অবক্ষয়ে আয়ু ফুরায়। ফিরে এসো চাকার কবিতারা মিলনের মধ্যে বিচ্ছেদ দেখেছে আগেভাগে। বিচ্ছেদের বেদনায় দেখতে পেয়েছে মিলনের অনিবার্য পরিণাম। বইয়ের সবগুলো কবিতা এই তারে সাধা হলেও কতিপয় পঙক্তি আওরানো যায় আরো একবার। বিনয় লিখছেন :
শাশ্বত মাছের মতো বিস্মরণশীলা যেন তুমি।
যদিও সংবাদ পাবে, পেয়েছো বেতারে প্রতিদিন,
জেনেছো অন্তরলোক, দূরে থেকে, তবু ভুলে যাবে।
. . .
জীবনে ব্যর্থতা থাকে ; অশ্রুপূর্ণ মেঘমালা থাকে;
বেদনার্ত মোরগের নিদ্রাহীন জীবন ফুরালো।
মশাগুলি কী নিঃসঙ্গ, তবুও বিষন্ন আশা নিয়ে
আর কোনো ফুল নয়, রৌদ্রতৃপ্ত সূর্যমুখী নয়,
তপ্ত সমাহিত মাংস, রক্তের সন্ধানে ঘুরে ফেরে।
. . .
কাঠ চেরাইয়ের শব্দ ; আমাদের দেহের ফসল,
খড় যেন ঝ’রে গেছে, অবশেষে স্বপ্নের ভিতরে।
এত স্বাভাবিকভাবে সবই ব্যর্থ-ব্যর্থ, শান্ত, ধীর।
. . .
কোনো স্থির কেন্দ্র নেই, ক্ষণিক চিত্রের মোহে দুলি।
ভিন্ন-ভিন্ন সুশীতল স্বাস্থ্যনিবাসের স্বপ্নরূপ
ইতস্তত আকর্ষণে ভ’রে রাখে শূন্য মন, সাধ।
. . .
অব্যর্থ পাখির কাছে যতোই কালাতিপাত করি
আমাকে চেনে না তবু, পরিচয় সূচিত হ’লো না।
কোনোদিন পাবো না তো, সেতুর উপর দিয়ে দ্রুত
ট্রেনের ধ্বনির মতো সুগম্ভীর জীবন পাবো না।
. . .
মৃত্যুর প্রস্তর, যাতে কাউকে না ভালোবেসে ফেলি।
গ্রহণে সক্ষম নও। পারাবত, বৃক্ষচূড়া থেকে
পতন হ’লেও তুমি আঘাত পাও না, উড়ে যাবে।
প্রাচীন চিত্রের মতো চিরস্থায়ী হাসি নিয়ে তুমি
চলে যাবে; ক্ষত নিয়ে যন্ত্রণায় স্তব্ধ হব আমি।
ইচ্ছে করলে আরো উদ্ধৃত করা যায়; তবে এটুকু যথেষ্ট বোঝার জন্য,—জীবনের সঙ্গে বিনয়ের হিসাব-কিতাব ও ফয়সালার কারণে কোনো গায়ত্রীসঙ্গে তাঁর কিছু পাওয়ার ছিল না। উদগ্র মাংসের লালসা সক্রিয় থাকলেও মানবীকে ভালোবাসা নিবেদনে একে যথেষ্ট ভাবেননি কবি। জীবনের স্বাদ ও পরিণাম নিয়ে দোটানার কারণে তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না নারীকে নিয়ে সাড়ম্বর ঘরামি যাপন। বিনয় তাঁর কাব্যভাষার তাই চিরন্তন প্রহেলিকা। গ্রহণ নয়, প্রত্যাখ্যানে নিজের নিরাময় তালাশ করেছেন :
অনেক ভেবেছি আমি, অনেক ছোবল নিয়ে প্রাণে
জেনেছি বিদীর্ণ হওয়া কাকে বলে, কাকে বলে নীল–
আকাশের, হৃদয়ের; কাকে বলে নির্বিকার পাখি।
. . .
হয়েছিলো কোনোকালে একবার হীরকের চোখে
নিজেকে বিম্বিত দেখে; তারপর আর কেন আরো
উদ্বৃত্ত ফুলের প্রতি তাকাবো উদ্যত বাসনায়?
কেন, মনোলীনা, কেন বলো চাকা, কী হেতু তাকাবো?
. . .
কাঁটার আঘাতদায়ী কুসুমের স্মৃতির মতন
দীর্ঘস্থায়ী তার চিন্তা; প্রথম মিলনকালে ছেঁড়া
ত্বকের জ্বালার মতো গোপন, মধুর এ-বেদনা।
যাক, সব জ্ব’লে যাক, জলস্তম্ভ, ছেঁড়া যা হৃদয়।
সুতরাং বিনয়ের অশান্ত হৃদয় প্রেমানুকূল নয় একটুও! তাঁর কবিবন্ধুরা যেমন পাগলাটে হয়েও দিব্যি সভ্য প্রেমিক, যদিও অন্তরে অসভ্য জখমি, যদিও তারা দলছুট, তথাপি সামাজিক,—গায়ত্রী নামক ধাঁধাসমতুল নারীর হাত তাঁরা ধরলেও ধরতে পারতেন হয়তো-বা! বিনয় নিজ কৃতিদোষে সেই হিসাবের বাইরে ঘুরেছেন আজীবন। উন্মাদের জন্য সিদ্ধান্তটি যথার্থ ছিল! ফিরে এসো চাকা যে-কবিতায় এসে শেষ হতেছে সেটি আস্ত পাঠ করি এবার। মনে গেঁথে নেই দৃশ্যনির্মিতি একঝলক, তাহলে বুঝব কেন গায়ত্রীমন্ত্রে গলা সাধা কবিকে দিয়ে হওয়ার ছিল না :
তুমি যেন ফিরে এসে পুনরায় কুন্ঠিত শিশুকে
করাঘাত ক’রে ক’রে ঘুম পাড়াবার সাধ ক’রে
আড়ালে যেও না; আমি এতদিনে চিনেছি কেবল
অপার ক্ষমতাময়ী হাত দুটি, ক্ষিপ্র হাত দুটি–
ক্ষণিক নিস্তারলাভে একা একা ব্যর্থ বারিপাত।
কবিতা সমাপ্ত হতে দেবে নাকি? সার্থক চক্রের
আশায় শেষের পংক্তি ভেবে ভেবে নিদ্রা চ’লে গেছে।
কেবলি কবোষ্ণ চিন্তা, রস এসে চাপ দিতে থাকে;
তারা যেন কুসুমের অভ্যন্তরে মধু-র ঈর্ষিত
স্থান চায়, মালিকায় গাঁথা হয়ে ঘ্রাণ দিতে চায়।
কবিতা সমাপ্ত হতে দাও, নারী, ক্রমে—ক্রমাগত
ছন্দিত, ঘর্ষণে, দ্যাখ, উত্তেজনা শীর্ষলাভ করে,
আমাদের চিন্তাপাত, রসপাত ঘটে, শান্তি নামে।
আড়ালে যেও না যেন, ঘুম পাড়াবার সাধ ক’রে।
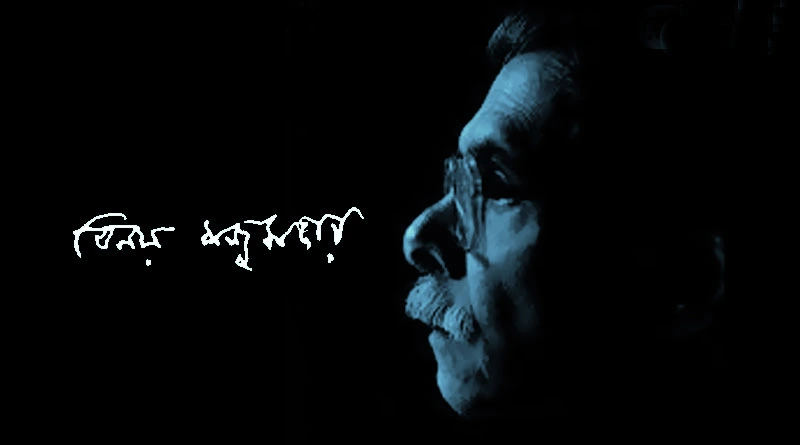
কবিতাটি যে-দৃশ্য তুলে ধরে, সেখানে কবি তার নারীকে বারবার শিশুকে ঘুম পাড়ানোর ছলে এসে চলে যেতে বারণ করছেন। কেন বারণ করছেন? কারণ, তাকে যদি কবিতায় যতি টানতে হয়, যদি শেষ করতে হয় কবিতা, সেখানে দুটি নারনারীর মধ্যে মিলনের পরম্পরা অটুট রাখা দরকারি। মিলন মানে তো ওই ছন্দ, ঘর্ষণ, পুলক, আর শীর্ষলাভের চূড়ায় উঠে রেতঃপাত… এবং অতঃপর ওম শান্তি। সুতরাং কবিতা তেম্নি নারী যাকে বাস্তবের নারীর মতো নিরবচ্ছিন্ন সম্ভোগে নিয়ে যাওয়াকে বিনয় সিদ্ধি ভাবছেন! আরেকবকার পাঠ যাই আস্ত আরেকখানা :
তোমাদের কাছে আছে সংগোপন, আশ্চর্য ব-দ্বীপ
কৃষ্ণবর্ণ অরণ্যের অন্তরালে ঘ্রাণময় হ্রদে
আমার হৃদয় স্বপ্নে মুগ্ধ হয়, একা স্নান করে।
হে শান্তি, অমেয় তৃপ্তি, তুমি দীপ্ত হার্দিক প্রেমের
মূলে আছো, আছো ফলে; মধ্যবর্তী অবকাশে প্রাণ
তবুও সকল কিছু সংযমে নিক্ষেপ করে দূরে;
ক্ষণস্থায়ী তৃপ্তিজাত আসক্তিতে চিরন্তন মোহে
রূপ দিতে বর্ণ, গন্ধ খুঁজে ফেরে, বায়ব আকাশ,
খুঁজে ফেরে চন্দ্রাতপ ; যেন সরোবরে মুগ্ধ তাপ –
জ্যোৎস্না উদ্ভাসিত হ’লে তবে তার স্নান গ্রহণীয়।
এসো হে ব-দ্বীপ, এসো তামোরস, এসো জ্বালা, প্রেম,
আলোড়ন, ঝঞ্ঝা, লোভ, সংযত সংহারমালা, এসো।
নিয়ে যায় মূলে, রসে, বাষ্পীভূত ক’রে মেলে দাও
আয়ুষ্কালব্যাপী নভে, আবিষ্কৃত আকাশের স্বাদে।
বস্তুসমুদয় অথবা এর আপাত মনোরম প্রতীক গায়ত্রীরা কাজেই বিনয়ের কবিতায় নিছক উপকরণ। তারা মনোহর হলেও ক্ষণস্থায়ী। অচিরে ক্ষয়ে যাবে। যা অক্ষয়, সেটি হচ্ছে কবির অশান্ত হৃদয়। আয়ুষ্কালব্যাপী নভে নিজেকে অবিষ্কারের বাসনায় যে-কবি তার কবিতাকে ফিরে আসা চাকার মতো ঘূর্ণিশীল দেখছে অবিরত।
. . .
. . .