জনপ্রিয় সংগীতের নন্দন : থিওডোর গ্র্যাসিক
ভাষান্তর : রিফাত মাহবুব

লেখক পরিচিতি থিওডোর গ্র্যাসিক (Theodore Gracyk) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিনাসোটা স্টেট ইউনিভার্সিটির ইতিহাস, ভাষা ও মানবিক বিভাগের অধ্যাপক। ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া, ডেভিস থেকে পিএইচডি অর্জন করেন। শিল্পের দর্শন; ইমানুয়েল কান্ট; আটারো শতকের দর্শন; সংস্কৃতিতত্ত্ব ইত্যাদি নিয়ে গবেষণা করেছেন। অন মিউজিক, রিদম এন্ড নয়েজ : এ্যান এসথেটিক্স অব রক এবং আই ওন্না বি মি : রক মিউজিক অ্যান্ড দ্য পলিটিক্স অব আইডেন্টিটি তাঁর আলোচিত বইগুলোর মধ্যে অন্যতম। দ্য জার্নাল অব এসথেটিক্স অ্যান্ড আর্ট ক্রিটিসিজম-এ সহসম্পাদক ছিলেন এই লেখক-গবেষক। আই ওন্না বি মি : রক মিউজিক এন্ড দা পলিটিক্স অব আইডেন্টিটি বইটির জন্য ২০০২ সনে উডি গাথরি পুরস্কারে তাঁকে সম্মানিত করা হয়। বক্ষ্যমাণ রচনা থিওডোর গ্র্যাসিকের দ্য এসথেটিক্স অব পপুলার মিউজিক (The Aesthetics of Popular Music) থেকে চয়ন করা হয়েছে। অনুবাদে প্রাঞ্জলতা রক্ষার খাতিরে কতকক্ষেত্রে স্বাধীনতা গ্রহণ করলেও যথাসম্ভব মূলানুগ থাকার চেষ্টা করেছি। -রিফাত মাহবুব . . .
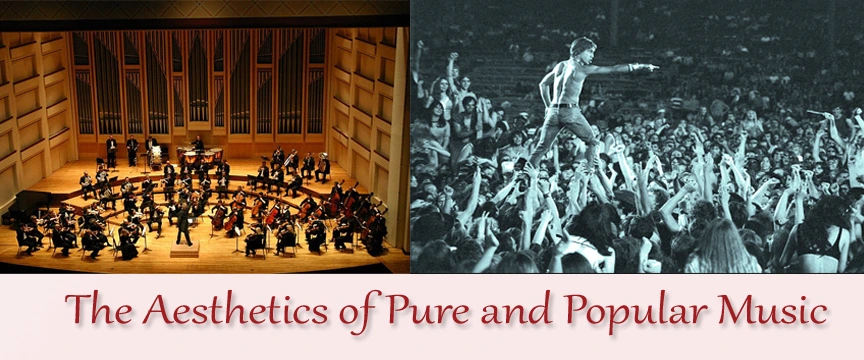
পপুলার মিউজিক বা আটপৌরে বাংলায় জনপ্রিয় সংগীতকে ঘিরে দার্শনিক আলাপে সংগীতের শুদ্ধ ও গুরুগম্ভীর শাখার বিপরীত স্রোত হিসেবে তাকে বিবেচনা করা হতো। সংগীত-দর্শনের সকল মনোযোগ শুদ্ধসুরে নিবেদেত থেকেছে। সংগীত নিয়ে দার্শনিক আলাপে আগ্রহীদের কাছে সম্প্রতি দুটি বিশেষ কারণে জনপ্রিয় সংগীত আবেদন রাখে; প্রথম কারণ,- জনপ্রিয় সংগীতে অভিনিবেশ সংগীত-দর্শনকে ঘিরে চলতে থাকা তর্ক-বিতর্ক চাঙ্গা রাখার অনিবার্য উপায়। সংগীত-দর্শনের মূল আলোচনা পাশ্চাত্য ধ্রুপদি সংগীতের সংগ্রশালাকে কেন্দ্র করে এখনো প্রবহমান। পাশ্চাত্যে সংগীতের শিকড় ও গতিপথ বুঝতে হলে কাজেই দর্শনবাদী আলোচককে শুদ্ধসুরের পাশাপাশি জনপ্রিয় সুরের দিকে দৃষ্টি দিতেই হবে। দ্বিতীয় কারণ,- শিল্প ও তার নন্দনতত্ত্ব বিষয়ক তর্কালাপে জনপ্রিয় সংগীতের প্রাসঙ্গিকতা বেড়ে চলেছে। ঐতিহ্যের যাঁতাকলে তার কলেবর ও নন্দনকে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে প্রান্তিক রাখা হয়েছিল;- মতবাদটি এখন জোরালো। এই মতবাদ যারা বহন করছেন তারা মনে করেন,- জনপ্রিয় সংগীত হচ্ছে নন্দনতাত্ত্বিক দর্শনের নিয়মতান্ত্রিক উপায়ের বিপরীত শক্তি।
জনপ্রিয় সংগীত বা পপুলার মিউজিক শুদ্ধ সংগীতের চেয়ে ভিন্ন;- এই মত যতটা জোরোশোরে প্রচলিত, ঠিক কী কারণে তারা একে অন্য থেকে আলাদা অথবা আলাদার মাত্রাটি কেমন,- এর কোনো সহজ উত্তর নেই। সকলে মেনে নেবেন এরকম সংজ্ঞার অভাবে জনপ্রিয় সংগীতের আলোচনায় তাকে ফোক বা লোকগান ও আর্ট বা শৈল্পিক সংগীতের চেয়ে ভিন্ন ভাবা হয়। পার্থক্য দেখাতে উদাহরণকে সম্বল করা হয় সেখানে। বলা হয়,- বিটলসের (The Beatles) গান হচ্ছে পপুলার মিউজিক, তবে ইগোর স্ট্র্যাভিনস্কি (Igor Stravinsky) শুদ্ধসংগীতে পড়ছে। সংজ্ঞার এই ধোঁয়াশা থাকায় পপুলার মিউজিকের বিভিন্ন ঘরানাকে ঘিরে আলোচনা জমে ওঠে। রক, হিপহপ, ব্লুজ;- জনপ্রিয় সংগীতের আলোচনায় এগুলোর সবটাই প্রধান রসদ।
প্লেটো (Plato) এবং এ্যারিস্টোটল (Aristotle) দুজনেই সংগীতের দর্শনে উৎসাহী ছিলেন। সেই হিসেবে বলা যায় সংগীত-দর্শন আধুনিক শিল্পকলার যে-দর্শন তার চেয়ে অনেক পুরোনো এবং উভয়ের মধ্যে পার্থক্য ব্যাপক। তথাপি, আধুনিক সংগীত-দর্শন আধুনিক নন্দনতত্ত্বের ধারণায় গভীরভাবে প্রভাবিত। রেনেসাঁ পরবর্তী সময়ে আটারো শতকের ইউরোপে ‘নন্দনতত্ত্ব‘ নামে নতুন এক পাঠ জন্ম দিতে দার্শনিক শ্রেণি মেতে ওঠেন, যার উদেশ্য ছিল ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা নানান ধরণের ‘শিল্পকলা’কে আদর্শের মাপকাঠিতে যাচাই-বাছাইয়ের চেষ্টা করা। উক্ত মাপদণ্ডে বিজ্ঞান ও কারিগরি বিষয়গুলো সংগীত, কবিতা, নাটক, নৃত্য, চিত্রকলা ও স্থাপত্য থেকে পৃথক হয়ে যায়। সংগীত-দর্শন উক্ত ধারণা মোতাবেক আধুনিক অর্থে যেটি ‘আর্ট’ বা ‘শিল্প তার পথানুসারী।
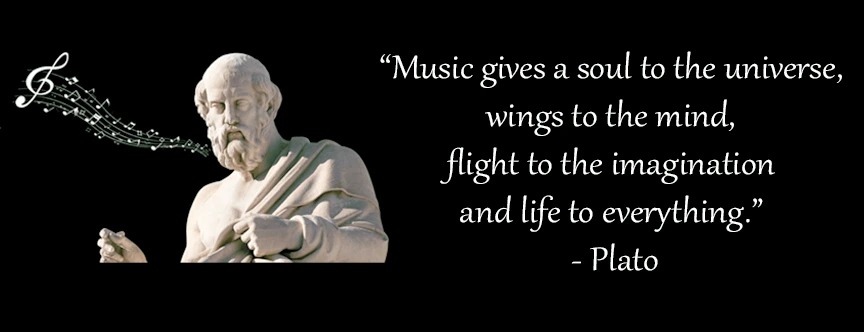
শুদ্ধ শিল্পকে জনপ্রিয় শিল্প থেকে আলাদা করার ক্ষেত্রে তিনটি বিষয় প্রাসঙ্গিক। প্রথমত, শিল্প প্রতিভাবানের সৃষ্টি। শিল্প সদা পরিবর্তনশীল, ফলে নতুন শিল্পমানে উন্নত পরিবর্তন। দ্বিতীয়ত, শিল্পের মূল্য নান্দনিকতায় নিহিত, এবং নান্দনিকতা তার নিজস্ব নিয়মে চলে। শিল্প ব্যবহারিক, নৈতিক অথবা সামাজিক মূল্যের ওপর নির্ভরশীল নয়। দ্বিতীয়ত, শুদ্ধ শিল্পের ক্ষেত্রে যেটি সত্য, সংগীতের ক্ষেত্রেও সেটি প্রযোজ্য। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি থেকে ঊনবিংশর মধ্যপর্ব পর্যন্ত দার্শনিকরা সংগীতকে শুদ্ধশিল্পের অপরিহার্য স্তম্ভ রূপে গ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং যে-সংগীত স্বাধীন নয় এবং যেখানে প্রতিভার স্বাক্ষর নেই তাকে শিল্প বলে গণ্য করার তাগিদ ছিল না। জনপ্রিয় সংগীতে এই অপরিহার্য গুণের অভাব আছে;- বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় এই মতবাদ শক্তিশালী ছিল।
অষ্টাদশ শতাব্দীর চিন্তাছক পরবর্তী সময়ে যথেষ্ট প্রভাব রেখেছে, তবে সেই ছকে শুদ্ধ বনাম জনপ্রিয় শিল্পের মধ্যে মোটাদাগে পার্থক্য নেই। যেমন, ইমানুয়েল কান্টের (Immanuel Kant) শিল্পদর্শন অষ্টাদশ শতকের নন্দনতত্ত্বে মাইলফলক। শিল্পের প্রতিভা নির্ভরতা ও স্বায়ত্তশাসনের ওপর সেখানে জোর দেওয়া হয়েছে। কান্টের এই তত্ত্ব অনেকসময় জনপ্রিয় সংগীতকে শিল্পের কোঠায় স্থান দেওয়ার দাবিটিকে খারিজ করে বসে। সংগীত-দর্শন নিয়ে আলাপিদের অনেকে কান্টের সঙ্গে সহমত,- জনপ্রিয় সংগীতের মতো চটুল শিল্প বুদ্ধিবৃত্তিকে ভোঁতা করে দেয়। জনপ্রিয় সংগীতে না আছে শুদ্ধ সংগীতের ভাবগাম্ভীর্য, না আছে নিরীক্ষায় দক্ষতা, কাজেই জনপ্রিয় সংগীত সস্তা বিনোদনের একটি মাধ্যম ছাড়া কিছু না। এই তর্ক কান্ট প্রস্তাবিত তত্ত্বের প্রায়োগিক রূপ; তথাপি মনে রাখা প্রয়োজন,- কান্ট নিজে জনপ্রিয় শিল্পের প্রবর্তক ছিলেন না, তাই তার আলোচনায় জনপ্রিয় শিল্প ও তূলনামূলক চটুল শিল্প স্থান পায়নি। কান্টের আলোচনায় সংগীতের মূল্য নিয়ে নিৰ্দিষ্ট বা শেষ কথা বলে কিছু নেই। বস্তুত কান্টের নৈতিকানুগ নিয়মচারিতার তকমার সঙ্গে তার সংগীত বিষয়ক কিছু দার্শনিকতাকে সাংঘর্ষিক মনে হতেই পারে। কান্ট একপর্যায়ে যন্ত্রনির্ভর সুর/সংগীতকে মূল সংগীত থেকে এক ধাপ নিচে রেখেছিলেন; এই যুক্তিতে যে,- যন্ত্রসংগীত কেবল ইন্দ্রিয়কে তুষ্ট করে।
অষ্টাদশ শতাব্দীর দর্শনে শুদ্ধ সংগীত ও জনপ্রিয় সংগীতের পার্থক্য বিষয়ক নীরবতাকে সর্বাগ্রে সত্য বলে ধরে নেওয়ার কারণ নেই। উক্ত শতকের অনেক আলোচনায় জনপ্রিয় সংগীত ও শুদ্ধ সংগীতকে আলাদা করে দেখা হয়নি। যেমন, যে-সময়ে কান্ট যন্ত্রসংগীতের মেধা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন, একই সময়ে মোজার্ট (W. A. Mozart) অপেরাতে চপল সুরনির্ভর সহজ-শ্রুতির সাংগীতিক প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে কথা বলছিলেন। এই ধরনের তর্ক প্রচলিত থাকলেও অষ্টাদশ শতকের আলোকায়নপর্বে শুদ্ধ সংগীত ও জনপ্রিয় সংগীতের পরিষ্কার পার্থক্য ছিল;- এটি ধরে নেওয়া পুরোপুরি যথার্থ নয়। বেশি হলে, সেইসময়ের দার্শনিকরা শালীন ও অশালীন সংগীতের পার্থক্য নিয়ে সতর্ক ছিলেন। সংগীতের ভালো-মন্দের শ্রেণিবিভাজন তখন থেকে শুরু, যখন পপুলার কালচার বা জনপ্রিয় সংস্কৃতির আলাদা ক্ষেত্রটি তৈরি হচ্ছিল, যেখানে অবশ্যম্ভাবীভাবে ‘জনপ্রিয়’ বিশেষণকে নেতিবাচক হিসেবে দাঁড় করানো হয়।
শুদ্ধ সংগীত ও অন্যান্য ধারার সংগীতে মোটাদাগের পার্থক্য ঊনিশ শতকের ঘটনা। ঊনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে এখন যাকে আমরা পপুলার বা জনপ্রিয় সংগীত বলছি, তার ধারণাবীজ বপনের কাজটি শুরু হয়। সংগীত-আলোচকরা ইউরোপের কনসার্টে পরিবেশিত সংগীত কী-কারণে ভিন্ন ও গুণবিচারে উৎকৃষ্ট, সেই বিতর্কে জড়িয়ে পড়লেন। কান্টের স্বশাসিত নন্দনতত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে এডুয়ার্ড হ্যান্সলিক (Eduard Hanslick) যন্ত্রসংগীতে মনোনিবেশ করেন। সংগীতের কলা হচ্ছে তার স্বরের নিরীক্ষা। কণ্ঠের নিরীক্ষাই তার সর্বোচ্চ উৎকর্ষ এবং সেটি স্বশাসিত। অ-শুদ্ধ সংগীত, ভাষা অথবা আবেগের ওপর নির্ভর করে;- এই সূত্র মোতাবেক প্রায় সকল ধরনের জনপ্রিয় সংগীত অ-শুদ্ধ, কেননা সেগুলো ভাষা ও আবেগ দিয়ে বিরচিত।
এর প্রায় সিকি শতাব্দী পর এডমান্ড গার্নি (Edmund Gurney) সংগীতের স্বাধীনতা নিয়ে আরো আলোচনা হাজির করেন। গার্নি অবশ্য জনপ্রিয় সংগীতে সুরমাধুর্যের প্রশংসা করেছেন, তবে জনপ্রিয় সংগীতে আবেগের প্রাধান্যকে সমালোচনার তিরে বিদ্ধ করে জানিয়ে দেন,- এটিকে তিনি সংগীতের নিম্নস্তরে রাখছেন। হ্যান্সলিক ও গার্নি দুজনেই সাহিত্যের রোমান্টিক যুগে সংগীতের সাবলীল প্রকাশভঙ্গি জনপ্রিয় হয়ে ওঠার বিপরীতে নিজেদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করছিলেন। সংগীতের সেই পুরোনো সমালোচনা, যেখানে আবেগ প্রকাশে দেহের ব্যবহারকে কটাক্ষ করা হয়, একে সমর্থন দিতে হ্যান্সলিক ও গার্নি এই মতবাদ নিয়ে আসলেন,- সংগীতে দৈহিক আবেগের ব্যবহার তার মান ক্ষুণ্ন করে। এক্ষেত্রে তাঁদের দুজনের ওপর কান্টের প্রভাব লক্ষণীয়। কান্টের মতে সংগীতের দৈহিক প্রকাশ একধরনের ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রতিক্রিয়া তৈরি করে, যেটি সংগীতের শুদ্ধ ও সর্বজনীন আবেদনের পরিপন্থী। যারা জনপ্রিয় সংগীতের গুণগত মানের সমালোচনা করেন এই বক্তব্যকে সামনে রেখে,- জনপ্রিয় সংগীত প্রধানত দৈহিক, অনিয়ন্ত্রিত আবেগের প্রকাশ,- তাদের জন্য হ্যান্সলিক ও গার্নির মতবাদ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাদের মতে, ক্লাসিক্যাল বা শাস্ত্রীয় সংগীতের বিমূর্ত কাঠামোকে উপলব্ধি করতে প্রয়োজন জ্ঞান ও প্রজ্ঞা। দেহ কেবল সুর শুনে, কিন্তু জ্ঞান সুরে নিমগ্ন হয়।
গার্নি অবশ্য জনপ্রিয় সংগীতের পুরোপুরি বিপক্ষে ছিলেন না। তিনি জনপ্রিয় সংগীতের মধ্যে শ্রেণিবিভাজন করেছেন : সাধারণ মানুষকে স্থূল আনন্দ দিতে বাণিজ্যিকভাবে সস্তা বা নিম্নস্তরের জনপ্রিয় সংগীত ব্যবহৃত হয়। কিছুটা উন্নত জনপ্রিয় সংগীতের একটি সার্বজনীন আবেদন থাকে;- ফোক বা লোকগান দ্বিতীয় ধারায় পড়ছে। অপেরা ও ধ্রুপদি ঘরানায় এই ধাঁচের অন্যান্য যা আছে, সেগুলোও জনপ্রিয় সংগীতে পড়বে। ১৮৮০ সালের দিকে গার্নি বুঝেছিলেন, রুচির বাঁধাধরা বিন্যাসের সাহায্যে সমাজে শ্রেণিবিভাজনকে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়, যার ফলে সংগীতের অবাধ বিচরণ ব্যাহত হতে থাকে। ফলে সমাজে জনপ্রিয়তা বিষয়ক ধারণার সত্যিকার প্রতিফলন ঘটে না। রিচার্ড ওয়াগনারের (Richard Wagner) মতবাদ ছিল,- সত্যিকার জনপ্রিয়তা জাতীয়তাবোধের সীমায় পরিবেষ্টিত;- গার্নি মূলত তাঁর এই মতের সমালোচনা করেছেন।
গার্নির মতে সংগীত কখনো সত্যিকার অর্থে জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারে না, যদি তা সামাজিক শ্রেণিবিভাজনের দ্বারা বাধাগ্রস্ত হয়। ফ্রেডরিখ নিটশে (Friedrich Nietzsche) সম্পূর্ণ বিপরীত মত পোষণ করেছেন। তিনি মনে করতেন,- সংগীতের বিষয়টি সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গির বহিঃপ্রকাশ। নিটশে তাঁর শুরুর দিককার আলোচনায় পাশ্চাত্যের ধ্রুপদি সংগীতের উৎকর্ষকে একপেশে চোখে দেখেছেন। একইসঙ্গে তিনি সেইসব সুরকার ও সংগীতজ্ঞের গুণগান করেছিলেন যাদের আপাতদৃষ্টিতে যুক্তিহীন সৃষ্টি ইউরোপের অতি যুক্তিবাদী সৃষ্টিকেও চ্যালেঞ্জ জানায়। পর্যায়ক্রমে নিটশে তাঁর চিন্তাধারকে বিপরীত অভিমুখে চালিত করেন।
রিচার্ড ওয়াগনার সৃষ্ট অপেরার দীর্ঘ সমালোচনায় তিনি আর্ট বা শুদ্ধ সংগীতের একচেটিয়া ‘মাহাত্ম্য’কে কটাক্ষ করেন। কান্টের নন্দনতত্ত্বের সম্পূর্ণ বিপরীত প্রান্তে গমন করে নিটশে জর্জেস বিজেটের (Georges Bizet) জনপ্রিয় অপেরা কারমেনকে (১৮৭৫) তার চটুল ও সাদামাটা আবেদনের জন্য প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছিলেন। যদিও বেশিরভাগ দার্শনিক নিটশের চটুল সংগীতের জয়গান উপেক্ষা করেছেন। নিটশে ছাড়াও সংগীত-দর্শনের মূল আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু ছিল এই মতবাদ,- শুদ্ধ ও উন্নত সংগীত মানে সেটি স্বায়ত্তশাসিত ও আঙ্গিকের দিক থেকে জটিল। এমনকি সমসাময়িক নব্বই দশকে জনপ্রিয় সংগীত বিষয়ক দার্শনিক আলাপ ওই বিষয়কে ঘিরেই চলছে। দার্শনিকগণ অনেকটা সামগ্রিকভাবে দুই পুরাতন ধারাকে প্রতিষ্ঠিত করেন,- জনপ্রিয় সংগীত গুণগত বিচারে আর্ট বা শুদ্ধসংগীতের চেয়ে ভিন্ন, এবং জনপ্রিয় সংগীত মানের দিক থেকে শুদ্ধ সংগীতের নিচে অবস্থান করে। যার ফলে দার্শনিকদের মধ্যে যারা জনপ্রিয় সংগীত নিয়ে ভেবেছেন তাঁরা মূলত জনপ্রিয় সংগীতের খুঁত বের করতেই ব্যস্ত ছিলেন।
. . .
. . .





