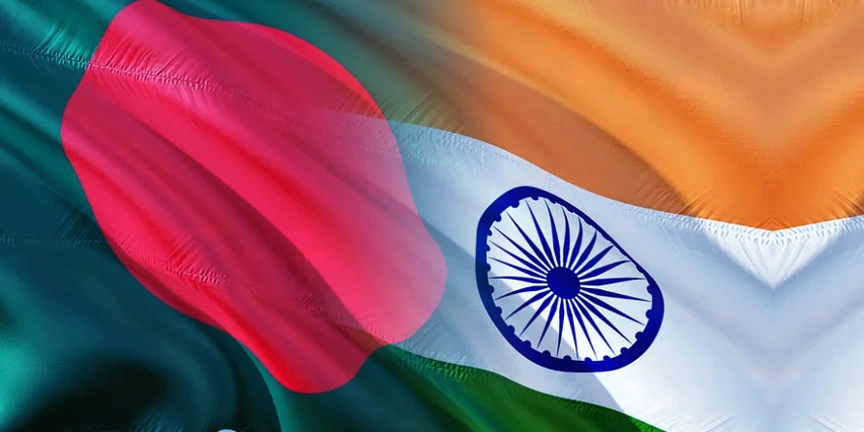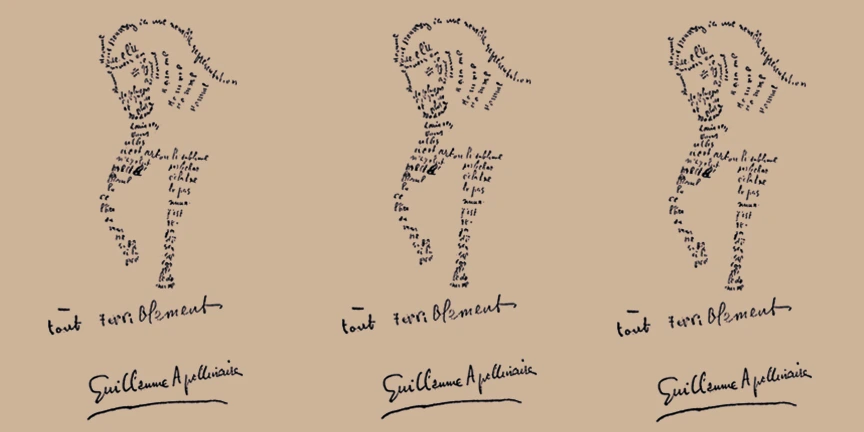মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত আপতত এমন এক বোঝাপড়ায় উপনীত, বড়ো আকারের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিবাদ না ঘটলে এই যৌথশক্তির সঙ্গে ইউনূস-শাহবাজ গং কুলিয়ে উঠতে পারবেন না। সুতরাং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য ভারত পাবে শতভাগ। চীনও পরিস্থিতি বিবেচনায় রা কাড়বে না। কথাগুলো আরো এ-কারণে বলা, রেজিম চেঞ্জার হিসেবে খ্যাত ডোনাল্ড লুকে বিদায় দিয়ে ট্রাম্প এস পল কাপুরের ঘাড়ে দক্ষিণ এশিয়ার নিরাপত্তা ইস্যু ডিল করার দায়িত্ব দিতে যাচ্ছেন। রিপাবলিক সিনেটরদের তাঁর ব্যাপারে আস্থা এখনো ইতিবাচক।
-
-
জনপ্রিয় সংগীতে চোখে পড়ার মতো গুণগত ও মৌলিক পার্থক্য না থাকায় এর কোনো কেন্দ্রীয় বার্তা থাকে না। তবে জনপ্রিয় সংগীত যে-দার্শনিক দৃষ্টিকোণ ধারণ করে, এর ভিতর দিয়ে অর্থ-সামাজিক প্রবাহের চিত্রখানা পাওয়া যায়, এবং এ-কারণে তার প্রভাব বাড়তেই থাকে। আধুনিক পুঁজিবাদে বিচ্ছিন্নতাবাদের সমস্যাকে সে প্রকট করে তোলে। জনপ্রিয় সংগীতে নিহিত ক্ষণিক আনন্দ হলো বিচ্ছিন্নতাবাদ থেকে একধরনের মুক্তি। সত্যিকার তৃপ্তি দিতে না পারায় অবিচ্ছিন্ন একটি চক্রে মানুষকে সে বেঁধে ফেলে। ভোগ, বিচ্ছিন্নতা, বিরক্তি ও বিক্ষিপ্ততাকে যেটি কিনা প্রলোভিত করে ।
-
সারসংক্ষেপ করলে প্রশ্নগুলো এমন : মার্কসের মানি ম্যানেজমেন্ট স্কিল দুর্বল, এপিকিউরিয়ানদের মতো ছিল তাঁর জীবন, সবসময় দেনার ওপর থাকত ইত্যাদি। দুর্বল মানি ম্যানেজমেন্টের কারণে সে বুর্জোয়াদের বিরোধিতা করেছে, ওদিকে জীবনযাপন করেছে বুর্জোয়া পরিবেশে। ছোটবেলা থেকে অগোছালো জীবনে অভ্যস্ত।মদ, সিগারেট টানত, আর গোসল করত না। মার্কসের আর্থিক অবস্থা যদি খারাপ হয়ে থাকে, তাহলে এতোগুলো বাচ্চা নিলো কেন? তার ওপর অনেকে আধ্যাত্মিকতা আরোপ করে থাকেন অথচ বাস্তবে সে ছিল ভোগবাদী;—আধ্যাত্মিকতার লেশমাত্র তাঁর মধ্যে ছিল না... ইত্যাদি... ইত্যাদি। এখন এসব প্রশ্নের কোনো উত্তর কি হয় আসলে? এভাবে বিচার করা কতটা যুক্তিসংগত?
-
ভাববাদের ভিত্তিভূমি ভারতীয় চিন্তায় এটি ছিল মারাত্মক হুমকি স্বরূপ ও বিপর্যয়ের শামিল। সুতরাং এ-ধরনের চিন্তার বিরোধিতা সকল দর্শনশাস্ত্রের মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। চার্বাকপন্থীদের বিরোধিতা করে মূলত অত্র অঞ্চলের মহান ভাবুক-চিন্তক-দার্শনিকগণ নিজ দর্শনের বিস্তার ঘটিয়েছেন। .. এখন এই চার্বাক আসলে কারা? তারা কি কোনো ব্যাক্তিবিশেষ অথবা গোষ্ঠী? তাদের প্রচারিত মতবাদের মূল বক্তব্য কী? এই প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর ইতিহাস থেকে উদ্ধার করা খুবই দুরূহ। চার্বাক মতবাদকে খণ্ডন করতে গিয়ে বিরোধীরা যা বলছেন সেটি সেখানে একমাত্র উৎস, এছাড়া আর কিছু মিলছে না। তাদের ব্যাপারে পরিচ্ছন্ন উপসংহারে পৌঁছানোর সমস্যা তাই যথেষ্ট গুরুতর।
-
কবিতা কি ঈশ্বরের অভিশাপ? নাকি মস্তিষ্কের এমন কোনো অলৌকিক খেলা যা বিজ্ঞানীরা এখনো বুঝলেও ব্যাখ্যা করে উঠতে পারছেন না? কারণ, কবিতায় শব্দ কেবল ভাষা নয়, তারা অস্তিত্বের গভীরতম অন্ধকারে জ্বলজ্বল করতে থাকা শিখা। দুটি পঙক্তি ভাবা যাক, কবি লিখছেন : তোমার ঠোঁটের কাছে জল রেখে যাবো/ সন্ধ্যার ছায়ায় যেন মুখ ধুয়ে নিতে পারো। এই জল কি বাস্তব? নাকি অলীক প্রত্যাশার ছায়া? কবিতার সৌন্দর্য এখানেই—এটি একইসঙ্গে বাস্তব এবং বাস্তবাতীত,—অনুভবের প্রকাশ এবং অনুভবের অতীত। মস্তিষ্ক তার যৌক্তিকতার পরিসরকে ছাড়িয়ে গিয়ে কবিতায় আশ্রয় নেয়, যেখানে ভাষা নিজে তার সীমা অতিক্রম করে।